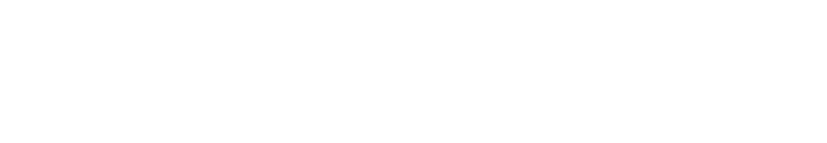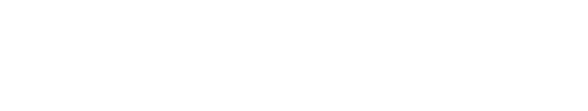কারবালায় হযরত ইমাম হোসেনের (আ.) শাহাদাত অনন্ত কাল ধরে সত্যসংগ্রামীদের অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে । তবে তাঁর আন্দোলনের কারণ ও শিক্ষা সম্বন্ধে যুগে যুগে যে সব মূল্যায়ন হয়েছে সে সবের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য লক্ষ্য করা যায় ।
বলা বাহুল্য যে, এ সব মূল্যায়নে তাঁর এবং তাঁর সঙ্গীসাথী ও পরিবারের প্রতি ভক্তি, ভালোবাসা ও সমবেদনা অভিন্ন উপাদান । কিন্তু তাঁর আন্দোলনের স্বরূপ ও কারণ সম্বন্ধে বিভিন্ন মত প্রকাশিত হয়েছে । বলা বাহুল্য যে, এ আন্দোলনের স্বরূপ ও কারণ সম্পর্কিত মূল্যায়ন যতো বেশী নির্ভুল হবে তাঁর এবং তাঁর সঙ্গীসাথী ও পরিবারের ত্যাগ ও আত্মত্যাগ থেকে আমরা ততো বেশী সঠিক শিক্ষা লাভ করতে ও উপকৃত হতে পারবো ।
এ প্রসঙ্গে অতি সংক্ষেপে হলেও প্রথমে ইসলামী ‘আক্বাএদে অর্থাৎ ইসলামের তাত্ত্বিক ভিত্তিতে হযরত ইমাম হোসেনের (আ.) মর্যাদা সম্পর্কে আভাস দেয়া প্রয়োজন বলে মনে হয় ।
একজন মানুষের অনেকগুলো মর্যাদা থাকতে পারে এবং তাঁর সবগুলো মর্যাদা সম্বন্ধে সকলের মধ্যে মতৈক্য না-ও থাকতে পারে । তবে হযরত ইমাম হোসেনের (আ.) যে মর্যাদা সম্পর্কে ইসলামের সকল মাযহাব ও ফির্কাহ্ অভিন্ন মত পোষণ করে তা হচ্ছে, তিনি এবং তাঁর বড় ভাই হযরত ইমাম হাসান (আ.) রাসূলে আকরাম হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর আহলে বাইতের সদস্য; অপর দু’জন তাঁদের পিতা-মাতা হযরত আলী (আ.) ও হযরত ফাতেমাহ্ (সা.আ.); এ চারজনের ব্যাপারে এমন কোনো ভিন্ন মত নেই যা এ ব্যাপারে বিন্দুমাত্রও সংশয় সৃষ্টি করতে পারে । আর আহলে বাইতের সদস্যগণ শুধু গুনাহ্ থেকেই মুক্ত নন বরং সকল প্রকার চারিত্রিক ও আচরণগত অপকৃষ্টতা থেকেও মুক্ত (সূরা আল্-আহযাব : ৩৩) ।
পাপমুক্ততার এ দৃষ্টিকোণ থেকে তাঁদের মর্যাদা নবী- রাসূলগণের (আ.) মর্যাদার সমস্তরের । যদিও রাসূলে আকরাম হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর পরে আর কোনো নবী আসবেন না এবং কারো প্রতি নতুন কোনো আয়াত বা শরঈ বিধান নাযিল হবে না, তবে তাঁর ঘোষণা অনুযায়ী তাঁর উম্মাতের ওলামায়ে কেরামের মর্যাদা বানী ইসরাঈলের নবী-রাসূলগণের (আ.) সমান এবং তাঁরা নবী-রাসূলগণের (আ.) উত্তরাধিকারী ও প্রতিনিধি; এ তিনটি মর্যাদা আহলে বাইতের সদস্যদের ক্ষেত্রে শতকরা একশ’ ভাগ প্রযোজ্য । তাই তাঁদের প্রতি দরূদ বর্ষণ ছাড়া আমাদের নামায ও খুতবাহ্ ছ্বহীহ্ হয় না । এ কারণে নামাযের দরূদে বলতে হয় : “হে আল্লাহ্! মুহাম্মাদ ও আলে মুহাম্মাদের (অর্থাৎ আহলে বাইতের) প্রতি দরূদ প্রেরণ করো যেভাবে তুমি ইব্রাহীম্ ও আলে ইব্রাহীমের প্রতি দরূদ প্রেরণ করেছো ... । হে আল্লাহ্! মুহাম্মাদ ও আলে মুহাম্মাদের (অর্থাৎ আহলে বাইতের) প্রতি বরকত নাযিল করো যেভাবে তুমি ইব্রাহীম্ ও আলে ইব্রাহীমের প্রতি বরকত নাযিল করেছো ... ।” আর হাদীছের (তিরমিযী, ইব্নে মাজাহ্, মুস্তাদরাকে হাকেম, কানযুল উম্মাল, ...) ভিত্তিতে খুতবায় আমরা হযরত ইমাম হোসেন ও হযরত ইমাম হাসান (আ.) কে ‘বেহেশতে যুবকদের নেতা’ বলে উল্লেখ করি ।
শুধু তা-ই নয়, হযরত রাসূলে আকরাম (সা.) হযরত ইমাম হাসান ও হযরত ইমাম হোসেনের (আ.) সন্তুষ্টি-অসন্তুষ্টিকে তাঁর সন্তুষ্টি-অসন্তুষ্টি বলে (ইবনে মাজাহ্) এবং তাঁর সন্তুষ্টি-অসন্তুষ্টিতে আল্লাহ্ তা‘আলার সন্তুষ্টি-অসন্তুষ্টি ও বেহেশত-দোযখের পরিণতি বলে (মুসতাদরাকে হাকেম্, হাইছামী, তিবরানী ও কানযুল উম্মাল) উল্লেখ করেছেন । এছাড়া যারা তাঁদেরকে ভালোবাসে তাদেরকে ভালোবাসার জন্য তিনি আল্লাহ্ তা‘আলার কাছে দোআ করেন (তিরমিযী) ।
আল্লাহর রাসূল হযরত ইব্রাহীম্ (আ.) সকল কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার পর আল্লাহ্ তা‘আলা তাঁকে মানব জাতির জন্য ইমাম বা নেতা মনোনীত করেন এবং তাঁর প্রশ্নের জবাবে জানান যে, তাঁর বংশের নেককারদেরও [অর্থাৎ আলে ইব্রাহীমকে তথা তাঁর বংশের নবী-রাসূলগণ ও বিশেষ নেককার লোকদেরকে (আ.)] ইমাম বা নেতা বানানো হলো (সূরা আল্-বাক্বারাহ্ : ১২৪) । অতএব, নামাযের বিশেষ দরূদে আলে ইব্রাহীমের সাথে আলে মুহাম্মাদের তুলনা থেকে উম্মাতের ওপর আলে মুহাম্মাদের দ্বীনী নেতৃত্ব এবং সেই সাথে রাজনৈতিক নেতৃত্বের হক্ব অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয় ।
সংক্ষেপে এই হলো আমাদের আক্বাএদে হযরত ইমাম হোসেন (আ.)-এর বিতর্কাতীত মর্যাদা । আর সাধারণ দৃষ্টিতেও একটি ইসলামী সমাজের নেতৃত্ব ও শাসন-কর্তৃত্ব অর্পিত হতে হবে দ্বীনী জ্ঞান, আচরণ ও যোগ্যতার বিচারে শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তির ওপরে ।
অন্যদিকে বিচারবুদ্ধির রায় অনুযায়ী, ইসলামী সমাজের নেতৃত্ব ও শাসনকর্তৃত্বের ভার সরাসরি আল্লাহ্ তা‘আলার পক্ষ থেকে কারো ওপর অর্পণ করা না হলে বা এরূপ ব্যক্তি সমাজে উপস্থিত না থাকলে এ দায়িত্ব অর্পণের জন্য জনগণের দ্বারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে সম্ভাব্য সর্বাধিক যোগ্যতার অধিকারী কাউকে বেছে নিতে হবে; রাজতন্ত্র, স্বৈরতন্ত্র, ক্ষমতা জবর দখল, জোর করে জনগণের ওপর শাসন-কর্তৃত্ব চাপিয়ে দেয়া, ধোঁকা-প্রতারণা, ষড়যন্ত্র, উৎকোচ প্রদান বা অন্য যে কোনো অনৈতিক পন্থার আশ্রয় নিয়ে রাষ্ট্রক্ষমতা করায়ত্তকরণ তথা ধর্মসম্পর্কহীন (সেক্যুলার) নেতৃত্ব ও শাসন-কর্তৃত্ব ইসলামের দৃষ্টিতে বৈধ নয় । এ সব বিষয়কে বিবেচনায় রাখলে এটা সন্দেহাতীত যে, ইসলামী উম্মাহর ওপর ইয়াযীদের নেতৃত্ব ও শাসনকর্তৃত্ব ছিলো পুরোপুরি অবৈধ ।
অবশ্য সত্যিকারের দ্বীনী নেতৃত্ব অবৈধ নেতৃত্ব ও শাসন- কর্তৃত্বের মোকাবিলায় কখন কোন্ কর্মনীতি অনুসরণ করবেন তা নির্ভর করে স্থান-কাল ও পরিস্থিতির ওপর এবং এ সবের মূল্যায়ন করে তিনি নিজেই তা নির্ধারণ করবেন । স্বয়ং রাসূলে আকরাম হযরত মুহাম্মাদ (সা.) আল্লাহ্ তা‘আলার পক্ষ থেকে নবুওয়াতের দায়িত্বে অভিষিক্ত হবার পর মক্কায় প্রথম তিন বছর গোপনে দ্বীনী দাওআতের কাজ করেন, অতঃপর দশ বছর স্থানীয় কুফরী নেতৃত্বের যুলুম-অত্যাচারের বিরুদ্ধে কোনো রূপ প্রতিরোধে না গিয়ে প্রকাশ্যে দ্বীনের দাওআত দেন এবং এরপর মদীনায় গিয়ে ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠা করেন । আর তাঁর মদীনাহর জীবনের দশ বছরে তাঁকে পরিস্থিতিভেদে যুদ্ধ, সন্ধি, কূটনৈতিক যোগাযোগ ও দাওআত ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের কর্মনীতি অনুসরণ করতে দেখা যায় । পূর্ববর্তী নবী-রাসূলগণের (আ.) অনুসৃত কর্মনীতিও ছিলো অভিন্ন ।
এ বিষয়টির প্রতি এ কারণে বিশেষ দৃষ্টি প্রদান করা প্রয়োজন যে, আমাদের মধ্যে হযরত ইমাম হোসেন (আ.) ও হযরত ইমাম হাসান (আ.) কে দুই ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়; একজনকে অসম সাহসী বীর পুরুষ ও একজনকে খুবই নরম মনের মানুষ গণ্য করা হয়, অথচ আমাদের ‘আক্বাএদে (নামাযের দরূদ ও খুতবাহর ভিত্তিতে) উভয়ের মর্যাদা অভিন্ন । বিষয়টির প্রতি অগভীর দৃষ্টিতে দৃষ্টিপাত করার কারণেই আমরা এরূপ মনে করে থাকি, অথচ হযরত ইমাম হাসান (আ.) তাঁর জীবনে অনেকগুলো যুদ্ধে সশরীরে অংশগ্রহণ করেছিলেন ।
অন্যদিকে মুয়াবীয়া বিশ বছর ব্যাপী রাজত্বকালের দশ বছর পর হযরত ইমাম হাসান (আ.)কে বিষপ্রয়োগে শহীদ করা হয় । তাঁর শাহাদাতের পর আহলে বাইতের এবং তাঁদের ভক্ত-অনুরক্ত- অনুসারীদের নেতৃত্বে আসেন হযরত ইমাম হোসেন (আ.) । কিন্তু তিনি মুয়াবীয়ার শাসনের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য প্রচারে অবতীর্ণ হন নি - যা তিনি ইয়াযীদের বিরুদ্ধে করেছিলেন । এর কারণ তাঁদের দুই ভাইয়ের মধ্যকার চরিত্রবৈশিষ্ট্যের পার্থক্য নয়, বরং পরিস্থিতির পার্থক্য ।
ইসলামের সকল মাযহাব ও ফির্কাহ্ হযরত আলীর (আ.) খেলাফতের বৈধতার ব্যাপারে একমত এবং বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য যে, সাধারণ জনগণের অনুরোধে তিনি খেলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করেন; স্বল্পসংখ্যক লোক তাঁকে খলীফাহ্ বানান নি । এতদসত্ত্বেও মুয়াবীয়া তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন ।
হযরত আলীর (আ.) শাহাদাতের পর শহীদ বৈধ খলীফাহর অনুসারী জনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে হযরত ইমাম হাসান (আ.)কে খলীফাহ্ হিসেবে বরণ করে নেন । কিন্তু মুয়াবীয়া যে কোনো মূল্যে ক্ষমতা দখল করতে বদ্ধপরিকর ছিলেন । ঐ সময় হযরত ইমাম হাসান (আ.)-এর অধীনে চল্লিশ হাজার সৈন্য ছিলো । এমতাবস্থায় তিনি যুদ্ধ করলে সে যুদ্ধে হার-জিত যার যা-ই হতো না কেন, বিপুল সংখ্যক হতাহতের কারণে মুসলমানদের সামরিক শক্তি নিঃশেষ হয়ে যেতো এবং এই সুযোগে রোম সাম্রাজ্য হামলা চালিয়ে খুব সহজেই গোটা ইসলামী ভূ-খণ্ডকে দখল করে নিতো । এ কারণে, ইসলাম ও মুসলমানদের বৃহত্তর কল্যাণ তথা অস্তিত্ব রক্ষার লক্ষ্যে হযরত ইমাম হাসান (আ.) তাঁর বৈধ খেলাফতকে মুয়াবীয়ার হাতে ছেড়ে দেন ।
অবশ্য মুয়াবীয়া লিখিতভাবে এ মর্মে অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়েছিলেন যে, তাঁর পরে হযরত ইমাম হোসেন (আ.) খলীফাহ্ হবেন । কিন্তু তিনি সে অঙ্গীকার রক্ষা করেন নি এবং স্বীয় চরিত্রহীন পুত্র ইয়াযীদকে পরবর্তী খলীফাহ্ তথা যুবরাজ হিসেবে মনোনীত করে যান ।
এতো কিছু সত্ত্বেও হযরত ইমাম হোসেন (আ.) মুয়াবীয়ার বিরুদ্ধে প্রকাশ্য বিরোধিতা ও প্রচারে অবতীর্ণ হন নি । কারণ, সর্বসম্মত বৈধ খলীফাহ্ হযরত আলীর (আ.) বিরুদ্ধে বিদ্রোহ থেকে শুরু করে ইয়াযীদকে যুবরাজ মনোনীত করার মধ্য দিয়ে রাজতন্ত্রের গোড়াপত্তন সহ মুয়াবীয়ার বিভিন্ন রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের বিচার-বিশ্লেষণ করা ও তা বোঝা তৎকালীন পরিবেশে সাধারণ মুসলিম জনগণের পক্ষে সম্ভব ছিলো না এবং তাদেরকে তা বুঝানোও সম্ভব ছিলো না । কারণ, সাধারণ মানুষ জানতো যে, মুয়াবীয়া ছিলেন হযরত রাসূলে আকরাম (সা.)-এর ছ্বাহাবী ও ওয়াহী-লেখকদের অন্যতম এবং দৃশ্যতঃ বাহ্যিক দ্বীনী আমলের ক্ষেত্রে তাঁর মধ্যে কোনো শৈথিল্য ছিলো না । এছাড়া (এবং অংশতঃ এ কারণেও) অনেক ছ্বাহাবীও তাঁর সাথে ছিলেন । তাই হযরত ইমাম হোসেন (আ.) মুয়াবীয়ার বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে রাজনৈতিক বিরোধিতায় ও প্রচারে অবতীর্ণ হলে জনগণের মধ্যে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হতো এবং মুয়াবীয়ার পক্ষে তাঁর বিরাট প্রশাসন ও প্রচারযন্ত্র কাজে লাগিয়ে হযরত ইমাম হোসেন (আ.)কে ক্ষমতালোভী হিসেবে জনগণকে বিশ্বাস করানো সম্ভব হতো । এটাই ছিলো তাঁর নীরবতার কারণ ।
কিন্তু ইয়াযীদ ক্ষমতায় বসার পর পরিস্থিতি পাল্টে যায় । কারণ, ইয়াযীদের অনৈসলামী চরিত্রবৈশিষ্ট্য ছিলো এমনই সুস্পষ্ট যে, জনগণ কখনোই তাকে দ্বীনদার মনে করতো না, ফলে হযরত ইমাম হোসেন (আ.)-এর পক্ষ থেকে তার বিরোধিতায় বিভ্রান্তির কোনো কারণ ছিলো না ।
শুধু তা-ই নয়, এ ক্ষেত্রে হযরত ইমাম হোসেন (আ.)-এর নীরবতাও হতো ইসলামের জন্য বিপর্যয়কর । কারণ, নবী-রাসূলগণের (আ.) সমতুল্য মর্যাদা নিয়েও তিনি যদি কেবল প্রাণ বাঁচানোর লক্ষ্যে নীরব থাকতেন তাহলে এটা সকল মুসলমানের জন্য সুবিধাবাদ ও কাপুরুষতার দৃষ্টান্ত হতো । তাই তিনি স্বল্পসংখ্যক অনুসারী নিয়েও প্রকাশ্যে সত্যের পতাকা উত্তোলন করেন ।
এখানে এ কথাটিও স্মরণ করিয়ে দেয়ার প্রয়োজন রয়েছে যে, হযরত ইমাম হোসেন (আ.) ইয়াযীদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র যুদ্ধ ঘোষণা করেন নি । তিনি কেবল ইয়াযীদের মতো চরিত্রহীন ব্যক্তিকে খলীফাহ্ হিসেবে মেনে নিতে অস্বীকার করেন এবং জনগণের কাছে সত্যকে তুলে ধরেন । তিনি তাঁর বিভিন্ন ভাষণে সুস্পষ্টভাবে বলেন যে, তাঁর আন্দোলন ক্ষমতা দখলের জন্য নয়, বরং তাঁর নানার [রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর] আদর্শ পুনরুজ্জীবিত করা এবং ‘ভালো কাজের আদেশ দান ও মন্দ কাজে নিষেধ করার লক্ষ্যে ।
লক্ষণীয়, হযরত ইমাম হোসেন (আ.) ইয়াযীদের অনুকূলে বাইআত হন নি, অতএব, ইয়াযীদের বিরুদ্ধে তাঁর উত্থানকে বিদ্রোহ বলা চলে না । তিনি যা করেন তা ছিলো জনগণের মধ্যে সচেতনতা ও জাগরণ সৃষ্টির চেষ্টা । অন্য কথায়, তিনি স্বীয় মত প্রচারের মাধ্যমে জনমত গঠনের চেষ্টা চালিয়েছিলেন ।
আজকের দিনে বিশ্বের অধিকাংশ অমুসলিম দেশেও মত প্রকাশের স্বাধীনতা ও সরকারের বিরোধিতা, এমনকি জনমত গঠনের মাধ্যমে সরকার পরিবর্তনের প্রচেষ্টাকে বৈধ গণ্য করা হয় । কিন্তু খলীফাতুল মুসলিমীন হবার দাবীদার ইয়াযীদের স্বৈরাচারী রাজতান্ত্রিক শাসনে সে অধিকারটুকুও স্বীকার করা হচ্ছিলো না ।
এখানে উল্লেখ্য যে, বর্তমান যুগের পার্থিব [সেক্যুলার] রাজনৈতিক বিবেচনায় মুয়াবীয়া অত্যন্ত দূরদর্শী রাজনীতিক ছিলেন, এ কারণে তিনি বুঝতে পারেন যে, হযরত ইমাম হোসেন (আ.)-এর কাছ থেকে জোর করে বাইআত আদায় করতে গেলে তার পরিণতিতে সংঘাত অনিবার্য হয়ে উঠবে । তাই তিনি ইয়াযীদকে হযরত ইমাম হোসেন (আ.)-এর কাছ থেকে বাইআত আদায়ের চেষ্টা করতে নিষেধ করে যান এবং তাঁকে স্বাধীনভাবে ছেড়ে দেয়ার জন্য উপদেশ দিয়ে যান । [স্মর্তব্য, হযরত ইমাম হাসান (আ.) মুয়াবীয়ার হাতে রাষ্ট্রক্ষমতা ছেড়ে দিলেও এ দুই মহান ভ্রাতা আনুষ্ঠানিকভাবে মুয়াবীয়ার অনুকূলে বাইআত হয়েছিলেন বলে কোনো অকাট্য তথ্য পাওয়া যায় না ।]
কিন্তু উদ্ধত অহঙ্কারী ইয়াযীদ তাঁর পিতার উপদেশ উপেক্ষা করে হযরত ইমাম হোসেন (আ.)-এর ওপর চাপ সৃষ্টি করে তাঁর কাছ থেকে বাইআত আদায়ের চেষ্টা করে । এমতাবস্থায় হযরত ইমামের অনুসারীরা জীবন দিয়ে যুদ্ধ করার জন্য প্রস্তুত থাকলেও যেহেতু তাঁর উদ্দেশ্য রাষ্ট্রক্ষমতা ‘দখল করা’ ছিলো না, সেহেতু তিনি রক্তপাত এড়ানোর জন্য রাতের অন্ধকারে মদীনাহ্ ত্যাগ করে মক্কাহর পথে রওয়ানা হন এবং মক্কায় এসে আল্লাহর ঘরের পাশে আশ্রয় নিয়ে তাঁর সত্যপ্রকাশের দায়িত্ব পালন অব্যাহত রাখেন । এ অবস্থায় ইয়াযীদ হজ্বের সমাবেশে ভীড়ের মধ্যে তাঁকে হত্যা করার জন্য গুপ্তঘাতক পাঠায় । হযরত ইমাম হোসেন (আ.) তা জানতে পারেন । কিন্তু তিনি মসজিদুল হারামে বা পবিত্র ‘আরাফাহর ময়দানে তাঁর রক্তপাত হোক তা চান নি । অন্যদিকে কূফা বাসীরা সেখানে গিয়ে তাদেরকে নেতৃত্ব দেয়ার জন্য তাঁকে শত শত পত্র পাঠায় । এমতাবস্থায় তিনি হজ্বের আগের দিন মক্কাহ্ ত্যাগ করে কূফার পথে রওয়ানা হন ।
হযরত ইমাম হোসেন (আ.) কূফার জনগণের চরিত্র বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জানতেন যে, তাদের অঙ্গীকারের ওপর আস্থা রাখা যায় না । কিন্তু যেহেতু কেউ কার্যতঃ অপরাধ না করা পর্যন্ত তাকে অপরাধী গণ্য করা চলে না সেহেতু তিনি তাদের ডাকে সাড়া না দিলে এটা ইসলামী আচরণবিধি অনুযায়ী খারাপ দৃষ্টান্ত হতো এবং যে কারো জন্য যে কারো সাথে কেবল সন্দেহবশে আচরণ করার বৈধতা সৃষ্টি হয়ে যেতো ।
অবশ্য কারবালায় উপনীত হবার পর তাঁর কাছে কূফা- বাসীদের (অল্প কিছু ব্যতিক্রম বাদে) বিশ্বাসভঙ্গের বিষয়টি প্রমাণিত হয়ে যায় । অতঃপর আর তাঁর জন্য কূফায় যাওয়ার নৈতিক বাধ্যবাধকতা থাকে নি । এমতাবস্থায় তিনি অন্যত্র চলে যাবার জন্য প্রস্তুত ছিলেন । কিন্তু স্বীয় তাবেদারদের প্রতি ইয়াযীদের নির্দেশ ছিলো এই যে, হযরত ইমামের (আ.) কাছ থেকে বাইআত আদায় করতে হবে, আর তিনি তাতে সম্মত না হলে তাঁকে হত্যা করতে হবে ।
বলা বাহুল্য যে, হযরত ইমাম হোসেন (আ.)-এর পক্ষে ইয়াযীদের অনুকূলে বাইআত হওয়া সম্ভব ছিলো না । এমতাবস্থায় তিনি নীরবে যালেমের তলোয়ারের নীচে মাথা পেতে দেবেন এটাও ছিলো অচিন্ত্যনীয় । অতএব, এর মানে ছিলো সশস্ত্র প্রতিরোধ । কিন্তু তিনি যুদ্ধ ও রক্তপাতে আগ্রহী ছিলেন না এবং এ জন্য তিনি আসেনও নি । তাই তিনি যেখান থেকে এসেছেন সেখানে ফিরে যাবার বা দেশের সীমান্তের বাইরে হিজরত করার বিকল্প প্রস্তাব দেন ।
কিন্তু ইয়াযীদের বাহিনী তা প্রত্যাখ্যান করে, বরং ইয়াযীদের পক্ষ থেকে যে দুটি বিকল্প দেয়া হয়েছিলো তার ভিত্তিতে তার অনুগত বাহিনী হযরত ইমামের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে । ফলে বাধ্য হয়ে হযরত ইমামকে অস্ত্র হাতে নিতে হয় এবং ইসলামী আদর্শকে সমুন্নত রাখার লক্ষ্যে যে প্রয়োজনে জীবন দিতে হবে তার দৃষ্টান্ত স্থাপন করে এ অসম যুদ্ধে বাহাত্তর জন সঙ্গীসাথী সহ তিনি শাহাদাত বরণ করেন ।
কেবল স্বাধীনভাবে মত প্রকাশ ও সত্য প্রচারের কারণে হযরত ইমাম হোসেন (আ.) ও তাঁর সঙ্গীসাথীদের যেভাবে হত্যা করা হয় তা সমগ্র মুসলিম উম্মাহর চেতনাকে এমনভাবে নাড়া দেয় যে, তা তাদের মধ্যে ঈমানদীপ্ত নতুন প্রাণের সঞ্চার করে এবং ইসলামের ইতিহাসে সত্যের জন্য আত্মত্যাগের এক নতুন ধারা সৃষ্টি করে, শুধু তা-ই নয়, তিনি সমগ্র মানবতার জন্য সংগ্রামী প্রেরণার দৃষ্টান্তে পরিণত হন । তাঁর শাহাদাতের মাধ্যমে তিনি দ্বীনের যে খেদমত আঞ্জাম দিলেন তিনি বেঁচে থাকলে এবং অনুসারীগণ সহ সর্বস্ব বিনিয়োগ করে প্রচারকার্য চালিয়েও তা পারতেন না ।
এ থেকে সুস্পষ্ট যে হযরত ইমাম হোসেন (আ.) যুদ্ধবাজ ছিলেন না, কিন্তু তিনি ছিলেন স্বীয় নীতি-আদর্শ ও লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের প্রশ্নে আপোসহীন । তিনি ছিলেন স্বৈরতন্ত্র ও সুবিধাবাদ - উভয়কে প্রত্যাখ্যানের প্রতীক - অটল পাহাড়ের ন্যায় ।
যারা আল্লাহর যমীনে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠা করতে চান তাঁদেরকে হযরত ইমাম হাসান ও হযরত ইমাম হোসেন (আ.) - উভয় কর্তৃক বিভিন্ন পরিস্থিতিতে অনুসৃত বিভিন্ন কর্মনীতি বিশ্লেষণ করে তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে স্বীয় পরিস্থিতি অনুযায়ী কর্মনীতি নির্ধারণ করতে হবে । কেবল তাহলেই তাঁদের প্রতি আমাদের আন্তরিক ভালোবাসার সার্থকতা ।
প্রকাশ : দৈনিক দিনকাল, ০৬-১১-২০১১
পরিমার্জনঃ ১৭-০১-২০১৩