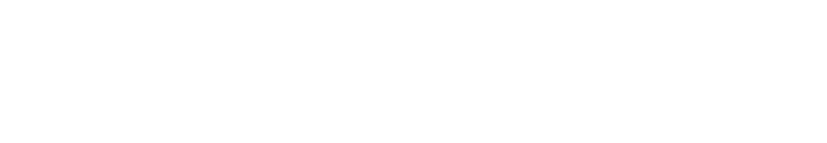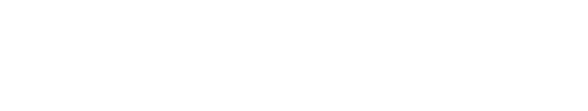জীবনের লক্ষ্য সম্পর্কে পাঁচটি বক্তৃতা
- সৃষ্টির লক্ষ্য;
- ব্যক্তি ও সামাজিক পর্যায়ে নৈতিকতার ভিত্তি;
- বিশ্বাস, বিভিন্ন মতবাদ ও বৈশ্বিক দৃষ্টিভঙ্গি;
- ইসলামী বিশ্বাস এবং মানবীয় পূর্ণতা ও
- ইসলামী একত্ববাদ : উপসংহার।
এ পাঁচটি বক্তৃতা, জীবনের চূড়ান্ত লক্ষ্য- স্রষ্টাকে কেন্দ্র করে আবর্তিত। প্রথম বক্তৃতা একটি ভূমিকা আর শেষটিতে সারসংক্ষেপ ও উপসংহার টানা হয়েছে। প্রথম প্রকাশকের ভূমিকায় এ ভাষণগুলোর প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। এতে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে, ‘আজ মানবজাতির জীবনে এত বেশি তিক্ততা পরিদৃষ্ট হচ্ছে যে, দুঃখ-দুদশা, বেদনা, তা কি জীবনের লক্ষ্য নিরূপণে মানবজাতির ব্যর্থতার পরিণাম নয়?
প্রথম বক্তৃতায় নবী-রাসূলগণের প্রথম লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের প্রেক্ষাপটে উপরিউক্ত প্রশ্ন নিয়ে বিশ্লেষণ করা হয়েছে । এতে দেখা যায়, সৃষ্টির একটি লক্ষ্য রয়েছে যার একটি ‘সৃষ্টি’ হচ্ছে-এর জীবের পক্ষে পূর্ণতা অর্জন- স্রষ্টা যার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন । নবী-রাসূলগণের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য এ বিষয়টির অগ্রগতি সাধন করে বলে স্বীকৃত। ঐশী প্রত্যাদেশের আলোকে সবাইকে আহ্বান করা হয়েছে তার ‘সম্ভাবনা’ অনুধাবন করার এবং তাদের প্রত্যেকের জীবনের লক্ষ্য অর্জন করার- স্রষ্টার উদ্দেশ্যে চূড়ান্ত যাত্রার আগে যা পরিপূর্ণতা লাভ করবে । আর স্রষ্টার কাছে যাবার ব্যাপারটি সকল সৃষ্টির জন্যই অবধারিত।
দ্বিতীয় বক্তৃতায় বা ভাষণে বলা হয়েছে যে, দার্শনিক মতবাদের সাথে আধ্যাত্মিক আদর্শেরও সমন্বয় থাকা প্রয়োজন যাতে ব্যক্তি কিংবা সমাজ সবারই অর্জনের জন্য সামনে কোনো লক্ষ্য থাকে । এখানে বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয় স্রষ্টার প্রতি তাদের সহজাত আধ্যাত্মিক দায়-দায়িত্বের ব্যাপারে (যদি স্রষ্টার অস্তিত্ব না থাকে তাহলে যে যার খুশীমতো চলতে পারে)। মানবজাতির অনন্য বৈশিষ্ট্য- পারস্পরিক সচেতনতার ভিত্তিতে এর পরিসমাপ্তির প্রতি দৃষ্টি দেয়া হয় ।
তৃতীয় ভাষণ থেকে এ ব্যাখ্যাটিই উপস্থাপিত হয়েছে যে, কোনো মতবাদ বা সামাজিক আদর্শে বিশ্বাস অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । এ থেকে প্রেম, আকর্ষণ এবং অন্যান্য গুণ মানবের জীবনে বিকাশ লাভ করে । এ প্রেক্ষাপটে ইসলামের সাথে একত্ববাদের সম্পর্ক বর্ণনা করা হয়, বিশেষ করে চিরন্তন প্রেক্ষাপটে দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ ও মানবতাবাদের গণ্ডি পেরিয়ে তা এগিয়ে যায়।
চতুর্থ ভাষণে মানবীয় পূর্ণতা অর্জনে বিশেষ শক্তি হিসাবে ইসলামী বিশ্বাসকে নিয়ে পরীক্ষা করা হয় । কিছু উপকারী প্রভাব বয়ে আনে বলেই শুধু বিশ্বাস স্থাপনকে আশীর্বাদ রূপে গণ্য করা যায় না; বরং ঐ বিশ্বাস স্থাপনের দাবি হলো নিরবচ্ছিন্নভাবে পূর্ণতার দিকে ধাবিত হওয়া । বস্তুত কিছু উপকার পাওয়া আমাদের জীবনের লক্ষ্য নয় বা লক্ষ্য হওয়াও উচিত নয় । ইবনে সিনার কথায় ‘পারিশ্রমিকের বিনিময়ে কাজ করার অর্থ হচ্ছে বেতন না থাকলে কাজ করার ইচ্ছেও থাকে না ।’ ইবাদাত নিয়ে হযরত আলী (আ.)-এর ভাষায় একটি ইসলামী যুক্তি এভাবে উপস্থাপন করা যায় । তিনি বলেন, ‘হে প্রভু! তোমার জাহান্নামের আগুনের ভয়ে অথবা তোমার জান্নাত পাওয়ার লোভে আমি তোমার উপাসনা করি না । আমি তোমার উপাসনা করি তুমি উপাসনার যোগ্য বলে।’
পঞ্চম ভাষণে মানবীয় পূর্ণতা প্রসঙ্গে সক্রেটিস, প্লেটো, জেনো এবং প্রক্টোরাল দার্শনিকসহ অনান্য মতামত পর্যালোচনা করা হয়েছে । এতে বলা হয় : স্রষ্টা পিতা বা অন্য কোনো ব্যক্তি অথবা পিতৃজাতীয় কোনো সত্তার সাথে তুলনীয় নয় । তিনি তা-ই যা তিনি এবং অন্যান্য সবকিছুরও অধিকারী তিনি । যেরূপ বলা হয়েছে শেখ সা’দীর বুস্তানে :‘বুদ্ধির পথ হচ্ছে একটি গোলক ধাঁধা তবে জ্ঞানীদের জন্য আল্লাহ্ ছাড়া কেউ নেই’।
জ্ঞান, প্রজ্ঞা, বিচারক্ষমতা, সত্য, সৌন্দর্য, স্বাধীনতা এবং অন্যদের প্রতি ভালোবাসা এ সবকিছুই তাঁর বদৌলতে, এমনকি তাঁর (পক্ষ থেকে আমাদের প্রতি) কল্যাণস্বরূপ আরোপিত । ফলে আমাদের প্রতি তাঁর দাবি হচ্ছে সকৃতজ্ঞ স্বীকৃতি-কেবল আনুষ্ঠানিক উপাসনা নয়। নিরবচ্ছিন্নভাবে সচেতন থেকে আমাদের আচার-আচরণ পরিশুদ্ধ করার মধ্য দিয়ে তা পালন করা সম্ভব।
সৃষ্টির লক্ষ্য
অনুসন্ধান করার সময় যে সব মৌলিক সমস্যা সামনে এসে দাঁড়ায় তার অন্যতম হচ্ছে ‘জীবনের লক্ষ্য’। মানুষ সব সময় জানতে চায় সে কেনো বেঁচে আছে এবং তার জীবনের লক্ষ্য কী হওয়া উচিত। ইসলামের দৃষ্টিতে একজন এমনও প্রশ্ন করতে পারে, নবী-রাসূল প্রেরণের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য কী?
নবী-রাসূল পাঠানোর উদ্দেশ্য, যাদের কাছে তাঁদের পাঠানো হয়েছে এমন লোকদের ব্যক্তিগত জীবনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের সাথে বৈসাদৃশ্যপূর্ণ নয় । কারণ, নবী-রাসূলদের পাঠানো হয়েছে নির্দিষ্ট একটি লক্ষ্যের প্রতি সাধারণ মানুষকে ধাবিত করার জন্য । আরও একধাপ এগিয়ে আমরা জিজ্ঞাসা করতে পারি, মানবসহ অন্যান্য প্রাণী সৃষ্টির উদ্দেশ্য কী?
এ বিষয়টির একটি সঠিক বিশ্লেষণ দরকার । এটা হয়তোবা সৃষ্টিতে স্রষ্টার লক্ষ্য বা তাঁর ইচ্ছে- উদ্দেশ্যের প্রকাশ সংক্রান্ত বিষয় । আমরা স্রষ্টার জন্য কোনো লক্ষ্য অনুমান করতে পারি না এবং বিশ্বাস করতে পারি না যে, তিনি কাজের মাধ্যমে কিছু অর্জন করার চেষ্টা করেন । এরকম কোনো ধারণা কর্ম সম্পাদনকারীর একটি ত্রুটি উত্থাপন করে যা ক্ষমতাবান কোনো সৃষ্টি বা প্রাণীর ক্ষেত্রে সত্য, তবে স্রষ্টার জন্য নয়; যেহেতু এর অর্থ দাঁড়ায় তিনি পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হতে চান এবং কিছু নিরাপদ রাখতে চান যা তাঁর নেই । তবে কখনও কখনও ‘সৃষ্টির লক্ষ্য’ বলতে সৃষ্টি কাজের লক্ষ্যকে বোঝায়, স্রষ্টাকে নয় । সেক্ষেত্রে পূর্ণতার উদ্দেশ্যে স্রষ্টার অভিযাত্রার সম্পর্ক পাওয়া যায় । স্রষ্টার নিজের পূর্ণতা নয় । যদি এভাবে আমরা চিন্তা করি যে, স্রষ্টার প্রকৃতি হলো সর্বদা পূর্ণতার অন্বেষণে অগ্রসর হওয়া; আর তখনই আমরা স্রষ্টার একটি উদ্দেশ্য খুঁজে পাই।
ব্যাপারটাও এরকম । সৃষ্ট প্রতিটি সত্তার সামনে অর্জনযোগ্য পূর্ণতার একটি পর্যায় বিরাজ করছে । আর প্রতিটি বস্তুর জন্যই রয়েছে অবনতি বা পূর্ণতার পর্যায়- সর্বোচ্চ সীমায় না পৌছানো পর্যন্ত। ‘মানব সৃষ্টির লক্ষ্য’ সংক্রান্ত প্রশ্নটি এমন এক মৌলিক প্রশ্ন যা ‘মানব স্বভাব’-কেও তুলে ধরে-তার মধ্যে যত প্রতিভা-ই থাকুক বা যত ব্যক্তিগত পূর্ণতা-ই তার জন্য সম্ভব হোক না কেনো । যখন কেউ ঐ পূর্ণতা অর্জন করতে পারে, আমরা তখন বলতে পারি যে, ঐ জন্যই তাকে সৃষ্টি করা হয়েছিল । আপাতঃদৃষ্টিতে মনে হয় ‘মানব সৃষ্টির লক্ষ্য’-কে আলাদা বিষয় রূপে বিশদভাবে আলোচনা করার দরকার নেই । মানুষ কী ধরনের প্রাণী এবং তার মধ্যে কী ক্ষমতা আছে এ টুকু জানাই যথেষ্ট । অন্য কথায় আমাদের দেখা উচিত ইসলাম কীভাবে মানব ও তার সক্ষমতার বিষয়টি তুলে ধরে। কেননা,
আমরা দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি নয়; বরং ইসলামের প্রেক্ষাপটে এ বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করতে চাই।
স্বভাবতঃই নবী-রাসূলদের উদ্দেশ্যও ছিল মানুষকে পূর্ণতা উপহার দেয়া এবং তার সব দোষ-ত্রুটি দূর করা-যা ব্যক্তিগতভাবে তার অথবা তার সমাজের পক্ষে সম্ভব নয় । কেবল ঐশী প্রত্যাদেশের সাহায্যেই মানব সমাজ সে পূর্ণতার দিকে এগিয়ে যেতে সক্ষম হয় ।
অনুরূপভাবে প্রত্যেক ব্যক্তির দেখা উচিত তার মধ্যকার সম্ভাব্য ক্ষমতা অনুধাবনের পর সে কী হতে পারে, যাতে তা বাস্তবায়ন সম্ভব হয় । আর এটাই আমাদের জীবনের লক্ষ্য । এতক্ষণ এ বিষয়কে সাধারণভাবে তুলে ধরা হলো । এখন আমরা বিস্তারিত আলোচনায় যাবো : কুরআনে কি মানবের লক্ষ্য নিয়ে কিছু বলা হয়েছে অথবা এতে মানব সৃষ্টির লক্ষ্য বা নবী-রাসূল প্রেরণের কোনো কারণ ব্যাখ্যা করা হয়েছে ? প্রায়ই বলা হয়ে থাকে, সুখ অন্বেষণের জন্যই মানবের সৃষ্টি এবং মানব-সৃষ্টি থেকে স্রষ্টা কোনো উপকার চান না বা পান না । প্রকৃতপক্ষে মানবকে তার পথ মুক্তভাবে বেছে নেয়ার সুযোগ দেয়া হয়েছে; তার প্রতি নির্দেশিকা আসলে দায়িত্ব ও বিশ্বাস মাত্র, এটা বাধ্যতামূলক বা স্বভাবজাত নয় । তাই যেহেতু সে স্বাধীন, তার উচিত সঠিক পথ বেছে নেয়া । পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে, ‘আমরা মানুষকে পথ দেখিয়েছি, হয় সে কৃতজ্ঞ হবে বা অকৃতজ্ঞ হবে।’ (সূরাদাহর : ৩)
কিন্তু পবিত্র কুরআন অনুসারে ‘সুখ’ কী? প্রায়ই বলা হয়, মানব সৃষ্টি এবং নবী-রাসূল প্রেরণের উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষকে জ্ঞান অর্জন ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হতে শক্তিশালী করা যাতে সে অনেক বেশি শিখতে পারে এবং তার যা দরকার তা অর্জনের ক্ষমতা করায়ত্ত করতে পারে।
এভাবে একটি বীজ সৃষ্টির উদ্দেশ্য হচ্ছে তার সম্ভাবনার বাস্তবায়ন ঘটিয়ে একটি পূর্ণ বৃক্ষে রূপায়ন করা । আবার একটি মেষশাবকের তৃণভোজন ও বিকাশের মধ্য দিয়ে পূর্ণবয়স্ক মেষ হওয়া- এ রূপান্তর সৃষ্টির একটি উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করে (মানবের জন্য উপযোগী)। মানুষের ক্ষমতা আরও উন্নত পর্যায়ের । মানুষ মানেই সে জ্ঞানী-সক্ষম । সে যত বেশি জানতে পারে তত বেশি তার জ্ঞান কাজে লাগাতে পারে, আর ততই সে তার লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের নিকটবর্তী হয় ।
কখনও বলা হয়, মানব জীবনের লক্ষ্য হচ্ছে ‘সুখ’ লাভ করা । অর্থাৎ যতটা সময় একজন মানুষ বেঁচে থাকবে সে সুখে-শান্তিতে জীবন কাটাবে, প্রকৃতি ও স্রষ্টার কল্যাণ উপভোগ করবে, প্রকৃতি বা অন্যান্য প্রাণীর ক্ষতি থেকে কম দুঃখ-দুর্দশা ভোগ করবে । একেই বিবেচনা করা হয় ‘সুখ’। অর্থাৎ সর্বোচ্চ পরিমাণ ‘সুখ’ আর সর্বনিম্ন পরিমাণ দুঃখ-বেদনা-ই হলো সুখ।
এটাও বলা হয়, নবী-রাসূলদেরও পাঠানো হয়েছে যাতে মানুষের পক্ষে সবচেয়ে বেশি পরিমাণ সুখ অর্জন ও ন্যূনতম দুঃখ-কষ্ট পাওয়া সম্ভব হয় । যদি নবী-রাসূলগণ পরকালের পরিচয় দিয়ে থাকেন তা হবে এ জীবনেরই ধারাবাহিকতা । অন্য কথায় যেহেতু মানব-সুখের পথ দেখানো হয়েছে এবং তা অনুসরণের পরিণামরূপে পুরস্কারও প্রয়োজন; আবার এর বিপরীতে শাস্তির ও বিধান থাকা প্রয়োজন, তাই এ পৃথিবীতেই এ শাস্তি ও পুরস্কারের মডেল উপস্থাপিত হয়েছে । ফলে এ পৃথিবীর আইন-কানুন বিফল হবে না । যাহোক, নবী-রাসূলগণ এ পৃথিবীতে পুরস্কার বা শাস্তি দেবার মতো কোনো অবস্থানে ছিলেন না; তাই অন্য একটি জগৎ দরকার যেখানে ভালো লোকরা পুরস্কার লাভ করবে, আর অপরাধী ও পাপীরা শাস্তি ভোগ করবে।
কিন্তু আমরা পবিত্র কুরআনে এরকম কোনো কথা দেখতে পাই না । সেখানে জ্বীন ও মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্য রূপে বলা হয়েছে ‘উপাসনা করা’। (সূরা যারিয়াত : ৫৬) মনে হচ্ছে এটা উপলব্ধি করা খুব কঠিন । স্রষ্টার উপাসনায় লাভ কী? এতে তাঁর (স্রষ্টার) কিছু যায়-আসে না । মানুষেরই বা এতে কী লাভ? তবে সৃষ্টির লক্ষ্য হিসাবে পবিত্র কুরআনে এ বিষয়টিকে স্পষ্ট ভাষায় তুলে ধরা হয়েছে । পরবর্তী জীবন এ জীবনের মতো অতটা গুরুত্ববহ নয়-এমন ধারণার বিপক্ষে পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে, ‘তোমরা কি ধরে নিয়েছ তোমাদের এমনিতেই সৃষ্টি করা হয়েছে?’ (সূরা মুমিনূন : ১৫৫) এতে প্রমাণ মেলে সবকিছু প্রজ্ঞাপূর্ণভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে।
এমন ধারণা করা হয়ে থাকে যে, সৃষ্টির কোনো অর্থ হয় না, আর মানুষও স্রষ্টার সামনে ফিরে যাবে না! পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে সৃষ্টির উপযুক্ততা প্রসঙ্গে পরকালের কথা বারবার ঘোষণা করা হয়েছে । এর যৌক্তিকতার ভিত্তি এরূপ- এ পৃথিবীর একজন স্রষ্টা আছেন, তিনি কোনো কিছুই বৃথা সৃষ্টি করেন না এবং যা করেন সবই সঠিক- খেলার জন্য নয় এবং তাঁর কাছেই ফিরে যেতে হবে যিনি সমস্ত বিশ্বজগতের খবর রাখেন । আমরা পবিত্র কুরআনে এমন কথা পাই না যে, মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে যাতে সে বেশি বেশি জানতে পারে, ফলে তার লক্ষ্য অর্জনের জন্য বেশি করে কাজ করতে পারে । তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে ইবাদাত করার জন্য, আর স্রষ্টার উপাসনা নিজেই একটি লক্ষ্য । যদি স্রষ্টাকে জানার বা চেনার কোনো প্রয়োজন না থাকতো-যা ইবাদাত করার ক্ষেত্রে প্রথম পদক্ষেপ, তাহলে সৃষ্টির লক্ষ্যপানে অভিযাত্রায় মানুষ ব্যর্থ হয়ে পড়তো আর আল-কুরআনের দৃষ্টিতে সে সুখী হতো না । পয়গাম্বরগণও এসেছেন তাকে সুখের দিকে এগিয়ে নেবার জন্য- যা কিনা স্রষ্টার ইবাদাত ।
সুতরাং ইসলাম যে লক্ষ্য বা আদর্শের কথা বলে তা হলো স্রষ্টা এবং বাকী সবকিছুই এ লক্ষ্যে পৌঁছার প্রস্তুতিমাত্র- স্বয়ংসম্পূর্ণ নয় বা মৌলিকভাবে গুরুত্ববহও নয় । পবিত্র কুরআনের যে সব আয়াতে পূর্ণ মানবের কথা বলা হয়েছে বা তাদের পক্ষে বলা হয়েছে সে সব আয়াতে এরশাদ করা হয়েছে যে, তারা সত্যিকার অর্থে জীবনের লক্ষ্য বুঝতে পেরেছে এবং তা অর্জনের জন্য কঠোর পরিশ্রম করেছে । হযরত ইবরাহীম (আ.) সম্পর্কে বলা হয়েছে :
‘আমার ইবাদাত তাঁর জন্য উৎসর্গীকৃত, যিনি বেহেশত ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, আরআমি অবিশ্বাসী নই।’ (সূরা আনআম : ৮০)
এ সূরায় আরও বলা হয় :
‘আমার নামায, ইবাদাত, জীবন ও মৃত্যু আল্লাহর জন্য যিনি সমস্ত বিশ্বজাহানের মালিক।’ (সূরা আনআম : ১৬৩)
কুরআনের এ একেশ্বরবাদিতা কেবল একটি বুদ্ধিদীপ্ত বিষয় নয় যাতে ধারণা হয় বিশ্ব জাহানের উৎস একটি, আর সৃষ্টি আরেক ভিন্ন সত্তা । এখানে মানুষের বিশ্বাস ও দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত হয়েছে যে, স্রষ্টা শুধু একজন এবং তার (মানুষের) লক্ষ্য (তার কাছে মূল্যবান একমাত্র লক্ষ্য) কেবলই ঐ স্রষ্টা । অন্য সব লক্ষ্য এ প্রধান লক্ষ্যের উপজাত ও ঐ লক্ষ্য অর্জনের সহযোগী মাত্র।
এভাবে ইসলামে সবকিছুই স্রষ্টাকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয় । পয়গাম্বরগণের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য এবং ব্যক্তি পর্যায়ের জীবনের লক্ষ্যও এর অন্তর্ভুক্ত।
এবার আমরা ইবাদাত প্রসঙ্গটি নিয়ে পর্যালোচনা করব । দ্বিতীয় আয়াতে ইবরাহীম (আ.)-এর কথায় সর্বাত্মক আনুগত্য প্রকাশ পেয়েছে এবং তিনি নিজেকে সার্বক্ষণিকভাবে স্রষ্টার অনুগত দাস রূপে তুলে ধরেছেন, যিনি অন্য কোনো চিন্তা-ভাবনা নয়; বরং শুধুই স্রষ্টা কর্তৃক চালিত হন । পয়গাম্বরগণের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে বেশ কয়েকটি ব্যাখ্যা পাওয়া যায় । সূরা আহযাবের ৪৫ এবং ৪৬ নং আয়াতে বলা হয়েছে :
‘হে নবী! আমরা আপনাকে পাঠিয়েছি সাক্ষ্যদাতা, সুসংবাদদাতা এবং সতর্ককারীরূপে এবং আল্লাহর আদেশক্রমে তাঁর দিকে আহ্বায়ক রূপে এবং উজ্জ্বল প্রদীপরূপে।’
কাজেই একজন নবী হচ্ছেন সাধারণ মানুষের কর্মের সাক্ষী, ভালো কাজের সুসংবাদদাতা; মন্দ কাজের ব্যাপারে সতর্ককারী প্রতিনিধি এবং একজন মানুষ যিনি সাধারণ মানুষকে স্রষ্টার দিকে আহ্বান করেন- যা হচ্ছে চূড়ান্ত লক্ষ্য ।
অন্য এক জায়গায় নবী-রাসূলগণের লক্ষ্য হিসাবে বলা হয়েছে অন্ধকার থেকে মানুষকে আলোর দিকে এগিয়ে নেয়ার দায়িত্ব পালন । সুতরাং এটা পরিস্কার, মানবজাতিকে আল্লাহকে চিনতে আহ্বান করা হয়েছে, আর নবী-রাসূলগণ হচ্ছেন স্রষ্টা ও সৃষ্টির মধ্যে যোগসূত্র।
আরেকটি আয়াতে নবী-রাসূলগণের লক্ষ্য-উদ্দেশ্যরূপে অন্য একটি বিষয় তুলে ধরা হয়েছে : ‘সত্যই আমরা নবী-রাসূল পাঠিয়েছি সুস্পষ্ট প্রমাণসহ এবং তাদের সাথে আমরা কিতাব পাঠিয়েছি এবং সত্য পরিমাপ, যাতে মানুষ ন্যায়বিচারে উদ্বুদ্ধ হয় এবং আমরা লৌহ পাঠিয়েছি যাতে রয়েছে কঠিন দৃঢ়তা এবং মানুষের জন্য কল্যাণ...’ (সূরা কিয়ামাহ : ২৫)
এ আয়াতে ‘পরিমাপ’ বলে সম্ভবত ‘আইন’ বুঝানো হয়েছে যাতে ন্যায়বিচার নিহিত রয়েছে । এভাবে নবী-রাসূলগণ ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং এটা তাদের লক্ষ্যের আরেকটি দিক ।
কেউ কেউ, যেমন ইবনে সিনা যুক্তি দেখান বৈষম্যহীন আইন ছাড়া মানব সমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয় । আর এমন আইন দু’টি কারণে মানুষের পক্ষে রচনা করা সম্ভব নয় । প্রথমত মানুষ সম্পূর্ণরূপে সত্যকে চিহ্নিত করতে পারে না অথবা ব্যক্তিগত পক্ষপাত থেকে সে মুক্ত হতে পারে না । দ্বিতীয়ত এটা বাস্তবায়নের কোনো নিশ্চয়তা নেই; কারণ, মানুষের প্রকৃতিই তাকে একে অন্যের ওপর প্রাধান্য দিতে বাধ্য করে । তাই আইন-কানুন যখন তার পক্ষে, সে তা গ্রহণ করে, আর যখন তার স্বার্থের পরিপন্থী তখন সে তা প্রত্যাখ্যান করে ।
একটা আইন এমন হওয়া উচিত যার প্রতি মানুষ শ্রদ্ধাশীল হবে আর এমন আইন অবশ্যই স্রষ্টা কর্তৃক রচিত হবে যার প্রতি চেতনার গভীর থেকে মানুষ অনুগত হবে । এমন উপযুক্ত আইন আসবে স্রষ্টার কাছ থেকে এবং তা বাস্তবায়নে পুরস্কারের নিশ্চয়তা থাকবে; অমান্য করায় শাস্তিও নির্ধারিত থাকবে, এর প্রতি মানুষের বিশ্বাসও থাকবে; তারা স্রষ্টাকে চিনতে পারবে । এভাবে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার পূর্বশর্ত রূপে স্রষ্টাকে চেনার অনেক উপাদান ও কার্যকারণ বিদ্যমান । এমনকি ইবাদাতও নির্ধারণ করা হয়েছে যাতে এ আইন প্রণেতাকে মানুষ ভুলে যেতে না পারে । এ ছাড়াও প্রতি মুহূর্তে সর্বদর্শীরূপে স্রষ্টাকে মনে রাখবে । এ যুক্তিতে মানুষকে স্রষ্টার প্রতি আহ্বান করা আরেকটি লক্ষ্য, নচেৎ তাঁকে (স্রষ্টাকে) চেনার কোনো উদ্দেশ্য থাকে না ।
এভাবে আমরা তিন প্রকার যুক্তি পেয়ে থাকি । প্রথমটি হচ্ছে, নবী-রাসূলদের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য হলো এ জগতে কেবল জনসাধারণের মধ্যে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা এবং তাদের জন্য সুখী-সমৃদ্ধ জীবন নিশ্চিত করা । ফলে স্রষ্টাকে চেনা, তাঁর ওপর বিশ্বাস রাখা ও পরকালে বিশ্বাস রাখা হচ্ছে পূর্বোক্ত লক্ষ্যের পূর্বশর্ত । দ্বিতীয় যুক্তি প্রায় বিপরীতধর্মী । স্রষ্টাকে চেনা, তাঁর উপাসনা করা হচ্ছে প্রধান উদ্দেশ্য, আর ন্যায় বিচার হচ্ছে এর পরিপূরক । এ জগতে মানুষের আধ্যাত্মিকতা সমাজ-জীবনের ওপর নির্ভরশীল, আর আইন ও ন্যায়বিচার ছাড়া সমাজ-জীবন সম্ভব নয় । তাই আইন ও ন্যায়বিচার হচ্ছে স্রষ্টার প্রতি উপাসনার পূর্বশর্ত । সুতরাং সামাজিক সমস্যাদি দূরীকরণ, যা আজ ন্যায়বিচার প্রসঙ্গে অত্যন্ত গুরুত্ববহরূপে বিবেচিত তা নবী-রাসূলদেরও উদ্দেশ্য ছিল তবে তা গুরুত্বের দিক দিয়ে দ্বিতীয় পর্যায়ে থেকে যায়।
তৃতীয় মত অনুসারে নবী-রাসূলদের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য আলাদা হওয়া প্রয়োজন সৃষ্টি ও জীবনের লক্ষ্য থেকে । আর তাই এর একটি হবে প্রধান লক্ষ্য, আর অন্যটি হবে পরিপূরক । আমরা বলতে পারি, নবী-রাসূলগণের দু’টি স্বতন্ত্র লক্ষ্য ছিল : একটি হলো স্রষ্টার উপাসনা করার জন্য মানুষ ও স্রষ্টার মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন; অন্যটি হলো সাধারণ মানুষের মধ্যে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা । কাজেই এর একটি অন্যটির পূর্বশর্ত হবে এমন ধারণা আমরা অগ্রাহ্য করতে পারি ।
পবিত্র কুরআনে এর উদাহরণ পাওয়া যায়, যেখানে আত্মশুদ্ধির ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে আর পরিত্রাণপ্রাপ্তি এর ওপর নির্ভরশীল বলে বর্ণনা করা হয়েছে। আত্মশুদ্ধি কি ইসলাম সমর্থিত একটি লক্ষ্য? এটা কি একটি লক্ষ্য না কি পূর্বশর্ত? কিসের পূর্বশর্ত? স্রষ্টাকে চেনার এবং তাঁর সাথে সংযোগ স্থাপনের এবং তাঁর ইবাদাত করার নাকি সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার? এ মতানুসারে, যেহেতু নবী-রাসূলগণ সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য নিয়ে এসেছেন, তাই সামাজিক কল্যাণ- অকল্যাণ চিহ্নিত হয়েছে । তাঁরা উপদেশ দিয়েছেন সামাজিক অকল্যাণ পরিহার করার; যেমন ঈর্ষা, অহংকার, স্বার্থপরতা, কামুকতা ইত্যাদি পরিহার করার; আর ভালো গুণাবলী, যেমন সত্যবাদিতা, পুণ্যকর্ম, সহানুভূতি, বিনয় ইত্যাদি লালন করার । অথবা এটা দাবি করা ঠিক হবে যে, আত্মশুদ্ধি নিজেই একটি স্বতন্ত্র লক্ষ্য?
ওপরের এ মতগুলোর কোনটি গ্রহণযোগ্য? আমাদের চিন্তার প্রতি কুরআন কখনও কোনো অবস্থাতেই দ্বৈততা অনুমোদন করে না । কুরআন সকল অবস্থাতেই একটি একেশ্বরবাদী ধর্মগ্রন্থ । এতে বলা হয়েছে ‘স্রষ্টার মতো বা তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই।’ (সূরা শূরা : ১১)
এতে সকল গুণের চূড়ান্ত পূর্ণতা স্রষ্টার বলে বর্ণনা করে- ‘সকল উত্তম নাম তাঁর।’ (সূরা
ত্বহা : ৬০) ‘সর্বোত্তম মর্যাদাপূর্ণ গুণরাজি শুধুই স্রষ্টার।’ (সূরা নাহল : ৬০)
কুরআন ঘোষণা দেয় তাঁর কোনো শরীক নেই, কোনো প্রতিপক্ষ নেই এবং সকল ক্ষমতা তাঁর, অন্য কারও নয় । কুরআন স্রষ্টা ছাড়া আর কোনো লক্ষ্যকেই মৌলিক, স্বতন্ত্র বা বিশ্বজগতের চূড়ান্ত লক্ষ্য বলে অনুমোদন দেয় না, মানুষের জন্যও স্রষ্টা ছাড়া আর কোনো লক্ষ্যকেই মানুষের সৃষ্টি তার বাধ্যতা এবং কর্মের লক্ষ্য হিসাবে স্বীকার করে না।
এখানেই যে মানুষ ইসলাম চায়, আর যে শুধুই দার্শনিক ধারণায় বিশ্বাসী তার মধ্যে সকল ব্যবধান বিরাজ করে । ইসলাম সমর্থন করে এমন অনেক বিষয় অন্যরাও সমর্থন করে, তবে ভিন্ন প্রেক্ষাপটে । ইসলাম সব সময় একেশ্বরবাদী প্রেক্ষাপটেই সবকিছু বিবেচনা করে।
দর্শনে, যেমন আমরা আগে বলেছি, মানুষ এমন এক পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, সে বলে: এ বিশ্বজগৎ এতটি ধারাবাহিক অপরিবর্তনীয় নিয়মে চালিত হচ্ছে । পবিত্র কুরআনও একই কথা বলে, কিন্তু ঐশী প্রেক্ষাপটে : ‘আপনি কখনও স্রষ্টার নিয়মে পরিবর্তন পাবেন না।’ (সূরা সাবা : ৪৩)
পবিত্র কুরআন শুধু সামাজিক ন্যায়বিচারের নীতি গ্রহণ করে তা নয়; বরং তাকে অত্যন্ত গুরুত্ববহরূপে বিবেচনা করে যদিও চূড়ান্ত লক্ষ্য বা ইহজাগতিক সুখ বলতে যা বুঝি তার পূর্ব শর্তরূপে অনুমোদন দেয় না । ইসলাম ইহজাগতিক সুখকে গ্রহণ করে একেশ্বরবাদিতার বাস্তবধর্মী সীমারেখার গণ্ডিতে থেকে অর্থাৎ পূর্ণরূপে স্রষ্টার প্রতি অনুগত থাকাকে সুখ বলে চিহ্নিত করে । কুরআন অনুযায়ী মানুষ কেবল স্রষ্টার কাছ থেকেই সুখ পায় এবং তিনিই তার জীবনের সমস্ত অপূর্ণতা পূর্ণ করে দেন এবং তাকে তৃপ্ত করেন । কুরআনে বলা হয়েছে : ‘তারা যাদের বিশ্বাস আছে এবং স্মরণে যাদের হৃদয় প্রশান্ত হয়; জেনে রাখ, আল্লাহর স্মরণেই চিত্ত প্রশান্ত হয়।’ (সূরা রাদ : ২৪)
মানুষের উদ্বিগ্ন ও অস্থির হৃদয়ে কেবল স্রষ্টা-ই প্রশান্তি দেন । অন্যান্য বিষয় পরিপূরক ও প্রাথমিক; চূড়ান্ত পর্যায় নয়। ইবাদাত প্রসঙ্গে এরূপ বলা হয়েছে : ‘স্রষ্টার স্মরণে, প্রার্থনা করা।’ (সূরা ত্বহা : ১৪)
অন্য আয়াতে বলা হয়েছে : ‘প্রার্থনা পাপ ও অন্যায়কে প্রতিরোধ করে, আর স্রষ্টার স্মরণ আরও গুরুত্বপূর্ণ।’
ইসলাম অনুযায়ী মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে স্রষ্টার ইবাদাতের উদ্দেশ্যে- তাঁর নৈকট্য লাভের জন্য এবং তাঁকে চেনার জন্য, এর সবকিছুই তাকে ক্ষমতাবান করে । তবে জ্ঞান বা ক্ষমতা যেমন, তেমনি আত্মশুদ্ধিও চূড়ান্ত লক্ষ্য নয় ।
ব্যক্তিগত ও সামাজিক নৈতিকতার ভিত্তি
ব্যক্তিগত বা সামাজিক যে কোনো জীবনেই মানুষের কতকগুলো অবস্তুগত উদ্দেশ্য রয়েছে। প্রতিটি সমাজ ব্যবস্থায় কতকগুলো উদ্দেশ্য প্রয়োজন যা ব্যক্তিগত পর্যায়ের লক্ষ্যের অনুরূপ এবং যা ছাড়া সত্যিকার অর্থে সমাজ-জীবন গড়ে তোলা অসম্ভব । কাজেই সামাজিক জীবনের অর্থ হলো বস্তুগত ও আধ্যাত্মিক-উভয় ক্ষেত্রে অভিন্ন লক্ষ্য অর্জনে সহযোগিতা ।
কিছু সংখ্যক লোকের অভিন্ন লক্ষ্য বস্তুগত হতে পারে, যেমন বাণিজ্যিক বা শিল্প সংস্থা, যা বেশ কিছু সংখ্যক লোক মিলে গঠন করে যাদের কেউ মূলধন বিনিয়োগ করে, অপর কেউ শ্রম দিয়ে থাকে । কিন্তু মানব সমাজ একটি কোম্পানির মতো পরিচালনা করা সম্ভব নয়, যেহেতু এর ভিত্তি একটি সংগঠনের ভিত্তি থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন । অবশ্য এটা আমাদের ধারণা । আরও অনেকে আছেন, যেমন বার্ট্রান্ড রাসেল মনে করেন সামাজিক নীতি-নৈতিকতার ভিত্তি ব্যক্তিগত স্বার্থে নিহিত । তাঁরা সামাজিক নৈতিকতাকে ব্যক্তিবর্গের মধ্যকার চুক্তিরূপে গণ্য করেন, যার উদ্দেশ্য হচ্ছে তাদের নিজস্ব স্বার্থ নিরাপদ রাখা । এ বিষয়টির ব্যাখ্যায় রাসেল উদাহরণ দিয়েছেন- ‘আমি চাই আমারপ্রতিবেশীর গাভীটিও আমার হোক । কিন্তু আমি বুঝি, যদি আমি এরূপ করি, প্রতিক্রিয়ায় সেও আমার গাভীটি ছিনিয়ে নেবে। অন্য এক প্রতিবেশীও অনুরূপ কিছু করতে পারে । ফলে লাভের বদলে আমার লোকসান হবে । কাজেই আমার বিবেচনায় তার অধিকারের প্রতি সম্মান জানানোই ভালো । তাই সে তার গাভীটি নিজের করে রাখুক আর আমিও যাতে আমারটিকে...
রাসেল বিশ্বাস করেন, সামাজিক নীতি-নৈতিকতার ভিত্তি ব্যক্তি পর্যায়ের অধিকার প্রসঙ্গে পারস্পরিক সম্মান প্রদর্শন । আমরা এটাও তো বলতে পারি, চোরদের মধ্যেও এরকম সম্পর্ক বজায় আছে। একসঙ্গে তারা চুরি করবে এবং নিজেদের মধ্যে এক প্রকার ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করবে, যেহেতু তারা একা একা এ কাজ করতে পারে না । তাই আমরা বলতে পারি, রাসেলের নীতি তাঁর দর্শনের সাথেই খাপ খায় না । তাঁর নীতি মানবতাবাদী; কিন্তু তাঁর দর্শন এর বিপরীতে ব্যক্তি স্বার্থকে সামাজিক নীতি-নৈতিকতার ভিত্তিরূপে বিবেচনা করে । তাঁর মতানুযায়ী ব্যক্তি পর্যায়ে অন্যকে সহযোগিতা করা বাধ্যতামূলক । কেননা, ঐ ব্যক্তি প্রতিক্রিয়ার ভয়ে ভীত- যদি তাদেরও একই রকম ক্ষমতা ও শক্তি থাকে ! তবে কেউ যদি নিশ্চিত হয় সে এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, অন্যরা অনেক দুর্বল এবং তারা তার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না তখন তার ওসব সামাজিক রীতি-নৈতিকতা মেনে চলার দরকার পড়ে না ।
যেমন ধরা যাক নিক্সন এবং ব্রেজনেভ সমান ক্ষমতাবান । একে অন্যকে মোকাবেলায় তাঁরা হিসাব করে দেখলো যে, পরস্পরের প্রতি সম্মান দেখালে তাঁদেরই লাভ । তবে তাঁদের কেউ যদি একটি দুর্বল হাতিকে সামনে পায় তখন এরকম সম্মান দেখানোর কোনো দরকার পড়ে না । তখন ভিয়েতনামে যুক্তরাষ্ট্রের লড়াই নিয়ে রাসেলের সমালোচনা অগ্রহণযোগ্য হয়ে যায়!
সবক্ষেত্রেই তাঁদের ধারণা বিবেচনাহীন । যেমন তাঁদের ধারণামতে ক্ষমতাবান কেউ দুর্বলদের সংযত রাখবে । যদি দুর্বলের সংযত হবার মতো সহনশীলতা না থাকে তবে তারা শক্তিশালী হবার চেষ্টা করবে । রাজনৈতিকভাবে এটা সত্য হতে পারে, তবে নীতি-নৈতিকতা প্রশ্নে গ্রহণযোগ্য নয় । কারণ, দুর্বল কোনোক্রমেই সবলকে অন্য কোনোভাবে মোকাবেলায় সক্ষম নয় । রাজনৈতিক মতবাদে মনে হয় এটা অনুমোদনযোগ্য যে, সবল মধ্যপন্থী আচরণ করবে । যে কোনো মতবাদই এ রকম বস্তুগত লক্ষ্য অর্জনের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠা পেতে পারে, তবে বঞ্চনা রুখে দেবার মতো অন্যান্য পথও নির্দেশ করা উচিত । ব্যক্তিগত আগ্রাসনের কারণ অনুসন্ধান ও তা দূর করার কথা বলে এ কারণগুলোকে অহেতুক মানবিক বা বুদ্ধিবৃত্তিক বা শিক্ষামূলক সীমাবদ্ধতার সাথে সম্পর্কযুক্ত করা হয়েছে ।
যদি আপনি জিজ্ঞাসা করেন দুর্বলের বিপক্ষে সবলের আগ্রাসন মোকাবেলায় কী বাধা রয়েছে । তাঁরা হয়তো বলবেন : সমাজ প্রথম থেকেই এমনভাবে বিনির্মাণ করতে হবে যে, সেখানে কোনো সবল বা দুর্বল লোক থাকবে না । যদি শক্তি বা দুর্বলতার উৎস চিহ্নিত ও দূর করা যায়, তাহলে সব মানুষ একই পর্যায়ের হবে এবং সমান ক্ষমতার কারণে তারা একে অন্যকে সম্মান করবে । তাঁদের মতে এটা করা সম্ভব সম্পদের ব্যক্তি মালিকানাধীন ব্যবস্থা উচ্ছেদ করে । মালিকানাধীনের দশা থেকে মুক্তি লাভে মানবিক বৈষম্য দূর হবে এবং এমন একটি সমাজ হবে যেখানে সব মানুষের একটি বস্তুগত সাধারণ লক্ষ্য থাকবে এবং তা একটি প্রকৃত সমিতির মতো পরিচালিত হবে যেখানে কোনো অবিচার থাকবে না।
মার্কসীয় মতবাদ প্রায় এরকমই একটি ধারণা যেখানে মানুষের জন্য আধ্যাত্মিকতার কোনো সুযোগ নেই, নেই নীতি-নৈতিকতা সংক্রান্ত কোনো কথা । তারা গুরুত্ব আরোপ করে শুধু ‘মালিকানা’-এর ওপর, যা তাদের ধারণামতে সকল শোষণ ও অপরাধের উৎস । ব্যক্তিমালিকানা রাষ্ট্রীয় বা সামাজিক মালিকানায় রূপান্তরিত, যাতে প্রত্যেক মানুষ তার সাধ্য অনুযায়ী পরিশ্রম করে এবং তার প্রয়োজনঅনুযায়ী রাষ্ট্র বা সমাজ থেকে সে পারিশ্রমিক পায় । এমন ব্যবস্থাকে শান্তি, স্থিতিশীলতা, ন্যায়বিচার ও নীতি প্রতিষ্ঠায় স্বাভাবিকভাবে সহায়ক মনে করা হয় । সব সমস্যা, যেমন শক্রতা, ঘৃণা এবং অন্যান্য জটিলতা তখন আশা করা যায় দূর হবে এবং সবাই সাম্য ও ভ্রাতৃত্ববোধে বসবাস করবে ।
কিন্তু এর সবটাই ভুল এ কারণে যে, বাস্তবে দেখা গেছে, সমাজে ব্যক্তিমালিকানা ব্যবস্থা উচ্ছেদ করা হয়েছে, কিন্তু সেখানে শোষণ এবং বিভাজন অব্যাহত আছে । যদি সমাজতন্ত্রীদের সংস্কারের দাবি ঠিক হতো তাহলে সম্প্রদায় ভিত্তিতে সমান সংগঠনের সাথে সাথে দুর্নীতির ছোবল অসম্ভব হয়ে পড়তো । অন্যদিকে আমরা প্রায়ই দেখতে পাই সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোয় নেতৃস্থানীয় সদস্যদের অপসারণ করা হয় । সুতরাং ব্যক্তিমালিকানা সুবিধা প্রাপ্তির একমাত্র নিয়ামক হতে পারে না।
প্রথমত ‘সুবিধা’ কেবল অর্থকড়ি এবং চুক্তিনামা নিয়ে গঠিত নয় । আরও অনেক কিছু রয়েছে যা মানবসমাজে মূল্যবান । যেমন : অন্যদের চেয়ে সৌন্দর্য বেশি থাকা নারীর জন্য একটি সুবিধা, যার সাথে ইবাদাতের কোনো সম্পর্ক নেই । এমনকি সমাজতান্ত্রিক সমাজেও এর একটি নিজস্ব অবস্থান রয়েছে।
এর চেয়েও বেশি এবং বড় সুবিধা রয়েছে পদমর্যাদা এবং অবস্থানের । বিশ্বের অন্যতম ধনী ব্যক্তিত্ব রকফেলার সব সময় চাইতেন তিনি যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হবেন । কখনও কখনও কারো ক্ষেত্রে এ ইচ্ছা এত প্রবল যে, এটা পূরণ করার জন্য অনেক ধনী ব্যক্তি প্রায় পুরো সম্পদই উৎসর্গ করতে রাজী হয়ে পড়ে যাতে ক্ষমতাবান মানব হিসাবে সে সম্মান ও যশ অর্জন করতে পারে । মানুষের কাছে এটা সবসময়ই মূল্যবান যে, তাকে অন্যরা সম্মান করবে, হোক তা ভয়, সহানুভূতি বা ভক্তির কারণে।
এমন লোক পাওয়া যাবে না যে আয়াতুল্লাহ বুরুজারদীর মতো হতে চায় না যাতে মানুষ তাকে দেখার জন্য আগ্রহী হবে, তার হাতে চুমু খাবে, তার জন্য উপহার আনবে, তারা তাকে অভ্যর্থনা জানাবে আর সে সম্মানিত অনুভব করবে । তারা কি কেউ রাজা হবার বাসনা পোষণ করে না যাতে শত শত কর্মকর্তা এবং সাধারণ মানুষ তার সামনে ভক্তিভরে দাঁড়িয়ে থাকবে- ভয় করে হলেও? মানবসমাজ এগুলোকেও যথেষ্ট মূল্যবান মনে করে নতুবা এসব সুবিধা অর্জনের জন্য তারা সব কিছু হারাতে প্রস্তুত হবে না ।
কাজেই মানবিক অবনতি এবং সামাজিক দুষ্টক্ষত শুধু সম্পদের কারণে নয় । এক্ষেত্রে আরও নিয়ামক রয়েছে যা সমাজতন্ত্র অতিক্রম করতে পারেনি ।
দ্বিতীয়ত যখন অন্যান্য সুবিধা আগেকার কোনো সুবিধার কারণে অর্জিত হয়, এমনকি সমাজতান্ত্রিক সমাজেও, তখন ঐ সব সুবিধা থাকার কারণে তাদের বেশ ভালোই লাভ হয় । উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, একজন সোভিয়েত নেতার সম্পদের ওপর আয়কৃত সুদের পরিমাণ একজন কৃষকের সম্পদের ওপর নিরূপিত সুদের সমান হবে কি ? (যদিও ঐ নেতা কৃষিকাজে নিয়োজিত) একজন কৃষক জীবনেও একবার তার মতো ভ্রমণ করার সুযোগ পাবে না অথচ কোথাও যাওয়ার জন্য তার নেতার রয়েছে একটি শ্রেষ্ঠ বিমান । সুতরাং এটা দাবি করা যায় না যে, সবার জন্য সম্পদের সমান সুবিধা সমাজতন্ত্রে বাস্তবায়ন করা হয়েছে বা যে কেউ রাষ্ট্রীয় সম্পদ থেকে সমানভাবে উপকৃত হবে ।
ব্যক্তি মালিকানাধীন নয় অথচ সরকারি কোষাগার থেকে সকল সরকারি কর্মকর্তা কি সমানভাবে উপকৃত হয়? উঁচু স্তরের কর্মকর্তা সাধারণ কর্মচারী অপেক্ষা বেশি সুযোগ সুবিধা ভোগ করে থাকে ।
গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় হলো সমাজতান্ত্রিক দেশেও আত্মত্যাগ ও বস্তুগত সুবিধাদি বর্জনের প্রয়োজন দেখা যায় । যেমন একজন সৈন্য যুদ্ধে গিয়ে নিহত হলো; কোনো পারস্পরিক স্বার্থের কারণে তাকে হত্যা করা হয়নি । তাকে কোনো আদর্শ বা আবেগ-অনুভূতির আশ্রয়ে উদ্দীপ্ত করা হয়েছে যাতে সে তাদের স্বার্থে আত্মোৎসর্গ করে । কাজেই সবচেয়ে বস্তুবাদী মতবাদও কিছুটা আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ ছাড়া চলতে পারে না যদিও সে তার দৃঢ় বিশ্বাসকে উপাসনাযোগ্য কোনো কিছুর দিকে ঘুরিয়ে দেয়। সমাজভিত্তিক মতবাদ যা নিতান্তই বস্তু স্বার্থের ওপর নির্ভরশীল, বাস্তবসম্মত বা ব্যাপক নয়। নীতি, আদর্শ, লক্ষ্য এবং তাদের ব্যবস্থার প্রতীক প্রসঙ্গে সমাজতান্ত্রিক নেতৃবৃন্দ কেমন করে সক্রিয় থাকেন?
তারা এমন আচরণ করে যেন তাদের ব্যবস্থাটি সবকিছুর ঊর্ধ্বে অথচ এটা কেবল এ জীবনের কিছু সুখ অর্জনে নিয়োজিত । বস্তুবাদের ভিত্তিতে তাদের নীতিমালা একজন স্থাপত্য প্রকৌশলীর একটি ভবনের নক্শা তৈরির মতো । এ নক্শায় পবিত্রতার কোনো স্থান নেই। এটা বিনির্মাণ কাজের ক্ষেত্রে সহযোগিতা মাত্র । শ্রেষ্ঠ নকশাটি ঐ ভবনের পরিপূরক । এ মতবাদ সম্পর্কে বেশি যা বলা যায় তা হলো এটা সমাজের জন্য শ্রেষ্ঠ পরিকল্পনা । তবে এ পরিকল্পনাটিকে উপাসনাযোগ্য বলে বিবেচনা করা হবে কেনো? নকশাটি ভবনের জন্য আর ভবনটি আমার জন্য । কাজেই ঐ নকশার জন্য আমি কেনো আত্মোৎসর্গ করবো?
এরকম দাবির কোনো গ্রহণযোগ্যতা নেই । এখনও এ ব্যবস্থাকে শুধু সমাজ গঠনের উপায়রূপে দেখা হয় অথচ প্রায়ই এতে পবিত্র কিছুর আভাস পাওয়া যায়, যার সম্মানে কেউ জীবনও উৎসর্গ করে থাকে । এর অনুসারীরা তাদের দাবিকে ভিত্তিহীন মনে করতে পারে তথাপি তাদের নিজেদেরকে ও অন্যদেরকে বারবার অনুশীলন করে প্রস্তুত করতে হয় যেন আত্মোৎসর্গে যথেষ্ট উদ্দীপ্ত হয় । এবার আসুন আমরা দেখি কীসের সমন্বয়ে আধ্যাত্মিক লক্ষ্য ও মূল্যবোধ গঠিত হয় । এগুলো কি আসলেই বিরাজ করে নাকি নির্বোধ ব্যক্তিকে প্রতারণার কোনো উপদেশ মাত্র? কেনো এগুলোকে বস্তুগত মূল্যবোধ অপেক্ষা শ্রেয়তর বিবেচনা করা হয়?
যা হোক মূল্যবোধ কী? যখন কেউ স্বেচ্ছায় কোনো কাজ করে তার একটা উদ্দেশ্য থাকে, যা তার কাছে গুরুত্বপূর্ণ- হোক তা বস্তুগত বা আধ্যাত্মিক । অর্থাৎ ঐ উদ্দেশ্যে তার একটা স্বার্থ আছে নচেৎ সে তা অনুসরণ করবে না । বলা হয়ে থাকে পরম উদ্দেশ্যহীনতা বা ব্যর্থতা অসম্ভব ।
বস্তুগত দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী এটা স্পষ্ট যে, যা কিছু আমার কাছে প্রয়োজনীয় তার প্রতি আমি আকৃষ্ট হবো আমার জীবনের গতিময়তার কারণে; যেহেতু আমি প্রকৃতভাবে আমার জীবনের সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত । মূল্য শব্দটি বস্তুজগতের জন্য যেমন আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রেও তেমন ব্যবহৃত হতে পারে । একজন চিকিৎসকের কাছে আমার মূল্য আছে ঠিক যেমন ঔষধেরও মূল্য আছে ।
বস্তুজগতের জন্য শারীরিক অবয়ব দরকার; শরীরের জন্য শরীর চর্চা দরকার, যদিও তা কোনো বস্তু নয় । তাহলে! খাদ্য ও ব্যায়ামে আমাদের জন্য মূল্য আছে । অন্যদের প্রতি দানশীল হওয়া- যে দান করলো তার কোনো বস্তুগত লাভ নেই; একইভাবে সমাজসেবা বা পরবর্তী প্রজন্মের জন্য কিছু করে যাওয়া ভালো কাজরূপে গণ্য । কিন্তু যে এ কাজ করে গেল তার কাছে এর মূল্য কী? পরবর্তী প্রজন্মের জন্য কেউ অনেক পরিশ্রম করে একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দাঁড় করালো এবং এখান থেকে কোনো মুনাফা পেল না । অথবা তার সময় শেষ হয়ে গেলো, আরও বেশি উপার্জনের সুযোগও থাকলো না । এ ব্যাপারটিকে আমরা আধ্যাত্মিকতার আশ্রয়ে কীভাবে ব্যাখ্যা করতে পারি? আধ্যাত্মিক বিষয়াবলী মানব জীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রশ্ন করা যেতে পারে, আধ্যাত্মিকতা স্রষ্টা বিশ্বাসে সীমাবদ্ধ কি না। অথবা এটা সম্ভব কি না যে, এরকম কোনো বিশ্বাস থাকবে না অথচ মানব জীবন পরিচালনায় অসংখ্য আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ থাকবে?
সারটার তাঁর ‘জেনুইননেস্ অব ম্যান’ বইয়ে দস্তোভস্কির এ বাক্যের উদ্ধৃতি দিয়েছেন ‘যদি কোনো স্রষ্টা না থাকে, তাহলে সবকিছুরই অনুমতি থাকে’। অর্থাৎ ভালো এবং মন্দ, সত্য ও মিথ্যা, প্রতারণা ও সেবা সবকিছুই নির্ভর করে আমরা স্রষ্টায় বিশ্বাসী কি না তার ওপর । যদি আমাদের বিশ্বাস না থাকে, তাহলে কোনো বাধা থাকবে না এবং সব কিছুরই তখন অনুমতি থাকবে । এটা কি সত্য, নাকি মিথ্যা?
বস্তুবাদী হিসাবে মার্কসবাদীদের মধ্যে একটা অদ্ভুত ব্যাপার লক্ষ্য করা যায় । তারা দাবি করে তাদের আধ্যাত্মিকতা বা মানবতার কোনো দরকার নেই এবং যদি তারা পরিমিত মানবতার কথা বলে তা হলো শ্রেণীহীন মানবসমাজ । তাদের মতে মানুষ হয় অপূর্ণাঙ্গ । আর তাদের অপূর্ণাঙ্গ দশা সম্পদের ব্যক্তিমালিকানা এবং আর্থ-সামাজিক বৈষম্য থেকে উৎসারিত । একবার এ বৈষম্যগুলো দূর করা গেলে মানবসমাজ আবার তাদের আগের পূর্ণতায় ফিরে যাবে । তারা মানবের আর কোনো পূর্ণতায় বিশ্বাসী নয়-অন্য কোনো উন্নয়ন বা বিবর্তনেও নয় ।
তাহলে সারটার-এর মতবাদের ব্যাপারটা কী? সেখানে বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গির পাশাপাশি আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ, যেমন মানবতাও আছে । আবার সেখানে মানবের দায়-দায়িত্ব নিয়েও কথা বলা হয় । একদিকে বলা হয়, মানুষ সব ধরনের ঐশী সার্বভৌমত্ব থেকে মুক্ত বা প্রাকৃতিক শাসন থেকে স্বাধীন । তার ইচ্ছা কোনোভাবেই অতীতের ওপর নির্ভরশীল নয় । সে মানুষ, যে তাকে গড়ে তোলে- পরিবেশ নয়, লক্ষ্য নয়, নয় স্রষ্টা । কাজেই সে নিজের জন্য নিজেই দায়ী । সুতরাং সে যে কাজ পছন্দ করে ও সম্পাদন করে তা অবশ্যই ভালো হতে হবে । এভাবে সে নিজেকে অন্যদের জন্য আদর্শে রূপান্তরিত করে যেন অন্যরা তাকে অনুকরণ করে । আর এ ক্ষেত্রে সে অন্যদের আচরণের জন্যও দায়ী থাকে । এবার চলুন আমরা দেখি এ দায়-দায়িত্বটা কী এবং এর অর্থ-ই বা কী । এটা আধ্যাত্মিক বিষয়, বস্তুগত বিষয় নয় । বস্তুবাদ অনুযায়ী তারা বলতে পারে মানবের বিবেচনা রয়েছে যা দায়-দায়িত্ব বিষয়ক প্রশ্নের উত্তর দেয় । যদি তারা বিশ্বাস করে মানুষের মধ্যে দু’টি সত্তা রয়েছে- একটা জন্তুর, অন্যটা মানবের । যখন সে কোনো অপরাধ করে তখন জন্তু সত্তাকে মানব সত্তা ভর্ৎসনা করে । তাহলে দায়-দায়িত্বের শেকড় কোথায়?
যদি তারা কোনোভাবে দায়-দায়িত্বের কথা বলে, তাহলে তা তো আধ্যাত্মিক বিষয় । তারা বলে, ‘আমি মানব জাতি ও পরবর্তী প্রজন্মের জন্য দায়ী।’ এটা কী অর্থ বহন করে? তারা একটি বস্তুবাদী গোষ্ঠীর সদস্য, তথাপি তারা মানবতা প্রতিষ্ঠা করতে চায় । মানুষকে তার অধীন করতে চায়! চায় তারা এ ধারণা লালন করুক । তবে স্রষ্টাকে বাদ দিয়ে! সারটার এমনও বলেছেন, ‘যদি সব ক্ষেত্রে স্রষ্টা এসে যান, তথাপি তখন কোনো আধ্যাত্মিকতা অবশিষ্ট থাকে না । কারণ, এর ভিত্তি হলো পুরোপুরি মানব স্বাধীনতা, আর স্রষ্টার উপস্থিতি অর্থ স্বাধীনতার অভাব । এভাবে পছন্দের স্বাধীনতাবিহীন দায়দায়িত্ব অর্থহীন হয়ে পড়ে । কেউ হয়ত বলবেন, ‘স্রষ্টায় বিশ্বাস ছাড়া আধ্যাত্মিকতায় বিশ্বাস স্থাপনে বাধা কোথায়?’ কারণ, মানব প্রকৃতিতে বিবেক-বিবেচনা স্বতঃস্ফূর্তরূপে মিশে আছে যা তাকে ভালো কাজ উপভোগে সক্ষম করে তোলে এবং খারাপ কাজকেঘৃণা করতে উদ্বুদ্ধ করে । সে কোনো বস্তুগত স্বার্থে কেনো ভালো কাজ করে না, বরং সে ওটা করতে আনন্দ পায় যেমন সে আনন্দ পায় ইতিহাস, ভূগোল সম্পর্কে জ্ঞান আহরণে । এ ক্ষেত্রে একমাত্র লাভ হচ্ছে অধিকতর সচেতনতা । অনুরূপভাবে, নীতি-নৈতিকতার বিষয়াবলী তাকে আনন্দ দেয় । গ্রীক দার্শনিক এপিকিউরাস এ ধারণার প্রতি সমর্থন দেন । ওমর খৈয়ামও এটা বিশ্বাস করেন বলে শোনা যায় । পরে এপিকিউরিজম নির্বিচারে প্রয়োগ করা হয় প্রতিটি আনন্দদায়ক বিষয়ের প্রতি। তবে এমন দাবিও উত্থাপিত হয় যে, তাঁর প্রকৃত মতবাদে আধ্যাত্মিক আনন্দের কথা এপিউকউরাস বিশ্বাস করতেন যা অধিকতর স্থায়ী এবং সহজতর উপায়ে অর্জন করা যায় । সৌন্দর্য, ফুল, পাখি, গান ইত্যাদির প্রতি প্রেম আরো আনন্দের উদাহরণ যাতে কোনো বস্তুগত স্বার্থ নেই তবে মানবাত্মা আনন্দ পায়।
এসব মন্তব্য কোনো কোনো পরিসরে সত্য, তবে দু’টি সীমাবদ্ধতা রয়েছে । প্রথমত মানুষের বিবেক একটি মতবাদ দাঁড় করানোর ভিত্তি প্রদানে প্রয়োজনীয়তা গভীরতায় চিহ্নিত নাও হতে পারে। যদি একজন মানুষ কেবল আনন্দ পাওয়ার জন্য কিছু করে থাকে তবে তা সে করে মৃত্যুর সীমানার আগে বা পরবর্তী বন্দীদশার আগে এবং ভিন্নপথে গমনের ক্ষেত্রে; একটি মতবাদ যেরূপ চিহ্নিত করেততটা গভীর প্রয়োজনে নয় । কেউ একটি ফুলের জন্য প্রাণ দিতে রাজী হবে না । সে বেঁচে থেকে ঐ ফুল থেকে ঘ্রাণ নিয়ে আনন্দ পেতে চায় । অন্যদের সাহায্য করার আনন্দ আছে তবে এ আনন্দেরজন্য কেউ মরতে চায় না ।
তাই এটা ঠিক যে, মানুষ বিবেকের গভীরে ভালো কাজের আনন্দ উপভোগ করে । পবিত্র কুরআনেও এর সমর্থন পাওয়া যায় । তবে একটি মতবাদের ভিত্তি পাওয়া যাবে বিবেক-বুদ্ধি থেকে এটা সম্ভব নয় । এক্ষেত্রে আরও বেশি গভীরতায় বিশ্বাস প্রয়োজন । তাই যদি কেউ বলে যে, ইমাম হুসাইন (আ.) কারবালায় নিজের জীবন এবং তাঁর অনুসারীবৃন্দের জীবন উৎসর্গ করলেন কেবল মানুষেরসেবা সংক্রান্ত তাঁর দাবি পূরণের জন্য তাহলে সঠিক বিচার হবে না । কারণ, এটা সুস্পষ্ট যে, তিনি তাঁর বিবেক-বুদ্ধি দিয়ে নয়; বরং তাঁর গভীরতর বিশ্বাস থেকে এভাবে উজ্জীবিত হয়েছিলেন ।
যদি স্রষ্টা না থাকে এবং কোনো সুশৃঙ্খল উদ্দেশ্য না থাকে এবং মানুষ ও বস্তুর মধ্যে স্বাভাবিক কোনো সম্পর্ক না থাকে তাহলে কি আমরা বলবো না প্রকৃতিতে কোনো ত্রুটি রয়ে গেছে? শোপেনার বলেন, ‘প্রকৃতি মানুষকে বিভ্রান্ত করা ও তার নিজস্ব উদ্দেশ্য পূরণের পর তাকে পাঠিয়ে দেবার জন্য আনন্দ উপহার দেয়।’ উদাহরণস্বরূপ, প্রকৃতি চায় প্রাণীজগৎ টিকে থাকুক। যদি সে কোনো ব্যক্তিকে বিয়ের নির্দেশ দেয়; কাজ করে স্ত্রী-পুত্র পরিজনের খরচ বহনের নির্দেশ দেয় তাহলে কোনো বুদ্ধিমান লোক তা করবে না; কিন্তু প্রকৃতি তাকে এমন মায়াডোরে আবদ্ধ করে যে, সে নিজেই বিয়ে করতে চায় । যে কোনো ক্ষেত্রেই প্রতিটি আনন্দ কোনো প্রয়োজনের ওপর নির্ভরশীল । আমরা খাই; কারণ, আমাদের প্রকৃতির ঐ দ্রব্য দরকার; একই কারণে আমরা পান করি, ঘুমাই । যদি আমাদের কোনো প্রয়োজন না থাকতো তাহলে আমরা ওগুলোর শরণাপন্ন হতাম না । বস্তুগত আনন্দের কারণ পরিস্কার, তবে আধ্যাত্মিক আনন্দের ব্যাপারটা কীরূপ? আমি যদি দেখি, একজন ইয়াতিম খাবার খাচ্ছে, কেনো আমি আনন্দ পাবো? এর সাথে আমার কোনো সম্পর্ক নেই । তাই এ আনন্দ নিষ্ফল; কারণ, এতে মৌলিক কোনো জ্ঞান নেই । কিন্তু আমরা যদি বিশ্ব পর্যায়ে আন্তঃসম্পর্কে বিশ্বাস করি এবং বুদ্ধিমত্তানির্ভর কোনো সৃষ্টিতে বিশ্বাস করি, তাহলে সকল মানুষকে একটি সম্প্রদায়ের সদস্য বলে গণ্য করবো যারা অন্যের কল্যাণ প্রত্যক্ষ করে আনন্দপাবে । এরকম হওয়ার কারণ হলো সৃষ্টির একটি সত্য নিয়ম-নীতি আমরা মেনে চলি। কিন্তু এ আনন্দ যদি দৈবক্রমে হয় এবং কেবলই প্রাকৃতিক কারণে হয়, তাহলেও তা ব্যর্থ হবে । কারণ, তখন এতে প্রাকৃতিক উদ্দেশ্য অনুপস্থিত থাকে । কাজেই যখন আমরা নৈতিক বিবেচনায় বিশ্বাস করি এবং দাবি করি যে, মানুষ প্রকৃতিগতভাবে ভালো কাজ করে উপকৃত হয় এবং মন্দ কাজ করে হেরে যায়, তখনও আমাদের কর্ম নিষ্ফল হবে স্রষ্টার ওপর এবং সৃষ্টির লক্ষ্যের ওপর বিশ্বাস স্থাপন ছাড়া ।
যখন আমরা বিশ্বাস করি, স্রষ্টা মানুষকে নীতি-নৈতিকতা-বিবেচনা দিয়েছেন একটি লক্ষ্য অর্জনের জন্য, তখন একজন ইয়াতিম শিশু, একজন বৃদ্ধা নারী এবং আমি নিজে সবাই এক মহাপরিকল্পনারঅংশ-বিশেষ এক সংগঠনের সহ-সদস্য বলে বিবেচিত হবো । এভাবে আমরা ঐশী এক ইচ্ছা ও জ্ঞানের অনুসরণ করছি এবং ঐ লক্ষ্য অর্জনের চেষ্টা করছি । তখন কোনো কিছুই নিষ্ফল নয় এবং সবকিছুই সত্য ও আসল । সুতরাং প্রতিটি মতবাদ এবং প্রতিটি সমাজ ব্যবস্থার প্রয়োজন বেশ কিছু আধ্যাত্মিক ধারণা, একটি আদর্শ যা বস্তুগত মূল্যবোধের অনেক ঊর্ধ্বে এবং এত শক্তিশালী যে, তা পবিত্র হয়ে পড়ে । এ পবিত্রতা একজন মানুষের কাছে যথেষ্ট মূল্যবান বলে গণ্য হবে যাতে সে তার ব্যক্তিগত জীবন উৎসর্গ করতে পারে।
সা’দীর কবিতায়ও ওপরের মতবাদের ইঙ্গিত পাওয়া যায় :
‘বাতাস, মেঘ, সূর্য, আকাশ
সবাই কাজে ব্যস্ত,
যেন তুমি জীবিকা অর্জন করতে পারো।
তাই এসব নষ্ট করো না অবহেলায়।’
এতে প্রতিটি সৃষ্ট বস্তুর দায়-দায়িত্বের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করা হয়েছে । যেমন : পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করা হয়েছে :
‘তুমি কি দেখ না আসমান যমিনের সবকিছুকে স্রষ্টা তোমাদের জন্য পালন করছেন।’ (সূরা লুকমান : ২০)
অর্থাৎ সৃষ্টি জগতের প্রতিটি সৃষ্টির একটি উদ্দেশ্য আছে এবং সকলেই নিজ নিজ কাজ সুচারুরূপে সম্পাদন করছে । তাই মানুষের দায়িত্ব-কর্তব্য রয়েছে দায়-দায়িত্বের এক মহাসমুদ্র মাঝে । কিন্তু যে ব্যবস্থায় বস্তুজগতকে চূড়ান্ত কোনো লক্ষ্যহীন বলে বিবেচনা করা হয় তাতে বিশ্বাস স্থাপিত হয় যে, প্রাণীর কোনো দায়িত্ব-কর্তব্য নেই; এটা শুধু মানুষের বেলায় সীমাবদ্ধ । কেনো এমন হবে তা কিন্তু ব্যাখ্যা করা হয়নি। প্রতিটি মতবাদের জন্য আদর্শ হচ্ছে একটি মৌলিক বিষয় । ফলে ব্যক্তি বা সমাজের সামনে কিছু উপস্থাপন করা যায়, যার জন্য তারা পরিশ্রম করবে । আর স্রষ্টায় বিশ্বাস ও সৃষ্টিতে তাঁর প্রজ্ঞার ওপর বিশ্বাস ছাড়া এসব আদর্শ অর্থহীন হয়ে পড়ে।
বিশ্বাস, বিভিন্ন মতবাদ এবং বৈশ্বিক দৃষ্টিভঙ্গি
বুদ্ধিবৃত্তিক এবং দার্শনিক ব্যাখ্যাসহ বিশ্বাস হচ্ছে গুরুত্বসহ গৃহীত আদর্শের জন্য প্রয়োজনীয় শর্ত । এতে বিশেষ যুক্তি ও অন্তর্দৃষ্টির ওপর নির্ভরশীল বিশ্বজনীন প্রেক্ষাপটকে ধরে নেয়া হয় যার প্রতি বিশ্বাস ও বিশ্বজগৎ সংক্রান্ত সুচারু যৌক্তিকতার সমর্থন মেলে । বিশ্বাস একে এমন লক্ষ্যের প্রতি ধাবিত হওয়ার শক্তি যোগায় যা ব্যক্তিগত পর্যায়ের বা বিশেষ লক্ষ্যের চেয়েও উচ্চতর । আর সত্যটি কোনো কোনো আধুনিক মতবাদেও প্রকাশ পেয়েছে, যেমন অস্তিত্ববাদ । তারা একটি আদর্শ গড়ে তুলতে চায় বিশ্বাসকে বাদ দিয়ে । তারা বিশ্বাসকে ছেড়ে কেবলই দর্শনের ওপর ভিত্তি করে একটা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে চায় যেখানে উচ্চতর লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের জন্য এক প্রকার প্রেমের দেখা মেলে । তবে তা সম্ভব নয়।
কখনও তারা একটি দূরবর্তী ছায়া স্থাপন করে, আর তা মানুষের খেয়ালনির্ভর; এর বেশি কিছু নয় । তথাপি বিশ্বাসের ওপর প্রতিষ্ঠিত একটি আদর্শ বিশ্বাসের কারণে পবিত্র । যদি এর ভিত্তি ‘বিশ্বাস’ না হয়ে শুধু অন্য কোনো বুদ্ধিবৃত্তিক ব্যবস্থা হয়, তাহলে তা প্রেম ও আবেগ জাগাতে পারে না । কারণ, তা বল প্রয়োগ বা উপদেশ দিয়ে সবার ওপর চাপিয়ে দেয়া গেলেও এর যৌক্তিক ভিত্তি নেই ।
একটিমতবাদ একটি একক ব্যবহারিক ব্যবস্থা- তাত্ত্বিক বা তত্ত্বীয় বিজ্ঞানের সাথে সম্পর্কযুক্ত কোনো কিছু নয় । এ ব্যবস্থায় যা বিরাজমান তার ব্যাপারে ধারণা দেয়া হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, অ্যারিস্টটল বা নিউটনের পদার্থ বিজ্ঞান প্রতিটি তত্ত্বগতভাবে ধারণ করা একটি ব্যবস্থা ।
একটি ব্যবহারিক ব্যবস্থা হচ্ছে তা-ই । প্রাচীন কালেও দেখা যায়, জ্ঞান দু’ভাগে বিভক্ত ছিল : তাত্ত্বিক এবং ব্যবহারিক । অভিজ্ঞতালব্ধ ব্যবস্থায় একটি অনুসন্ধানের লক্ষ্য থাকে শ্রেষ্ঠ পথটি বের করা । যেমন মানুষ কীভাবে বসবাস করবে এবং একটি সমাজের কেমন হওয়া উচিত । এর একটি স্তম্ভ হলো সংগঠন যার কতক বিভাগ আছে এবং এদের প্রতিটির নিজস্ব অবস্থান রয়েছে, নিজস্ব কাজ ও গুরুত্বও রয়েছে । বিক্ষিপ্ত এক গাদা ধারণার সমষ্টি একটি সুসংহত ব্যবস্থার প্রবর্তন করতে পারে না । একটি মতবাদ হলো সামঞ্জস্যপূর্ণ ধারণাসমূহের সমষ্টি যা বাস্তব জীবনের সাথে সম্পর্কযুক্ত। যেমন কেমন হওয়া উচিত, কেমন হওয়া উচিত নয়। তাত্ত্বিক ধারণা-ই এর ভিত্তি এবং চালিকা শক্তি। তাই আমরা বলি, প্রতিটি মতবাদ সর্বজনীন প্রেক্ষাপটের ওপর ভিত্তিশীল। যার অর্থ দাঁড়ায় পৃথিবী যেমন আছে তেমন দেখা- মানুষের কেমন হওয়া উচিত এভাবে দেখা থেকে তা সুস্পষ্টভাবে আলাদা । একটি মতবাদের চালিকা শক্তিকে একদিকে অবশ্যই দীর্ঘ মেয়াদী দৃষ্টিভঙ্গির হতে হবে এবং অস্তিত্বমান-এর মূল্যায়ন করতে হবে। অন্যদিকে তাকে আদর্শ সৃষ্টি করতে হবে-কেবল দার্শনিক ভিত্তি নয় বরং ধর্মীয় ভিত্তির ওপরও তার প্রতিষ্ঠিত থাকা উচিত। এতে কিছু উপস্থাপন করা হবে যা সবাই ভালোবাসবে- একটি নীতি এবং একটি সামাজিক আদর্শ। জ্যোতির্বিদ্যা মহাকাশে বিরাজমান গ্রহ-নক্ষত্র সম্পর্কে জ্ঞান বিতরণ করে থাকে তবে সেগুলোর কেমন হওয়া উচিত বা কেমন হওয়া উচিত নয় এ সম্পর্কে কিছুই বলে না। কারণ, এসব ব্যাপার মানব জীবনের সাথে সম্পর্কিত নয়।
একটি মতবাদ এমন কিছু উপস্থাপন করে যাতে মানবের জন্য একটি আদর্শ তুলে ধরা হয়। সর্বজনীন প্রেক্ষাপটে দর্শনের ভিত্তি উপস্থাপনে একেশ্বরবাদিতা সফল। একইভাবে একটি অন্তর্দৃষ্টি লাভেও তা সক্ষম। একই সাথে তা স্রষ্টার একত্বকে ঘোষণা করে, যেমন কুরআনে বলা হয়েছে : ‘আল্লাহ ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই।’
প্রাচীনকালে একেশ্বরবাদিতা কয়েকটি ভাগে বিভক্ত ছিল : আভাস, গুণাবলী, কাজ ও উপাসনার একেশ্বরবাদ। আভাসের একত্ববাদে বলা হয় স্রষ্টার সমকক্ষ বা অংশীদার নেই । গুণাবলীর একত্ববাদে তুলে ধরা হয় তাঁর আভাস তাঁর গুণাবলীর প্রতিপক্ষ নয়, আবার এরা পারস্পরিক প্রতিপক্ষ নয়। তাঁর প্রজ্ঞা ও জ্ঞানে সকল পূর্ণতা বিরাজমান। কর্মের একেশ্বরবাদিতা মানে সকল কর্মের ঐক্য; উপাসনার একেশ্বরবাদ দাবি করে তিনিই একমাত্র উপাসনার যোগ্য এবং অবশ্যই তাঁর উপাসনা করতে হবে, আর এ বিষয়টি মানব আত্মায় মিশে আছে। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে : ‘তোমরা কি আল্লাহর দীন অপেক্ষা অন্য কোনো ধর্ম সন্ধান করছো অথচ আসমান যমীনের সবকিছু তাঁকে মেনে চলে?’ (সূরা আলে ইমরান : ৮৩)
আমাদের উপাসনা এক রকম- আত্মসমর্পণ ও আনুগত্য। যেমন বলা হয়েছে সৃষ্টির সব কিছুই তাঁর প্রশংসা করে। (সূরা জুমুআ : ১, সূরা সফ্ফ : ১, সূরা রাদ : ১৫) উপাসনার একেশ্বরবাদে স্রষ্টার আভাস মানবের জন্য আদর্শ । যেহেতু স্রষ্টা একক-অনন্য, তাঁর জন্য কোনো দ্বিতীয় শরীক নেই, আর তিনিই বিশ্বজগতের উৎস এবং উপাসনার যোগ্য একমাত্র সত্তা, এভাবে একেশ্বরবাদে দু’টি বৈশিষ্ট্য রয়েছে : প্রথমত এটা একপ্রকার দৃষ্টিভঙ্গি ও অস্তিত্বের মূল্যায়ন, আর দ্বিতীয়ত মানবের জন্য আদর্শ। মাকর্সবাদ পুরোপুরি ভিন্ন । একটি বস্তবাদী দৃষ্টিভঙ্গি যাতে জীবন যাপন নিয়ে বিচার- বিবেচনা রয়েছে তবে কখনই তা অর্থনীতিকে পাশে সরিয়ে আদর্শ উপস্থাপন করে না । উদ্দেশ্য হিসাবে তা বঞ্চিত মানুষের স্বার্থের কথা তুলে ধরে; তাদেরকে তাদের অধিকার ছিনিয়ে নেবার চেষ্টা করতে বলে । কিন্তু এটা একটি ত্রুটিপূর্ণ লক্ষ্য এবং অর্জন না করা পর্যন্ত তা আদর্শ রূপেও গণ্য হতে পারে । তবে লক্ষ্য অর্জিত হবার পর ? আদর্শ বা লক্ষ্য-উদ্দেশ্য হওয়াটা তখন শেষ হয়ে যায় । বস্তুবাদী কোনো লক্ষ্যকে পবিত্র লক্ষ্যরূপে ব্যাখ্যা করা যায় না । এ উদ্দেশ্য মানবিক লক্ষ্যের ঊর্ধ্বে নয় এবং এখানে অত্মোৎসর্গ অযৌক্তিক, যেহেতু তা বস্তুবাদী ধ্যান-ধারণার সমষ্টি । আত্মোৎসর্গের মাধ্যমে বস্তুবাদী লক্ষ্য অর্জন করা স্ববিরোধী একটি ব্যাপার । সুতরাং একে কি আদর্শ বলা যায়?
মার্কস্বাদ আসলে আদর্শের অনুপস্থিতি এবং ব্যক্তি-স্বার্থের আবেগের দিকে প্রত্যাবর্তন । এর শক্তি শেকল ভাঙ্গায় নিহিত। জীবনের সকল ক্ষেত্র তা পরিব্যাপ্ত করতে পারে না । যেমন : রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং নীতি-নৈতিকতা ইত্যাদি ক্ষেত্রে এর কোনো ভূমিকা নেই । কেবল প্রচ্ছন্ন বা পরোক্ষ সংযোগ পাওয়া যায় । ফলে ন্যায়বিচার ও নীতি-নৈতিকতা প্রকৃত অর্থ হারিয়ে ফেলে ।
কোনো মতবাদে কার্যকারণ সম্পর্কে নির্ধারিত উদ্দীপনার দেখা মিলতে পারে, তবে একটি মতবাদের অবশ্যই যুৎসই আদর্শ থাকা দরকার যা বিশ্বজনীন একটি রূপ লাভ করবে । এর বিপরীত বক্তব্য সঠিক নয়, যেহেতু উপযুক্ত আদর্শ ছাড়া বিশ্বজনীন দৃষ্টিভঙ্গির কোনো মতবাদে সামগ্রিক উদ্দীপনার দেখা পাওয়া অসম্ভব । গঠনমূলকভাবে দেখা যায়, মানুষ ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে থাকে, অতীত বা বর্তমানের দিকে নয় । সুতরাং দর্শন একা যথেষ্ট নয় । বিশ্বজনীন দৃষ্টিভঙ্গিও পরস্পর বিরোধী হতে পারে। একটি হয়ত বাধ্যবাধ্যতা আরোপ করে অথচ অন্য কোনোটি তা করে না । অন্য কথায় কোনোটি হয়ত মানুষকে দায়-দায়িত্ব দিচ্ছে; কিন্তু অন্যটি দিচ্ছে না । একেশ্বরবাদী বিশ্বজনীন দৃষ্টিভঙ্গি একটি ঐশী বাধ্যতা আরোপ করে; অন্যদিকে যেমন অস্তিত্ববাদে আধ্যাত্মিক ভিত্তি নেই । এক ব্যক্তি বলতে পারে, ‘আমি আমার জন্য দায়িত্ববান যেহেতু আমি স্বাধীন।’ কিন্তু এরকম স্বাধীনতার কোনো অর্থ নেই যেহেতু তা অন্য সবকিছুর সঙ্গে সম্পর্কহীন এবং তাই অনেক সমস্যা সৃষ্টি করে । ধরুন আমি মুক্ত এবং ঐশী বা পরিবেশগত বাধ্যবাধ্যতা আমাকে চালনা করে না । তাহলে তারা যেমন বলে, ‘আমি আমার জন্য দায়িত্ববান, অন্য কেউ নয়’ এটা কি অন্যদেরও দায়- দায়িত্বের সাথে সংযুক্ত করে? আমি কি আমার জন্য এমন কিছু চাইবো যা অন্যদের জন্যও লাভজনক হবে ? তারা যদি এ দায়িত্ব আমার ওপর অর্পণ করে, তা কোত্থেকে এলো ? অন্যরাও মুক্ত এবং ঐ পরম স্বাধীনতার সাথে অন্যের সামনে দায়-দায়িত্বের কোনো যোগসূত্র নেই।
এ রকম যে স্বাধীনতার কথা তারা বলে থাকে তা আদর্শ হবে এটাও অর্থহীন । এ দিয়ে বোঝায় আমার পছন্দের সাধারণ স্বাধীনতা আছে এবং দাবি করা হয় ঐ পছন্দ শুধু আমার জন্যই ভালো নয়, বরং তা অন্যের জন্যও ভালো । কিন্তু অন্যরাও স্বাধীন এবং কারও নিজস্ব ইচ্ছার ব্যাপারে কোনো প্রতিনিধিকে প্রাধান্য দেয়া যায় না । অধিকন্ত আমরা আরও একমত হতে পারি যে, আমার পছন্দ এতটা সঠিক হবে যে, তা অন্যদের যা দায়-দায়িত্ব সে অনুভূতি থেকে আলাদা । একটি বিশেষ চলা বা না চলার জন্য কে আমার কাজের ওপর বাধ্যবাধকতা আরোপ করবে ? কোনো স্রষ্টা আছেন কি যিনি আমার হিসাব নেবেন ? আপনি হয়ত বলবেন, ‘না’ । বিবেক-বিবেচনা আছে কি? আবারও অপনি হয়ত বলবেন, ‘না’। তাহলে কে?...
একেশ্বরবাদী বিশ্বজনীন দৃষ্টিভঙ্গি পথ নির্দেশক রূপে কাজ করে যেহেতু আদর্শ এবং দায়িত্ববোধ সৃষ্টির ক্ষমতা তার আছে । এটা লক্ষ্য অর্জনের পথ দেখায় । এটা আনন্দ এবং উৎসাহ যোগায় এবং আমাদের মধ্যে আত্মোৎসর্গের উদ্দীপনা জাগিয়ে তোলে । সর্বোপরি, আল্লামা তাবাতাবায়ী বলেছেন, এটা এমন এক মৌলিক বিষয় হতে পারে যা শিক্ষণের সকল উপাদান নিয়ে গঠিত । একেশ্বরবাদ- এর নীতি যেন পানি- যা সকল ধারণার শেকড়ে সিঞ্চিত হয় অথবা রক্তের মতো যা খাদ্য বয়ে নিয়ে যায় শরীরের সকল অংশে অথবা অত্মার মতো যা একটি মতবাদে জীবন ও গতিময়তার উদ্রেক করে । আদর্শ প্রসঙ্গে সারটার ও অন্যরা বলেন, কোনো সীমারেখায় মানুষের থেমে থাকা উচিত নয়, বরং তার বাইরেও তার যাওয়া উচিত এবং নতুন লক্ষ্যের জন্য তার আগের পরিকল্পনা পরিবর্তন করা দরকার । আর এভাবে তাকে আব্যাহতভাবে এগিয়ে যেতে হবে । এর অর্থ হলো একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্যপানে নিরবচ্ছিন্নভাবে গতিশীল থাকা যেমন একটি লোক সামনে হেঁটে চলছে আর চলছে যতক্ষণ না নতুন দিগন্ত তার চোখের সামনে খুলে যায় । সে কোনো নির্দিষ্ট স্থানে থামতে চায় না; কারণ, সে জানে ঐ স্থান হচ্ছে মৃত্যু । একেশ্বরবাদে লক্ষ্যটি শুরু থেকেই সেখানে আছে- খুবই স্পষ্ট এবং অসীম । প্রতিনিয়ত তা নতুন এবং অদম্য । অন্য কোনো বিশ্বজনীন দৃষ্টিভঙ্গিতে আদর্শ এবং উদ্দীপনা শক্তিরূপে মতবাদের উৎস ও চলৎশক্তির সমন্বয় ঘটেনি । সে সাথে একেশ্বরবাদ বাধ্য বাধকতা আরোপ করে, আনন্দ সৃষ্টি করে, নির্দেশনা প্রদান করে, আত্মোৎসর্গে উদ্বুদ্ধ করে, মানবজাতির ব্যাপক উন্নয়ন ঘটায়, যাতে সব সমস্যার সমাধান করা যায় । এটা একমাত্র একেশ্বরবাদের বিশ্বজনীন দৃষ্টিভঙ্গি যার এত সব গুণ ধারণ করার ব্যাপকতা রয়েছে ।
ইসলামী বিশ্বাস ও মানব পূর্ণতা
ইসলামে কী বিশ্বাসের কথা বলা হয়েছে এবং কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে, অক্ষরূপে যাকে কেন্দ্র করে সবকিছু আবর্তন করে? এখানে প্রথমেই উল্লেখ করা হয়েছে আল্লাহর কথা । দ্বিতীয়ত ফেরেশতা, পবিত্র আসমানী গ্রন্থসমূহ, নবী-রাসূল, পরকাল ইত্যাদির ওপর বিশ্বাস । ইসলামের বর্ণিত এ বিশ্বাস কি মানব জাতির কোনো লক্ষ্য নাকি অন্য লক্ষ্যসমূহের জন্য উপায় স্বরূপ ? এর সবই মানবের লক্ষ্য; কারণ, ঐশী লক্ষ্য বা উপায় সম্পৃক্ত নয় । এ লক্ষ্যগুলোকে পূর্ণতার পথে মানবের অর্জন বলে ধরা হয়।
বিশ্বাস নিজেই কি মানবের পূর্ণতা, যা তার প্রতি উপদেশরূপে এসেছে? নাকি এ বিশ্বাসগুলোর ইতিবাচক প্রভাবের কারণে এগুলোর ওপর বিশ্বাস পোষণ করতে মানবজাতিকে আহ্বান করা হয়েছে ? দার্শনিকরা প্রশ্নটি এভাবে করেছেন ‘বিশ্বাস স্থাপন মানুষের জন্য আশীর্বাদ নাকি উপকারী ? ‘আশীর্বাদ’ আর ‘উপকারী হওয়া’ এ দু’টির মধ্যে পার্থক্য রয়েছে । আশীর্বাদ নিজেই কাঙ্ক্ষিত পূর্ণতা, নিজের জন্য-অন্য কোনো কিছুর জন্য নয় । কিন্তু প্রয়োজনীয় কোনো জিনিস ভালো তার উপকারী প্রভাবের জন্য । এটা আশীর্বাদের ভূমিকা, নিজেই আশীর্বাদ নয়।
ইসলাম নিয়ে আলোচনায় এটা অবশ্যই পরিস্কার হওয়া দরকার যে, প্রভাব নির্বিশেষে একটি লক্ষ্য নাকি আশীর্বাদ । আমরা বিশ্বাসের প্রভাবের কথা বলি, বিশ্বাস দুর্ঘটনার বিপরীতে প্রশান্তি, সহিষ্ণুতা দিয়ে থাকে এবং এর ফলে সমাজে একে অন্যকে বিশ্বাস করে; পরস্পরের উপকার করে, ঈর্ষা থেকে দূরে থাকে।
কিন্তু বিশ্বাস কি ভালো প্রভাবের জন্য? নাকি নিজেই পূর্ণতা অন্বেষণ করে বলে? এখানে প্রশ্ন উত্থাপিত হয় কিসে হয় মানব পূর্ণতা? বস্তুর পূর্ণতা সংক্রান্ত প্রশ্নের চেয়ে এ প্রশ্নের উত্তর দেয়া অধিকতর কঠিন। এ বিশ্বে আমরা প্রতিনিয়ত বস্তুর পূর্ণতা নিরূপণ করে থাকি । একটা ভালো আপেল কেমন হওয়া উচিত? এতে স্বাদ, গন্ধ, বর্ণ, আকার-আকৃতি ইত্যাদি বোঝায় । আর যদি একটি আপেল এমন হয় তাহলে বলি আপেলটি পূর্ণতা লাভ করেছে।
একটি পূর্ণ বাড়িও সহজে নির্ধারণ করা যায়, একটি ঘোড়াও । কিন্তু সবচেয়ে কঠিন ব্যাপার হলো একজন পূর্ণ মানবের সংজ্ঞা দেয়া । ফলে তাকে নিয়ে বিভিন্ন প্রকার ধারণা খতিয়ে দেখা দরকার কোনগুলো সঠিক অথবা আমরা যদি বৈজ্ঞানিক উপায়ে না পারি অন্তত কুরআন কীভাবে এবং কতটুকু ধারণা অনুমোদন করে তা দেখা উচিত।
এটা কি বলা ঠিক হবে যে, সেই সত্তা পূর্ণ যে তার বহির্জগৎ-প্রকৃতি থেকে সর্বাধিক পরিমাণ সাফল্য অর্জন করে? কিন্তু না, দু’টি কারণে এটা ভুল; প্রথমত আমরা অন্য কোনো কিছুকে এভাবে সংজ্ঞায়িত করি না । অমার বলি না, ঘোড়াটি পূর্ণ; একমাত্র কারণ, সর্বোচ্চ উপকার পেয়ে থাকি । আমরা এর নিজস্ব গুণাবলী ও সম্পদ বিবেচনা করি । আমরা বিবেচনায় নেই না অনেক বেশি পরিমাণ খাবার খায় বলে ঘোড়াটি পূর্ণতা অর্জন করেছে । একটি আপেল বেশি বাতাস, আলো, পানি পেয়েছে বলেই তাকে পূর্ণ বলি না।
দ্বিতীয়ত বিবেচনাপ্রসূত নয় যে, যে লোকটি প্রকৃতি থেকে সবচেয়ে বেশি আহরণ করলো- সে পূর্ণমানব । কারণ, এতে মন্তব্য করা যায়, যে প্রকৃতি থেকে কম সুবিধা নিতে পারলো সে ত্রুটিপূর্ণ (পঙ্গু) কোনো মানব!
আমরা দু’টি মানব চরিত্র নিয়ে একটু আলোচনা করি : মুআবিয়া আশি বছর দীর্ঘ জীবনে প্রচুর পার্থিব কল্যাণ ভোগ করেছেন । চল্লিশ বছর ধরে তিনি সিরিয়ার শাসনকর্তা ছিলেন । ( ২০ বছর ধরে শক্তিশালী গভর্ণর আর বাকী ২০ বছর প্রভাবশালী খলীফা) অন্যদিকে আলী (আ.) কঠোর সংযমী জীবন যাপন করতেন যাঁর দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি ছিল হয়তো বা মুক্ত হওয়া, নয় মহৎ বা মানবিক হওয়া, অথবা এ পৃথিবী থেকে কিছু না নেয়া । তবে আধ্যাত্মিক বিষয়ে মনোযোগ দেয়ার ব্যাপারটা ছিল নিশ্চিত । যা হোক তাঁর পার্থিব ভোগের পরিমাণ ছিল কয়েক টুকরো রুটি। তাঁকে কি আমরা অসম্পূর্ণ মানব রূপে অভিহিত করবো পার্থিব ভোগ ন্যূনতম বলে?
যদি আমরা এমনটা বলি, তাহলে জন্তুর চেয়েও মানবকে খাটো করে ফেলা হয় । কারণ, এ পৃথিবী থেকে উপকৃত হবার মাপকাঠিতে আমরা জীব-জন্তুকেও মূল্যায়ন করি না; অবশ্য কেউ কেউ মানুষের মূল্যায়নে এর বাইরে কিছু চিন্তাও করে না । তবে এমন কাউকে পাওয়া যাবে না যে, আধ্যাত্মিক বিষয়াবলি অস্বীকার করে এগুলো বিশ্বাস করবে । এখানে আরেকটি বিষয়ের অবতারণা করা যায়, যদি এ পার্থিব সুখ অর্জন মানবের পূর্ণতার মাপকাঠি না-ই হয় তবে পরবর্তী বিষয়টির ব্যাপারে কী বলা যায়? অর্থাৎ মানবের পূর্ণতা হচ্ছে স্রষ্টার উপহার থেকে উপকৃত হওয়া-ঐ উপহার প্রাপ্তির যোগ্যতা অর্জন করা । তবে পার্থিব উপায়-উপকরণ দিয়ে এটা পরিমাপ করা সম্ভব নয় । তাই মানুষ প্রার্থনা করে পরকালে সর্বাধিক পরিমাণে উপকৃত হবার জন্য । এরকম প্রার্থনা নিয়ে ইবনে সিনা বলেন : ‘এরকম লোকরা প্রার্থনা করে শ্রমিকের মতো যারা বেতনের আশায় পরিশ্রম করে । অর্থাৎ বেতন ছাড়া তাদের কাজের কোনো আগ্রহ নেই।’
ইসলামী যুক্তির নিরিখে এ রকম বিশ্বাসে যে ইবাদাত করা হয় তা ত্রুটিপূর্ণ, যেমন শুধু বেহেশতে পুরস্কারের আশায় আনুগত্য দেখানো, উপাসনা করা । ইমামগণ থেকে এ প্রসঙ্গে প্রচুর সংখ্যক বর্ণনা আছে । ‘যারা ভয়ে ইবাদাত করে, তারা দাসের মতো যেন কেউ মনিবের ভয়ে কোনো কাজ করে।’ একই রকম কথা বলেছেন আলী (আ.)। (নাহজুল বালাগা, জ্ঞান গর্ভমূলক বাণী : ২২৯)
‘কেউ আল্লাহর উপাসনা করে লোভে; এটা হলো ব্যবসায়িক ইবাদাত; কেউ ভয়ে; এটা দাসের ইবাদাত; কেউ ইবাদাত করে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য আর এ ইবাদাত বিনয়ীর ইবাদাত।’ অন্যত্র আলী (আ.) আরও পরিস্কার করে বলেছেন, ‘হে আল্লাহ! আমি জাহান্নামের ভয়ে বা জান্নাতের লোভে তোমার ইবাদাত করি না; আমি তোমার ইবাদাত করি; কারণ, তুমি ইবাদাতের যোগ্য।’
কাজেই বস্তুগত সর্বোচ্চ সুবিধা ভোগ করার সামর্থ্য দিয়ে মানব পূর্ণতা পরিমাণের ধারণা সঠিক নয় । এমনটি এ পৃথিবীর গুণরাজি অস্বীকার করে বা ভবিষ্যৎ জীবনের পার্থিব সুবিধাদি জমা রেখেও মানব পূর্ণতা পরিমাণের বিষয়টি সঠিক নয় । বিভিন্ন রকম বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে যার সবকিছুই শুধু কল্যাণের ধারণায় পর্যবসিত হয়।
আধ্যাত্মিক ধারণা নিম্নরূপ
১. সম্ভবত ‘পূর্ণ মানব’ সংক্রান্ত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ধারণাটি হলো জেনো’র ধারণা । বিভিন্ন ধর্মে প্রভাবিত হয়ে তাঁরা এ ধারণার সূত্রপাত ঘটিয়েছেন । বিভিন্ন ধারণা, যেমন ‘আদম’, ‘নবী -রাসূল’, ‘সিদ্ধপুরুষ’ এবং ‘প্রতীক্ষিত মাহদী’র মতো পূর্ণ মানব থেকেও তাঁরা প্রভাবিত । ম্যাকিনিয়ন ‘ইসলামে পূর্ণ মানব’ নামে বই লিখেছেন । আবদুর রহমান বাদাভী বইটি আরবি ভাষায় অনুবাদ করেছেন । এখানে তিনি বলেন, ‘পূর্ণ মানব তত্ত্ব গ্রীক সনদে প্রাপ্ত নয়; কারণ, এ ব্যাপারে গ্রীক দর্শনে কিছুই বলা হয়নি।’
ইসলামী জগতে সূফীবৃন্দ, যেমন মহিউদ্দীন আরাবী এ বিষয়টি উত্থাপন করেছেন । অনুরূপ বই-পত্র লিখেছেন আবদু-করিম দেইলামী, আজিজ আল দীন নাসাফী এবং একজন সূফী কবি সাইয়্যেদ মুহাম্মাদ বরকতি । জেনো মানবের পূর্ণতার ও পূর্ণ মানব-এর ব্যাপারে সুস্পষ্ট ধারণা পোষণ করতেন যা অন্যদের কাছে হয়ত পুরোপুরি গ্রহণযোগ্য ছিল না; তবে তাঁরা চূড়ান্ত নির্ধারণী মন্তব্যে তা উপস্থাপন করতেন।
তাঁরা বিশ্বাস করতেন, একটি সত্য আছে, আর তা হলো স্রষ্টা । অন্য সবকিছু ঐ সত্যের ছায়া মাত্র । তাঁদের ধারণা সবকিছুই স্রষ্টার মহিমা প্রকাশ করে । যদি আমরা ঐ সত্যের পরিচয় না পেয়ে মারা যাই আমাদের মৃত্যু হবে অবিশ্বাসীর, মূর্খের, অন্ধকারের এবং চরম উদাসীনতার মৃত্যু । একজন মানুষ পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয় যখন সে ঐ সত্যকে বুঝতে পারে এবং তা অর্জন করে । তাঁদের ধারণা এটা অসম্ভব যে, স্রষ্টা মানুষের মধ্যে উপস্থিত হবেন বা তার সঙ্গে সংযুক্ত হবেন । তাঁদের ধারণামতে রূপধারণ হচ্ছে দ্বৈততা । কাজেই সত্য পাওয়া বা স্রষ্টাকে পাওয়ার অর্থ হলো নিজেকে স্রষ্টায় বিলীন করে দেয়া । আর তা হবে সত্যকে পুরোপুরি উপলব্ধি করার পর আর তখনই সে নিজেকে চিনবে । স্রষ্টা হচ্ছেন একমাত্র সত্য আর বাকী সব কিছুই তাঁর প্রকাশ । এটা মোটামুটি স্রষ্টার কাছে পৌঁছানোর মতো একটা ধারণা । এ ধারণা মতে তাঁরা বিশ্বাস করেন, তা না হলে নির্দিষ্ট নিয়মে ধাপে ধাপে স্রষ্টার দিকে এগুতে হবে । কাজেই জেনো মতবাদের সত্য অর্জনের বিভিন্ন ধাপ রয়েছে । যে তা অর্জন করতে পারে না সে অপূর্ণ, আর মানবতা নির্ভর করে সত্যকে জানা ও অর্জন করার ওপর।
সত্য ও স্রষ্টার দিকে এগিয়ে যেতে সহায়ক হচ্ছে প্রেম, সহানুভূতি ও পরিচিতি । তাঁর দিকে যাবার পথে দর্শন বা মন দিয়ে নয়- হৃদয় দিয়ে এগুতে হয় । অন্য সকল পূর্ণতা, তাঁর পূর্ণতা থেকে উৎসারিত । আর কেবল এ কারণেই একে পূর্ণতা বলে বিবেচনা করা হয় । সংযম কি পূর্ণতা? তারা বলবেন, হ্যাঁ! কারণ, ঐ পথে চলার জন্য এটা একটা শর্ত । বিনয়, সহায়তা, পথনির্দেশসহ এরূপ আরও বিভিন্ন সদগুণাবলি যেগুলোর নৈতিক কল্যাণ রয়েছে সেগুলো ঐ পথে চলার শর্ত ।
২. ঐশী মতবাদে বিশ্বাসী দার্শনিকরা জেনো’র ধারণার সাথে ভিন্নমত পোষণ করেন । তাঁদের মতানুসারে মানবের পূর্ণতা দু’টি বিষয়ের ওপর নির্ভরশীল; ঘটনার স্বীকৃতি ও জ্ঞান । জেনো গুরুত্ব দেন ‘সত্যের’ ওপর, কিন্তু ঐ দার্শনিক গুরুত্ব দেন জ্ঞানের ওপর, যা হলো বস্তু ও তার অস্তিত্বের বাস্তবতা সম্পর্কে উপলব্ধি; সাধারণত জ্ঞান নয় । যেমন : আপেলের বৈশিষ্ট্যাবলি বিজ্ঞানের সাথে সম্পর্কিত, জ্ঞানের সঙ্গে নয় । আবার একটি নগরী বা বাড়ি সম্পর্কে সামগ্রিকভাবে জানা আর তার ভিন্ন ভিন্ন অংশ সম্পর্কে জানা এক নয়।
একজন সাধক বিশ্বজগতের বৈজ্ঞানিক ও সঠিক স্বীকৃতির সাধারণ প্রেক্ষাপটে মানবপূর্ণতাকে বিবেচনা করেন । তার কাছে বস্তুগত এ জগৎ বৈজ্ঞানিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক যা উদ্দেশ্যমূলক জগতের সাথে সংযুক্ত । যেমন : উদ্দেশ্যমূলক জগতে একজন স্রষ্টা আছেন, তাঁর চিরন্তন নিয়ম-শৃঙ্খলা, বস্তু ও অবস্তুও রয়েছে সেখানে । বিজ্ঞানসম্মত বা বুদ্ধিবৃত্তিক জগতেও এ বিষয়গুলো নিশ্চিতভাবে বিরাজ করে । তাদের ধারণামতে একজন পূর্ণ মানবকে তাই জ্ঞানের স্বীকৃতি দিতে হবে । আমরা জ্ঞানের সাক্ষ্য-প্রমাণ দিয়ে আলোচনা করতে পারি; কিন্তু আমরা এর উৎস বা নিয়মনীতি নিয়ে কিছু বলতে অপারগ । পবিত্র কুরআন ঘোষণা করে, ‘জ্ঞানের আশীর্বাদ যে কারও ওপর মঞ্জুর করা যেতে পারে যে ইচ্ছা পোষণ করে এবং যে তা গ্রহণ করে অফুরন্ত কল্যাণ খুঁজে পায়।’ (সূরা বাকারা : ২৬৯)
জ্ঞানের পাশাপাশি পূর্ণতার পূর্বশর্ত রূপে এমন সাধক ন্যায়বিচারকে শর্ত বলে মনে করেন-নৈতিক ন্যায়বিচার যার ওপর সামাজিক বিচার নির্ভরশীল । এর অর্থ দাঁড়ায় মানুষের শারীরিক শক্তি ও বুদ্ধিবৃত্তিক শক্তি যা তার অন্তর্নিহিত বিষয়াবলির ওপর প্রাধান্য বিস্তার করে এ দুয়ের মধ্যে ভারসাম্য থাকা উচিত । অন্য কথায় বুদ্ধির উচিত সকল ক্ষুধা, তাড়না ও কল্পনার ওপর প্রাধান্য বিস্তার করা যাতে এগুলোর প্রতিটি শক্তি যোগ্যতা অনুযায়ী পরিমিত অংশ নিতে পারে । সাধকদের পরিভাষায় জ্ঞানের সাথে সম্পর্কিত বিষয়াবলিকে অনুসন্ধিৎসু বুদ্ধি, আর বিচার সম্পর্কিত বিষয়াবলিকে ব্যবহারিক বুদ্ধি বলে অভিহিত করা হয়।
‘বিশ্বাস’ সংক্রান্ত প্রশ্নটিকে ‘জ্ঞান’ প্রসঙ্গে পুনরায় উত্থাপন করা যায়। জ্ঞান কি মানুষের ‘সমাপ্তি’ বা ‘উপায়’ তুলে ধরে? জ্ঞান নিজেই কি ‘সমাপ্তি’, ‘উপায়’ নাকি উভয়? জ্ঞান কি মানবের পূর্ণতা । যদি তা-ই হয় তাহলে তা সুবিধাদি সম্পর্কিত হয়ে পড়ে, আর সুবিধা ছাড়া তা মূল্যহীন হয়ে য়ায় এবং যতই সুবিধা ততই এটা ভালো হয়।
৩. তৃতীয় একটি মত অনুযায়ী মানবের পূর্ণতা আবেগ-অনুভূতিতে অন্তর্নিহিত; যেমন প্রেম । এটা একটা নীতিগত দৃষ্টিভঙ্গি যা দাবি করে অন্যদের প্রতি যার সহমর্মিতা বেশি সে-ই পূর্ণ । আর যদি সে অন্যদের প্রতি নামমাত্র সহানুভূতিশীল হয় সে অপূর্ণ এক মানুষ । নৈতিক বঞ্চনার ভিত্তি হচ্ছে স্বার্থপরতা । স্বার্থপরতাকে যে যত বেশি দূরে রাখতে পারে সে তত বেশি পূর্ণ । এ বিষয়ের ওপর হিন্দুরাও বেশ গুরুত্ব আরোপ করেছে । ‘এ আমার বিশ্বাস’ গ্রন্থে গান্ধী এ বিষয়টির ওপর ব্যাপক গুরুত্ব দিয়েছেন । হিন্দু ধর্মে সত্য ও সুন্দর (প্রেম) দু’টির ওপরই জোর দেয়া হয়েছে এবং এ দু’টি বিষয় অস্বীকারকারী পশ্চিমা সভ্যতার সমালোচনা করেছে।
৪. মানবপূর্ণতা নিয়ে আরেকটি মতবাদ হচ্ছে সৌন্দর্য। অবশ্য এ সৌন্দর্য বাহ্যিক নয়, আধ্যাত্মিক । শৈল্পিক বস্তু শৈল্পিক মেজাজ প্রকাশ করে, আর সব সুন্দর বস্তুর সৃষ্টি হয় ।
৫. আরেকটি দৃষ্টিভঙ্গি যা পাশ্চাত্য ধারণারূপে খ্যাত তা বস্তুবাদী । এ মতবাদে মানবপূর্ণতা ক্ষমতায় নিহিত । যে ব্যক্তি যত বেশি ক্ষমতাশালী, নিজ গণ্ডি ও অন্যদের ওপর যত বেশি প্রভাবশালী, সে তত পূর্ণ । ডারউইনের বিবর্তনবাদেও এ ধারণা প্রতিফলিত হয় । ডারউইনের মানদরণ্ড অধিকতর পূর্ণ সত্তা নিজের সুরক্ষায় অবশ্যই যথেষ্ট শক্তিশালী এবং টিকে থাকার লড়াইয়ে সে প্রতিপক্ষকে নির্মূল করতে সক্ষম । ডারউইনের সমালোচনা করা হয়েছে তাঁর ‘টিকে থাকার লড়াই’ সংক্রান্ত তত্ত্বে নীতি-নৈতিকতার কোনো স্থান না দেয়ার কারণে । অনেক পশ্চিমা পণ্ডিতও স্বীকার করেছেন জ্ঞানই মানুষের উপকার করে, তাকে আরও ক্ষমতাবান করে এবং প্রকৃতিতে বিরাজ করে । এভাবে তাঁরা বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের প্রচার চালান সভ্যতা ও প্রযুক্তি উন্নয়নের অনুঘটক রূপে । এ ধারণার প্রয়োগও রয়েছে এবং তা এমন পরিসরে চলছে যে, উপকারের চেয়ে ক্ষতিই বেশি হচ্ছে । তাঁরা জ্ঞান, সততা, প্রেম এবং বিশ্বাস-এর পবিত্রতা অগ্রাহ্য করেছেন যা আগে মানবজাতি বিশ্বাস করতো । তাঁদের মতে সব কিছুই ক্ষমতার কাছে নতি স্বীকার করে আর তাই তার মানবিক অগ্রগতির পথ পরিবর্তন করেছে । আর তখন থেকেই মানুষ আধ্যাত্মিকতায় বিশ্বাস ছেড়ে দিয়েছে । যদি তাঁরা আধ্যাত্মিকতার দাবি করেন, তা হবে তাঁদের প্রতিপক্ষের কাজ ।
নিৎসে’র দর্শন সমালোচিত হয় অনেক আড়ম্বরতার কারণে । তবে তিনি খোলাখুলি ও পরিস্কার ভাষায় কথা বলতেন । তাঁর যৌক্তিক উপসংহার- ক্ষমতার সেবায় বিজ্ঞান নিয়োজিত, আর মানবের পূর্ণতা স্বীকৃত তার ক্ষমতায় ।
ইসলামী একেশ্বরবাদ : উপসংহার
মানবের পূর্ণতা প্রসঙ্গে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি কী? যখন একটি মতবাদ কোনো আদর্শ স্থাপন করতে চায় তখন অবশ্যই নির্দেশিকা ও তা মেনে চলার কারণ জোরালোভাবে উপস্থাপন করে এবং সামনে লক্ষ্য-উদ্দেশ্য উপস্থাপন করে তা সবাইকে অনুসরণ করতে আহ্বান জানায় । ইসলামের লক্ষ্য হচ্ছে সত্যিকারের একজন মুসলমানের সত্যিকার উদ্দেশ্য । একজন পূর্ণ মানবের ধারণা তুলে ধরা হচ্ছে আসলে ইসলামী আদর্শ ও এতৎসংক্রান্ত নীতিমালা নিয়ে একটি মৌলিক আলোচনা । মানব-পূর্ণতা এবং একটি পূর্ণ-সত্তা নিয়ে বিভিন্ন মতবাদ ইতোমধ্যে আলোচিত হয়েছে । এখানে একটি উপসংহার টানা হবে।
জেনো-এর ধারণামতে ‘সত্য’ হচ্ছে সবকিছুর ভিত্তি । ‘সত্য’ শব্দটি দিয়ে তাঁরা ‘স্রষ্টার আভাস’ এবং সৃষ্ট সকল আকার-আকৃতি ও বস্তু ‘স্রষ্টার প্রকাশ’ বলে অর্থ করেন । এভাবে যে ‘সত্য’ স্রষ্টা তা ছাড়া অন্য সবকিছুই তাঁর ছায়া, তবে সত্য নিজেই এক বাস্তবতা । স্রষ্টা বলতে পরম প্রভুকে বোঝানো হয়েছে, কেউ যাঁর সমকক্ষ নয় বা যাঁর সাথে তুলনীয় নয় । তাঁরা আরো বিশ্বাস করেন, মানুষ স্রষ্টার সাথে মিশে যেতে পারে অথবা তাঁরা যেমন বলেন, স্রষ্টায় বিলীন হয়ে যেতে পারে । মানুষ একটি সত্তা, তার স্রষ্টা থেকে ভিন্ন সত্তা; মানবের পূর্ণতা বা সুখ তার উৎস-স্রষ্টার কাছে ফিরে যাওয়ার মধ্যে নিহিত । তাঁরা এ লক্ষ্য অর্জনের পথ ও উপায় প্রদর্শন করেন, আর তা একজন মানুষের সারা সত্তায় নিহিত যেমন এর হৃদয় এবং তার পরিবর্তন-পরিবর্ধন যা পূর্ণ একত্বের পথের প্রতিবন্ধকতা সরিয়ে দেয় । তাদের উপায় হলো প্রেম, উপাসনা ও আত্মশুদ্ধি ।
ঐশী মতবাদে বিশ্বাসী দার্শনিকরা বিষয়টি ভিন্নভাবে দেখেন । তাঁরা বলেন, মানুষের অস্তিত্ব তার বুদ্ধিতে আর বাকী সব বিষয় দ্বিতীয় পর্যায়ের । বুদ্ধিবৃত্তিক ক্ষমতার পূর্ণতার দু’টি দিক : অনুসন্ধিৎসু ও ব্যবহারিক । অনুসন্ধিৎসু বা তাত্ত্বিক দিকে আছে জ্ঞান যার অর্থ হলো যা যেমন আছে তাকে সেভাবে উপলব্ধি করা, আর ব্যবহারিক দিকে আছে ন্যায়বিচার । ন্যায়বিচার বলতে বোঝায় মানবের সমগ্র সত্তার ওপর অন্তর্নিহিত কোনো কামনা যা শক্তি নয়- বুদ্ধিবৃত্তিই বিজয়ী হবে । প্লেটো তাঁর ‘থিওরী অব রিপাবলিক’-এ এমন একটি বিষয় তুলে ধরেন যে, দার্শনিকরা শাসকে বা শাসকবর্গ দার্শনিকে রূপান্তরিত হন । এ তত্ত্বটি ব্যক্তি পর্যায়েও ব্যবহার কার যায় এবং বলা হয়, একজন তখনই সুখী হয় যখন তার অস্তিত্ব দর্শন দিয়ে পরিচালিত হয়। তাঁদের মতে সত্য অর্জন বিবেচ্য বিষয় নয়; তাঁরা চিন্তাধারা এবং প্রতিক্রিয়ার ওপর জোর দেন- হৃদয় বা আত্মার ওপর নয়। ঐ লক্ষ্য অর্জনের পথ হলো বুদ্ধিবৃত্তি, যুক্তি এবং কার্যকারণ।
অন্য একটি গোষ্ঠী প্রেমকে মানবপূর্ণতা বলে বিবেচনা করে । এর অর্থ নিজেকে ভুলে যাওয়া এবং অন্যদের ভালোবাসা যাতে আপন-পরের মধ্যে কোনো সীমারেখা না থাকে । আর যখনই কোনো পছন্দের প্রশ্ন আসে তখন অন্যকে নিজের ওপর অগ্রাধিকার দিতে হবে । কারও মানবিক আবেগ- অনুভূতি তার সীমারেখার লক্ষ্য পর্যন্ত বিকশিত হলে তাকে পূর্ণ মানব বলা যেতে পারে ।
আবার অন্য একটি মতবাদে পূর্ণমানবের অস্তিত্ব রূপে সৌন্দর্যের কথা বলা হয় যে সৌন্দর্য হবে আত্মিক, বাহ্যিক নয় । বাহ্যিক সৌন্দর্য কোনো গুরুত্ব বহন করে না । সক্রেটিস এর ধারণার মূল কথা ছিল এটি । তাঁরা বলেন, সত্যবাদিতা ভালো; কারণ, তা সুন্দর । ‘ভালো’ শব্দটি বোধ এবং বুদ্ধি উভয় ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়েছে।
জ্ঞান তাঁদের জন্য একটি পূর্ণতা, কারণ, তা সুন্দর । বিপরীতে মূর্খতা, ক্ষমতা, দায়ভার এবং দুর্বলতাও একই মানদণ্ডে বিচার্য । কবিতা, শিল্প এবং মৌলিকত্বের অর্থ দাঁড়ায় সুন্দরের সৃষ্টি, আর এ সুন্দরের স্রষ্টাও নিজে সুন্দর এবং সুন্দর সৃষ্টিতে সক্ষম । কেবল সুন্দর আত্মা-ই সুন্দর কবিতা বা সুন্দর আঁকতে পারে। কাজার বংশীয় এক রাজা সম্পর্কে একটি গল্প শোনা যায় । তিনি দু’লাইনের একটি ছন্দের একটি লাইন লিখলেন; দ্বিতীয় লাইনটি আর লিখতে পারলেন না । তিনি বিভিন্ন কবির সহায়তা চাইলেন । অবশেষে একজন দ্বিতীয় লাইনটি লিখলো যা সবচেয়ে মানানসই । প্রথম লাইনটি ছিল ‘ইউসূফের মতো সৌন্দর্য আর কেউ দেখেনি’ আর দ্বিতীয় লাইনটি হলো ‘তবে যে ইউসূফকে সৃষ্টি করেছেন, প্রকৃত সৌন্দর্য তাঁরই । এটা খুবই সত্য কথা শুধু পরম সৌন্দর্যের অধিকারী স্রষ্টা-ই পারেন তাঁর সৃষ্টির মাঝে সৌন্দর্য ভরে দিতে।
এবার আসুন এসব মতবাদ সম্পর্কে ইসলামে কী মন্তব্য পাওয়া যায় । ‘সত্য’-ই পূর্ণতা- ইসলাম কি এটা মেনে নিয়েছে? আমরা সামগ্রিকভাবে জোনো-এর মতবাদ গ্রহণ করতে পারি না । কারণ, ইসলাম অনুসারে, পিতা বলতে যে ভাব প্রকাশ পায় স্রষ্টা তেমন কোনো স্রষ্টা নন (পিতা তার মতো আরও সত্তা জন্ম দিতে সক্ষম)। যদি তা-ই হয়, সৃষ্টির কর্ম সম্পাদনের পর তিনি কে? তিনি কি পিতার মতো যার সন্তানাদি আছে? নাকি কেবল সৃষ্টের জীবিকা প্রদান করেই ক্ষান্ত । নাকি অ্যারিস্টটল যেমন বলেছেন প্রথম চালিকা শক্তি?
ইসলামে স্রষ্টার ব্যাপারে যুক্তি, ‘তাঁর সাথে কারও তুলনা হয় না’ এ যুক্তির চেয়ে উঁচু স্তরের । পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে, ‘আল্লাহ আসমান যমিনের নূর’-(সূরা নূর : ৩৫) অর্থাৎ তিনি তিনিই, অন্য সব কিছু তাঁর অধিকারভুক্ত । কুরআনের অন্যান্য বর্ণনায় পাওয়া যায় তিনি ‘পরম সত্য’। কুরআনে আরো বলা হয়েছে : ‘আমরা শিগগিরই তাদেরকে বিশ্ব জগতে ও তাদের হৃদয়ে আমাদের চিহ্ন দেখাবো যাতে তাদেরকে নিশ্চিত করা যায়- কুরআন সত্য।’ (সূরা হা-মীম আস সাজদা : ৫৩) আসলে, যখন কেউ আল্লাহকে বিশ্বাস করে, তার জন্য সব কিছুই হ্রাস পেয়ে অনস্তিত্বে রূপান্তরিত হয় । কারণ, সে এমন জিনিস পেয়েছে যার তুলনায় আর সব কিছুই মূল্যহীন । সাদী তাঁর কাব্যগ্রন্থ
বুস্তানে বিষয়টি সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন-
‘বুদ্ধিজীবীর জন্য এ পথ গোলক ধাঁধাঁ,
তবে জ্ঞানীদের জন্য আল্লাহ্ ছাড়া আর কেউ নেই।’
তিনি তখন তার প্রশ্নের জবাব দেন :
‘হে আমার বিজ্ঞ বন্ধু! ভালো প্রশ্ন করেছো; আমি তোমার বুদ্ধিবৃত্তিক অনুমোদনের জবাব দেব । এই যে সূর্য, সাগর, পাহাড়, আকাশ, মানুষ, দৈত্য-দানব, জ্বিন এবং ফেরেশতাবর্গ, যা-ই হোক না কেনো, তারা স্রষ্টার অস্তিত্বের সামনে অস্তিত্বের প্রশ্নে অতি নগণ্য।’
যদি তিনি-ই সত্তা, বাকী সব কিছু অনস্তিত্ব হয়, তাহলে স্রষ্টাকে চেনার পর কারও পক্ষে অন্যদিকে ফিরে যাওয়া বা অন্য কোনো লক্ষ্য নির্ধারণ অসম্ভব । কাজেই স্রষ্টার সাথে অন্য কোনো স্রষ্টার তুলনা করার সম্ভাবনা অপেক্ষা ইসলাম অনুযায়ী বিশ্বাস অনেক ঊর্ধ্বে । স্রষ্টা সত্য, বাস্তবতা যাঁর সামনে আর কিছুই সত্য বা আসল নয়।
কিন্তু সাধকরা যে জ্ঞান-এর কথা বলেন ইসলামে কি তা গুরুত্বপূর্ণ? জ্ঞান সংক্রান্ত নীতি-যা যেমন আছে তার স্বীকৃতি-এটা ইসলামে অনুমোদন পায় । কুরআনে বলা হয়েছে, ‘তিনি যাকে ইচ্ছে করেন তার প্রতি জ্ঞানের আশীর্বাদ মঞ্জুর করেন, আর যে তা পায় সে অফুরন্ত কল্যাণ লাভ করে।’ (সূরা বাকারা : ২৬৯) এ আয়াত আমরা কীভাবে ব্যাখ্যা করবো ? জ্ঞানকে বলা হয়েছে মানবীয় কল্যাণ এবং তা প্রায় পূর্ণতার কাছাকাছি- তা কেবল প্রয়োজনীয় তা নয়।
ন্যায়বিচার অর্থাৎ সামাজিক ন্যায়বিচারও অনুরূপ । অবশ্য সামাজিক ন্যায়বিচার নৈতিক বিচার প্রসঙ্গে ব্যক্তি পূর্ণতার সাথে সম্পর্কযুক্ত । ইসলাম বিশ্বাস করে ক্ষমতা এবং অভ্যন্তরীণ আবেগ-অনুভূতির প্রতি নমনীয় সম্মানবোধ বজায় রাখা, তবে তা আড়ম্বরতা প্রত্যাখ্যান করে । এক বুদ্ধিবৃত্তিক বা বিশ্বাসের শাসনকে ইসলাম যথেষ্ট রূপে অনুমোদন করে না । মানব শক্তির দার্শনিকতাকে ইসলামে দেখা হয় মানব শাসনের অনুপযুক্তরূপ দুর্বলতা হিসাবে । বিশ্বাসের সাথে দর্শনের সংযোগ হলে তা গভর্নর হিসাবে ভূমিকা পালন করতে সক্ষম । তবে ইসলামে ‘প্রেম’ প্রসঙ্গে নবীজীর হাদীস অপেক্ষা আর বেশি কী বলা যায়? দয়া ও পারস্পরিক সহনশীলতা প্রসঙ্গে আমাদের পয়গাম্বর (সা.) তাঁর সাহাবীদের জিজ্ঞাসা করলেন, ‘বিশ্বাসের কোন্ শাখাটি অধিকতর শক্তিশালী?’ তাঁদের প্রত্যেকে ভিন্ন ভিন্ন উত্তর দিলেন, কেউ বললেন, ‘নামায’, কেউ ‘রোযা’, কেউ বললেন, ‘হজ্ব’ ইত্যাদি। তিনি বললেন, ‘তোমরা যা বলেছ তা সত্য, তবে এদের কোনোটি-ই সবচেয়ে শক্তিশালী নয়।’ তাঁরা জিজ্ঞাসা করলেন, ‘তাহলে সেটা কী?’ তিনি জবাব দিলেন, ‘আল্লাহর সন্তুষ্টির আশায় অন্যকে ভালোবাসা ।’
ওপরের বিশ্বাসগুলোর কোনটি গুরুত্ব বিবেচনায় প্রথম, আর কোন্গুলো এর পরিপূরক? ইবাদাত নিয়েও প্রশ্ন রয়েছে । পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে : ‘আমি জ্বিন ও মানব জাতিকে আমার ইবাদাত করা ছাড়া অন্য কোনো উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করিনি।’
কাজেই ইবাদাতকে উদ্দেশ্য হিসাবে উপস্থাপন করা হয়েছে যদিও কেউ কেউ এটা মানতে নারাজ । আমরা ইতোমধ্যে আলোচনা করেছি সেসব মতবাদ যা বস্তুগত সুবিধাদি সমুন্নত করে এবং মানবের পূর্ণতা এবং পূর্ণ সত্তার অস্তিত্বও অস্বীকার করে । তাঁরা জ্ঞানসহ সব কিছুকে মানবজাতির জন্য কল্যাণকর বলে বিবেচনা করে থাকেন।
বেকনের সময় থেকে মানুষের চিন্তাধারা এমনই ছিল । আজ দাবি করা হয় সমাজ উন্নত হয়েছে, বিবর্তিত হয়েছে । তাহলে কোন্ সমাজ বেশি পূর্ণ? সে সমাজ যা বাস্তবতার কাছাকাছি না বিশ্বাসের? নাকি সে সমাজ যেখানে জ্ঞান, ন্যায়বিচার বা প্রেম আছে? তাঁরা বলেন : ‘না, এটা সে সমাজ যা বেশি স্বার্থ নিশ্চিত করে, বেশি প্রযুক্তি, আরও বেশি বিজ্ঞানময় যার সবটাই মানবজাতিকে উন্নততর আরাম-আয়েশ এবং বস্তুগত স্বার্থ উপহার দেয়।’ এই যে অধিকতর স্বার্থ যা তাঁরা দেখতে পান তা জীব-জন্তু ও বৃক্ষলতা যা ভোগ করে তার চেয়ে বেশি কিছু নয় । এগুলো শারীরিক স্বাস্থ্য ও বৃদ্ধি, ক্ষুধা ও কামনা-বাসনা তৃপ্তিই নিশ্চিত করে মাত্র । কাজেই তাঁদের মতে জীবজন্তু ও বৃক্ষ –লতার পূর্ণতা ছাড়া আর কোনো মানবিক পূর্ণতা থাকতে পারে না । বিজ্ঞানও মানুষের তেমন যেমন একটি জন্তুর জন্য শিং যা অস্ত্র হিসাবে টিকে থাকার লড়াইয়ে ব্যবহৃত হয়।
আসুন এবার আমরা উপাসনার কথায় আসি । কেনো ইবাদাত করবো? দু’টি দৃষ্টিতে এটা দেখা যেতে পারে। সাধারণ মানুষের জন্য উপাসনা পরবর্তী জীবনে আল্লাহর কাছ থেকে পুরস্কার পাওয়ার উপায় । এ পৃথিবীর পুরস্কার সীমিত, তাই ইবাদাত এ জীবনের পর আরো গভীরতর এবং বৃহত্তর পরিসরে পুরস্কার পাবার আশা জাগ্রত করে । যেমন : হুর, বেহেশতী প্রাসাদ, মধু, সুস্বাদু ফল ও পানীয় । কিন্তু এটাও জীবের পূর্ণতার বাইরে কিছু নয় যদিও তা চিরকালের জন্য দেয়া হবে । ইবাদাতের অন্য অর্থও থাকতে পারে । যা দাসের ইবাদাত নয় যে পরকালে পুরস্কার লাভ করা যাবে । শারীরিক বা বস্তুগত দুঃখ-দুদশা থেকে মুক্তি লাভও উদ্দেশ্য নয় । এটা প্রাণীর ক্ষুধা থেকে অনেক দূরের বিষয় । এ ইবাদাত প্রেমের, আবেগ-অনুভূতির, কৃতজ্ঞতার । তখনই ইবাদাতের অর্থ খুঁজে পাওয়া যায় যা সত্যের প্রেম-এর সমার্থক- সমমানের । স্রষ্টা আর তখন ইহকাল বা পরকালে জীবনের উপায় রূপে বিবেচিত হন না । স্রষ্টা-ই তখন নিজে সত্য এবং প্রকৃত লক্ষ্য রূপে উদ্ভাসিত হন । এ ধরনের ইবাদাত অনেক উন্নত স্থানে সমাসীন; কারণ, এটা মাধ্যম নয়, ঐ সত্তায় তার সমাপ্তি।
এভাবে ইবাদাতের বিভিন্ন পর্যায়ে রয়েছে । পরকালে জীবের কামনা-বাসনা পূরণের জন্য ইবাদাত-যা ইবাদাতের অনুপস্থিতিতে তুলনামূলক এক প্রকার পূর্ণতা বোঝায় এবং তা বস্তু সাম্রাজ্যে এক প্রকার ইতিবাচক সহাবস্থান । কারণ, এর অর্থ দাঁড়ায় স্রষ্টার কাছে চিরস্থায়ী কিছু একটা কামনা করা-এ জগতে স্বার্থপরতা ও কামনা-বাসনার পরিবর্তে । তবে এরকম ইবাদাত সত্যিকার ইবাদাতের তুলনায় অনেক নিম্ন মানের । কাজেই ইবাদাত বিশ্বাসের ওপর নির্ভরশীল এবং বিশ্বাস নির্ভর করে সত্যের ওপর । ইসলাম মানবজাতিকে জ্ঞান, ন্যায়বিচার, প্রেম ও সৌন্দর্যের প্রতি আহ্বান জানায় । কিন্তু প্রধান লক্ষ্য কোনটি? এর সবগুলোই কি সমান গুরুত্ববহ? নাকি এর একটি প্রধান উদ্দেশ্য এবং অন্যগুলো এর পরিপূরক?
আমরা মনে করি, লক্ষ্য হচ্ছে ‘সত্য’ (স্রষ্টা) আল্লাহ্ । ইসলামী একেশ্বরবাদের কেবল এ অর্থই গ্রহণযোগ্য । যদি ইসলাম অন্য লক্ষ্য নির্ধারণ করে, যেমন : বেহেশত-দোযখ থেকে পলায়ন, এগুলো দ্বিতীয় সারির গুরুত্ব বহন করে । জ্ঞান নিজে লক্ষ্য নয় তবে সত্যের অন্বেষণে সহায়ক । ন্যায়বিচার ও মানবাত্মার পশুত্ব দমনে এবং সত্যের পথে কৃত্রিম বাধা-বিপত্তি দূরীকরণে কল্যাণকর । প্রেমও সত্য অর্জনে সহায়তা করে । বিশ্বাস যা ইসলামের লক্ষ্য হিসাবে বিবেচিত হতে পারে । কিন্তু বিশ্বাস কি দুর্দশা দূরীকরণে, আগ্রাসন প্রতিরোধে এবং পারস্পরিক আস্থা স্থাপনে ভূমিকা পালনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ? স্রষ্টার বিশ্বাস নিজেই একটি লক্ষ্য । বিশ্বাসের প্রভাব, যা অসংখ্য মানুষকে স্রষ্টার সাথে সংযুক্ত করে, আর ইসলামের দৃষ্টিতে এ সংযোগ-ই হচ্ছে পূর্ণতা।
সূত্র:(ঢাকা থেকে প্রকাশিত ত্রৈমাসিক পত্রিকা প্রত্যাশা, বর্ষ-১, সংখ্যা-১)