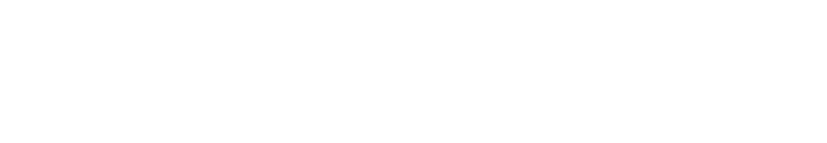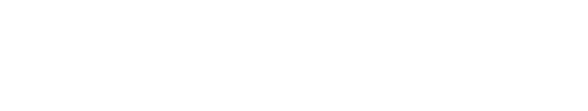জীবন ও জগতের পশ্চাতে কোন্ সত্য নিহিত? ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুজগতের অন্তরালে কোনো অতিন্দ্রিয় জগত আছে কি? বিশ্বজগতের কোনো আদি স্রষ্টা আছেন কি? মানুষের বস্তুদেহের অন্তরালে কোনো অবস্তুগত সত্তা আছে কি? তার চেয়েও বড় কথা, আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের স্বরূপ কী? বস্তুরই বা স্বরূপ কী? আমরা নিজেরাই বা কী অথবা কে?
এ সব প্রশ্ন হচ্ছে এমন কতগুলো মৌলিক জিজ্ঞাসা যা প্রতিটি মানুষের অন্তরে জাগ্রত হতে বাধ্য। আর সামাজিক পরিমণ্ডলে জন্মগ্রহণকারী মানুষ জন্মের পর থেকে স্বীয় পরিবেশে পূর্ব হতে বিদ্যমান জবাবসমূহ গ্রহণ করে এ সব প্রশ্নের জবাব লাভের জন্যে তার মধ্যে সৃষ্ট পিপাসার নিবৃত্তি করার চেষ্টা করে। কিন্তু বিভিন্ন পরিবেশে এ সব প্রশ্নের জবাবে বিভিন্নতা থাকার কারণে একই প্রশ্নের জবাব বিভিন্ন ব্যক্তির নিকট বিভিন্ন হয়ে থাকে। আবার অনেক ক্ষেত্রে একই ব্যক্তি অন্য পরিবেশে প্রদত্ত জবাব জানার পর নিজ পরিবেশে প্রাপ্ত জবাব পরিত্যাগ করে অন্য পরিবেশ থেকে প্রাপ্ত জবাব গ্রহণ করে অথবা উভয় জবাবের মধ্যে তুলনা ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে তৃতীয় কোনো জবাব উদ্ঘাটন করে - যা অবশ্য পরবর্তীকালীন লোকদের জন্য আরেক ধরনের গতানুগতিক জবাব হিসেবে পরিগণিত হয়।
নিঃসন্দেহে একই প্রশ্নের বিভিন্ন জবাবের মধ্যে সবগুলো বা একাধিক জবাব সঠিক হতে পারে না। এমনকি সবগুলো জবাব ভুল হবার সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেয়া যায় না। তাই প্রশ্ন হচ্ছে, সঠিক জবাব লাভের উপায় কী? একটি প্রশ্নের যতোগুলো জবাব দেয়া হয়েছে তার মধ্য থেকে প্রত্যেকটি জবাবই নিজেকে সঠিক বলে দৃঢ়তার সাথে দাবী করে এসেছে। এমতাবস্থায় কী করে বুঝবো যে, কোন্ জবাবটি সঠিক বা আদৌ কোনো সঠিক জবাব পাওয়া গেছে কি না?
অন্যদিকে জীবন ও জগত সম্পর্কে এ সব প্রশ্ন এতোই গুরুত্বপূর্ণ যে, এগুলোকে জবাববিহীনভাবে রেখে দেয়াও সম্ভব নয়। কারণ, এ সব প্রশ্নের জবাবের ওপর মানুষের গোটা জীবনের কর্মনীতি নির্ভর করে। এ সব প্রশ্নের জবাবের বিভিন্নতার কারণে এক ব্যক্তি আকণ্ঠ ভোগ-বিলাসে নিমজ্জিত থাকে, এক ব্যক্তি ব্যক্তিগত স্বার্থে যে কোনো অন্যায়-অপরাধ করতে দ্বিধা করে না, কেউ কেউ তো ‘অন্যায়’, ‘অপরাধ’ ইত্যাদি পরিভাষাকেই অর্থহীন ও হাস্যষ্কর বলে মনে করে, অন্যদিকে এক ব্যক্তি কোনো নীতি-আদর্শের জন্য বা দেশের জন্য বা মানুষের জন্য অথবা হৃদয়বৃত্তিকতা ও ভাবাবেগের জন্য স্বীয় ধনসম্পদ, এমনকি জীবন পর্যন্ত বিলিয়ে দিচ্ছে। আবার দেখা যায়, এক ব্যক্তি সংসার ত্যাগ করে পাহাড়ে-জঙ্গলে চলে যাচ্ছে বা ছন্নছাড়া হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে অথবা সন্ন্যাসব্রত অবলম্বন করছে, এক ব্যক্তি স্রষ্টাকে বা দেবতাকে সন্তুষ্ট করতে নরবলি দিচ্ছে, এক ব্যক্তি আত্মহত্যা করে এ দুনিয়া থেকে বিদায় নিচ্ছে, এক ব্যক্তি সন্তান-সন্ততির মাধ্যমে এবং আরেক ব্যক্তি কীর্তির মাধ্যমে নিজেকে অমর করে রাখার চেষ্টা করছে।
এ ধরনের আরো অনেক উদাহরণ দেয়া যায়। অতএব, এ প্রশ্নগুলো যে খুবই গুরুত্বপূর্ণ তাতে কোনোই সন্দেহ নেই। এমনকি যারা বলে, এ সব প্রশ্নের জবাব খুঁজে লাভ নেই, তার চেয়ে দু’দিনের এ দুনিয়ার জীবনটা ভোগ-আনন্দে কাটিয়ে দাও; সঠিক জবাব খুঁজতে খুঁজতে জীবনটা ব্যয় করে ফেললে পরে সে জবাব কী কাজে লাগবে? - বাহ্যতঃ তারা এ সব প্রশ্নের প্রতি উদাসীনতা ও উপেক্ষা প্রদর্শন করলেও কার্যতঃ তারাও এ সব প্রশ্নের এক ধরনের জবাব নির্ধারণ করে নিয়ে তার ভিত্তিতে আচরণ করছে। অর্থাৎ তারা মুখে স্বীকার করুক বা না-ই করুক, কার্যতঃ এই বস্তু ও জীব জগৎকেই একমাত্র সত্য বলে এবং এ পার্থিব জীবনকেই একমাত্র জীবন বলে গণ্য করছে।
তবে যারা এ সব প্রশ্নের জবাব সন্ধান থেকে বিরত থাকতে বলে তাদের মধ্যে অনেকে তাদের বক্তব্যকে যৌক্তিক ভিত্তির ওপর দাঁড় করিয়ে তার গ্রহণযোগ্যতা সৃষ্টির চেষ্টা করে থাকে। এদের কথা হচ্ছে, জীবন ও জগতের পিছনে কোনো সত্য আছে কিনা এবং থাকলে তা কী - তা আদৌ জানা সম্ভব নয়। অন্য কথায়, ‘জ্ঞান’ অর্জন করা সম্ভব নয়, তা যে কোনো বিষয়ের জ্ঞানই হোক না কেন।
এ ব্যাপারে তাদের যুক্তি অনেক। তাদের দাবী হচ্ছে, মানুষের সামনে নির্ভুল জ্ঞান অর্জন করার কোনো পথ নেই। মানুষের বস্তুগত দেহের অন্তরালে কোনো অবস্তুগত সত্তা আছে কি নেই সে ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া তো দূরের কথা, যে ইন্দ্রিয়নিচয়কে জ্ঞানমাধ্যম হিসেবে সকলেই স্বীকার করে তার ওপরেও নির্ভর করা যায় না। উদাহরণস্বরূপ, চোখ অনেক সময় ছোট জিনিসকে বড় দেখে, আবার বড় জিনিসকে ছোট দেখে। সূর্যটা কতো বড়, কিন্তু চোখ তাকে ছোট দেখে। অন্যমনস্ক অবস্থায় কানের কাছে শব্দ হলেও কান তা শুনতে পায় না। আবার অনেক সময় কোনো শব্দ না হলেও কান কাল্পনিক শব্দ শুনে থাকে। তেমনি মানুষের অন্যান্য ইন্দ্রিয়ও ভুল করে থাকে। তিনটি পাত্রে অল্প, মধ্যম ও বেশী তাপমাত্রার পানি রেখে অল্প ও বেশী তাপমাত্রার পানিতে দুই হাত ডুবিয়ে রেখে পরে উভয় হাত মধ্যম তাপমাত্রার পানিতে ডুবালে এক হাতে গরম ও আরেক হাতে ঠাণ্ডা মনে হবে, যদিও দুই হাতই অভিন্ন পানিতে ডুবানো হয়েছে। অতএব, সঠিক জ্ঞান অর্জন করা সম্ভব নয়।
উপরোক্ত ধারণা পোষণকারীদের সবচেয়ে শক্তিশালী যুক্তি হচ্ছে এই যে, আমরা যখন স্বপ্ন দেখি তখন তাকে বাস্তব বলে মনে করি, স্বপ্ন বলে মনে করি না। এমতাবস্থায় আমরা আমাদের এই জীবনকে যে বাস্তব মনে করছি, এ-ও যে এক বড় ধরনের স্বপ্ন নয় তা কী করে বুঝবো? হয়তো বা এ-ও এক ধরনের স্বপ্ন, মৃত্যুর মাধ্যমে যা ভেঙ্গে যাবে এবং অন্য এক জগতে আমরা জেগে উঠবো। অতএব, এ জীবনে সত্য উদ্ঘাটন তথা সঠিক জ্ঞান লাভ করা সম্ভব নয়। তাই জীবনজিজ্ঞাসা সহ কোনো জিজ্ঞাসারই জবাব সন্ধান করে লাভ নেই।
এদের দাবী দৃশ্যতঃ সঠিক মনে হলেও আসলে তাদের বক্তব্যের মধ্যেই তাদের মূল দাবীর ভ্রান্তির প্রমাণ নিহিত রয়েছে। তাদের মূল দাবী: সত্যকে জানা বা উদ্ঘাটন করা সম্ভব নয়। এখন প্রশ্ন হচ্ছে: তাদের দৃষ্টিতে তাদের এ দাবী সঠিক কিনা? যদি তারা এ দাবীকে সঠিক বলে গণ্য করে তাহলে তাদের এটা মানতেই হবে যে, তারা অন্ততঃ একটি সত্যকে উদ্ঘাটন করেছে, তা হচ্ছে: “সত্যকে উদ্ঘাটন করা যায় না।” কিন্তু একটি সত্যও যদি উদ্ঘাটন করা সম্ভব হয় তাহলে তা থেকেই তাদের দাবী মিথ্যা প্রমাণিত হয়ে যাচ্ছে।
আমাদের এ জবাবকে একটা জটিল কূটতার্কিক জবাব বলে কেউ দাবী করতে পারে। কিন্তু সত্যকে জানা যায় না বা সঠিক জ্ঞান অর্জন করা সম্ভব নয় - এটা প্রমাণের জন্য তারা যে সব উদাহরণ দিয়ে থাকে তা থেকেই প্রমাণিত হয় যে, সকল ব্যাপারে না হলেও অন্ততঃ কতগুলো ব্যাপারে অকাট্য জ্ঞান অর্জন করা সম্ভব। যেমন: তারা তাদের দাবী পেশ করতে গিয়ে কতগুলো বিষয় স্বীকার করে নিয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে: (১) তাদের নিজেদের অস্তিত্ব, যদিও তার স্বরূপ তারা জানে না। (২) তারা ছাড়া অন্য মানুষের বা তাদের কাছে যে বা যা তাদেরই মতো মানুষ বলে প্রতিভাত হচ্ছে তাদের অস্তিত্ব - যাদের সাথে তারা জ্ঞান সংক্রান্ত বিতর্ক করছে, যদিও তাদের অস্তিত্বের স্বরূপ তারা জানে না। (৩) এই বিতর্ককারী পক্ষদ্বয় ছাড়া তৃতীয় একটি অস্তিত্ব আছে যা হচ্ছে বাইরের বস্তু ও জীব জগৎ - যার স্বরূপ তারা জানে না। (৪) তাদের ও তাদের প্রতিপক্ষের বস্তুদেহের মধ্যে একটি বিতর্ককারী শক্তি আছে, যার স্বরূপ তারা জ্ঞাত নয়। (৫) জ্ঞান বলে একটা কিছু আছে যা সকলে অর্জন করতে চায়, কিন্তু অর্জন করা সম্ভব নয় বলে তারা মনে করে। (৬) অর্জন বলে একটা কাজ আছে যা সম্পাদন করা সম্ভব বা অসম্ভব বলে তারা দুই পক্ষ বিতর্ক করছে। (৭) সঠিক জ্ঞানের যেমন অস্তিত্ব রয়েছে, তেমনি ভুল জ্ঞানেরও অস্তিত্ব রয়েছে, যদিও তারা মনে করে যে, সঠিক জ্ঞান অর্জন করা সম্ভব নয় এবং তাদের প্রতিপক্ষ যে জ্ঞান অর্জন করেছে তা তাদের মতে ভুল জ্ঞান, তবে তার অস্তিত্ব রয়েছে; ভুল জ্ঞান অস্তিত্বহীন নয়। (৮) মানুষ স্বপ্ন দেখে যদিও তার স্বরূপ তার জানা নেই। (৯) যে মানুষ জাগ্রত সে বাস্তব জগতে রয়েছে, যদিও এ বাস্তব জগতের স্বরূপ সম্পর্কে নিশ্চিত জ্ঞান অর্জন করা সম্ভব নয় বলে তারা মনে করে এবং মৃত্যুর পরে এর সঠিক রূপ ধরা পড়ার সম্ভাবনা আছে। (১০) মানুষ স্বপ্নের ভিতরে যা দেখে তাকে বাস্তব গণ্য করে, জাগ্রত হবার পর যা বাস্তব নয় বলে মনে হয়। (১১) সে জানে যে, মানুষের ইন্দ্রিয়নিচয় তার তথ্য বা জ্ঞান আহরণের মাধ্যম। (১২) সে এ-ও জানে যে, ইন্দ্রিয়নিচয় অনেক সময় ভুল তথ্য সরবরাহ করে। (১৩) মানুষ অনেক সময় বুঝতে পারে যে, ইন্দ্রিয়নিচয় তাকে ভুল তথ্য সরবরাহ করছে। (১৪) মানুষের ভিতরে এমন একটি ইন্দ্রিয়বহির্ভূত শক্তি রয়েছে যা ইন্দ্রিয়ের ভুল সম্পর্কে নিশ্চিত হতে পারে।
অতএব, দেখা যাচ্ছে, সকল বিষয়ে না হলেও অনেক বিষয়ে মানুষ অকাট্য জ্ঞানের অধিকারী হতে পারে। আরো উদাহরণ দিতে গেলে এ তালিকা অনেক দীর্ঘ হয়ে যাবে। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে এই যে, মানুষের পক্ষে ‘অনেক’ বিষয়ে (সকল বিষয়ে নয়) সঠিক জ্ঞানের অধিকারী হওয়ার সম্ভাবনা থাকার মানে হচ্ছে ‘অনেক’ বিষয়ে ভুল জ্ঞান অর্জিত হওয়ার সম্ভাবনাও রয়েছে। এমতাবস্থায় এমন কোনো প্রক্রিয়া বা পথ থাকা প্রয়োজন যা সকল বিষয়ে, বা অন্ততঃ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহের ক্ষেত্রে মানুষের জন্য সঠিক জ্ঞান প্রাপ্তিকে নিশ্চিত করবে অথবা সঠিক জ্ঞান উদ্ঘাটনের কৌশলকে তার আয়ত্তে এনে দেবে। প্রশ্ন হচ্ছে, এমন কোনো প্রক্রিয়া বা পথ আছে কি? যদি থেকে থাকে, তো কী সে প্রক্রিয়া বা পথ? কীভাবে আমরা জীবনজিজ্ঞাসার সঠিক জবাব পেতে পারি এবং ভুল জবাবগুলোকে ভুল জবাব হিসেবে চিহ্নিত করতে পারি?
এ প্রশ্নের জবাব পেতে হলে আমাদেরকে সবগুলো জ্ঞান-উৎস ও জ্ঞানার্জনের মাধ্যমকে বিশ্লেষণ করতে হবে।
সবগুলো জ্ঞান-উৎস ও জ্ঞানার্জনের মাধ্যমকে বিশ্লেষণ করলে আমরা এগুলোকে মোট চার ভাগে ভাগ করতে পারি।
এ ক্ষেত্রে প্রথমেই বিবেচনায় আসে অভিজ্ঞতা ও পরীক্ষামূলক বিজ্ঞান থেকে লব্ধ জ্ঞান। অভিজ্ঞতা এবং এই অভিজ্ঞতারই উন্নততম সংস্করণ পরীক্ষামূলক বিজ্ঞান বা বস্তুবিজ্ঞান আমাদেরকে জীবনজিজ্ঞাসার জবাব দানে সক্ষম নয়। কারণ, প্রথমতঃ অভিজ্ঞতা এবং পরীক্ষামূলক বিজ্ঞান বা বস্তুবিজ্ঞান ইন্দ্রিয়জ পর্যবেক্ষণের ওপর নির্ভরশীল। আর ইন্দ্রিয়নিচয় সব সময় নির্ভুল তথ্য সরবরাহ করে না। এ কারণে, জীবন ও জগতের অন্তরালে নিহিত রহস্য উদ্ঘাটন করা তো দূরের কথা, ইন্দ্রিয়নিচয় অন্য কোনো জ্ঞান-আহরণ মাধ্যমের সাহায্য ছাড়া শুধু বস্তুজগত সম্পর্কেও সঠিক জ্ঞান সরবরাহের নিশ্চয়তা দিতে পারে না।
দ্বিতীয়তঃ মৌলিক জীবনজিজ্ঞাসাসমূহের বিষয়বস্তু কোনো বস্তুজাগতিক বিষয় নয়। এ কারণে, না তা ইন্দ্রিয়ের দ্বারা পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব, না পরীক্ষাগারে এতদসংক্রান্ত তথ্যাদির সত্যাসত্য পরীক্ষা করা সম্ভব। সৃষ্টিকর্তা আছেন অথবা নেই - এর কোনোটাই ইন্দ্রিয়নিচয় বলতে সক্ষম নয়। তেমনি মানুষের গোটা শরীর পরীক্ষাগারে বিশ্লেষণ করে জবাব পাওয়া যাবে না যে, তার মধ্যে আত্মার অস্তিত্ব আছে অথবা নেই। অতএব, বস্তুবিজ্ঞান আমাদেরকে বস্তুসংক্রান্ত অনেক জ্ঞান (অবশ্য অন্যান্য জ্ঞানমাধ্যমের সহায়তায়) দিতে সক্ষম হলেও জীবনজিজ্ঞাসার জবাবদানে সক্ষম নয়।
দ্বিতীয় একটি জ্ঞানমাধ্যম হচ্ছে পূর্ববর্তীদের রেখে যাওয়া জ্ঞানভাণ্ডার - যাকে এক কথায় علوم نقلی (‘উলূমে নাক্বলী - transferable knowledge - উদ্ধৃতিযোগ্য জ্ঞান) বলে অভিহিত করা যেতে পারে। এর মধ্যে ইতিহাস, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, সাহিত্য, ধর্ম, দর্শন, যুক্তিবিজ্ঞান, ভাষাতত্ত্ব, জ্ঞানতত্ত্ব এবং অন্যদের অভিজ্ঞতা, অনুভূতি ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা ইত্যাদি সকল বিষয়েরই কথিত বা লিখিত বিবরণ ও উপসংহার অন্তর্ভুক্ত।
উদ্ধৃতিযোগ্য জ্ঞানসমূহের মধ্যে বিশেষভাবে দর্শন ও ধর্মসমূহ জীবনজিজ্ঞাসার জবাব দেয়ার চেষ্টা করেছে। কিন্তু এ সব জ্ঞানসূত্রের মাধ্যমে মৌলিক জীবনজিজ্ঞাসাসমূহের জবাব উদ্ঘাটনের পথে কতগুলো কঠিন সমস্যা দেখা দেয়। এ ক্ষেত্রে বড় সমস্যা হচ্ছে, বিভিন্ন ধর্ম ও দর্শন এ সব প্রশ্নের বিভিন্ন জবাব দিয়েছে। স্রষ্টার সংজ্ঞা, সংখ্যা, গুণাবলী, স্বরূপ, আত্মার সংজ্ঞা ও স্বরূপ, স্রষ্টা ও মানুষের মধ্যকার সম্পর্ক ইত্যাদি প্রশ্নে বিভিন্ন ধর্ম ও দর্শন বিভিন্ন জবাব দিয়েছে। এ সব জবাবের মধ্যে কতগুলো ক্ষেত্রে কোনো কোনো ধর্ম ও দর্শন অপর কোনো কোনো ধর্ম ও দর্শনের সাথে অভিন্ন জবাব দিলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাদের জবাবের মধ্যে পারস্পরিক বিভিন্নতাই শুধু নয়, বরং বৈপরীত্যও দেখা যায়। শুধু তা-ই নয়, এমনকি অনেক ক্ষত্রে একই ধর্মের বিভিন্ন সূত্র একই প্রশ্নের বিভিন্ন জবাব দিয়েছে। তাছাড়া বিশেষ করে ধর্মীয় জবাবের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট জবাব যে সব ব্যক্তির নিকট থেকে প্রাপ্ত বলে দাবী করা হয়েছে তাঁদের ঐতিহাসিকতা, গ্রহণযোগ্যতা এবং তাঁদের দেয়া জবাব নির্ভুলভাবে বর্তমান প্রজন্ম পর্যন্ত পৌঁছার বিষয়টি সুনিশ্চিত নয়। তারপর কথা হচ্ছে, একই প্রশ্নের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধর্মীয় সূত্র যে পরস্পর বিরোধী বিভিন্ন জবাব দিয়েছে তা গ্রহণ-বর্জনের মানদণ্ড কী?
অতএব, দেখা যাচ্ছে, ধর্মীয় বা দার্শনিক জ্ঞানসূত্রসমূহ জীবনজিজ্ঞাসাসমূহের যে সব জবাব দিয়েছে তা গ্রহণ-বর্জনের জন্য অন্য কোনো জ্ঞানমাধ্যমের দ্বারা পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও যাচাই-বাছাইয়ের প্রয়োজন রয়েছে।
জ্ঞানার্জনের, বিশেষতঃ জীবনজিজ্ঞাসার জবাব প্রাপ্তির তৃতীয় মাধ্যমটি হচ্ছে জ্ঞানের স্বতঃপ্রকাশিত হবার প্রক্রিয়া। ‘ইরফানী (আধ্যাত্মিক) ধারাও এ পর্যায়ের। কোনোরূপ পার্থিব কারণ ছাড়াই যেভাবে হঠাৎ করে কারো মস্তিষ্কে একটি বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার খেলে যায়, ঠিক সেভাবেই কারো নির্মল অন্তঃকরণে জীবনজিজ্ঞাসাসমূহের এক ধরনের জবাব ধরা পড়ে যেতে পারে। কিন্তু এর দ্বারা আমাদের সমস্যার সমাধান হতে পারে না। কারণ, এটা কোনো সর্বজনীন জ্ঞানমাধ্যম নয় এবং এর যথার্থতা সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়ার কোনো সর্বজনীন পার্থিব পন্থা জানা নেই। এ ধরনের অনর্জিত ও ইন্দ্রিয়াতীত মাধ্যম লব্ধ জ্ঞান বস্তুবিজ্ঞান বিষয়ক হলে তার যথার্থতা অভিজ্ঞতা দ্বারা বা পরীক্ষাগারে পরীক্ষা করে দেখা যেতে পারে, কিন্তু তা জীবনজিজ্ঞাসার জবাব বিষয়ক হলে তার যথার্থতা অভিজ্ঞতা দ্বারা বা পরীক্ষাগারে পরীক্ষা করে দেখা সম্ভব নয়। অন্যদিকে যে কেউ চাইলে এবং চেষ্টা করলেই তার অন্তরে জীবন ও জগতের মহাসত্যসমূহ সংক্রান্ত প্রশ্নের জবাব ধরা দেবেই তার কোনো নিশ্চয়তা নেই। তেমনি এরূপ জ্ঞানের প্রকৃত উৎস কী এবং সে উৎস সঠিক কিনা - এ প্রশ্ন থেকে যায়। কারণ, এটা ব্যক্তির সচেতন চিন্তাচেতনার অবচেতন প্রভাবজাতও হতে পারে। অন্যদিকে যার নিকট এ জ্ঞান উদ্ভাসিত হয়েছে তিনি এ ব্যাপারে যে পর্যায়ের নিশ্চয়তার অধিকারী তাঁর নিকট থেকে যারা শুনবে তাদের পক্ষে তদ্রূপ নিশ্চয়তার অধিকারী হওয়া সম্ভব নয়। ফলে তাদের জ্ঞান অকাট্য পর্যায়ের হবে না। তাছাড়া এরূপ ব্যক্তির দাবীর সত্যাসত্য সম্পর্কে নিশ্চিত হবার প্রয়োজন রয়েছে। আর তা হতে হলে অন্য কোনো জ্ঞানমাধ্যমের সাহায্য নিতে হবে।
বস্তুতঃ কারো কাছে যে জ্ঞান স্বতঃপ্রকাশিত হয় অন্যদের জন্য তাঁর সে জ্ঞান এক ধরনের ধর্মীয় জ্ঞান বৈ নয়, লোকেরা যা তাদের দৃষ্টিতে নির্ভরযোগ্য বলে পরিগণিত লোকদের নিকট থেকে গ্রহণ করে থাকে। এখানে আরো স্মরণীয় যে, এভাবে অন্তরে জীবন ও জগতের মহাসত্য ধরা পড়ার বিষয়টি (ইলহাম্ বা কাশফ্) সাধারণতঃ সুদীর্ঘ কাল ব্যাপী ধর্মীয় জীবন যাপন ও বিশেষ ‘ইরফানী (আধ্যাত্মিক) প্রক্রিয়ায় সাধনার ফলশ্রুতি হয়ে থাকে। সে হিসেবে তা ধর্মীয় জ্ঞানেরই পর্যায়ভুক্ত বা তার একটা প্রধান শাখা মাত্র, অন্যদের জন্য যার গ্রহণযোগ্যতা পরীক্ষা-নিরীক্ষার মুখাপেক্ষী।
চতুর্থ জ্ঞানমাধ্যমটি হচ্ছে বিচারবুদ্ধি (‘আক্বল্)। আসলে বিচারবুদ্ধি হচ্ছে মানুষের ব্যক্তিসত্তায় নিহিত এমন একটি শক্তি যা একই সাথে জ্ঞানের উৎস এবং অন্যান্য জ্ঞানসূত্র থেকে প্রাপ্ত তথ্যাদির সত্যাসত্য পরীক্ষাকারী ও সে সবের মধ্যে সমন্বয়সাধনকারী।
বস্তুতঃ ‘জ্ঞান’ বিষয়টি পুরোপুরিভাবেই বিচারবুদ্ধির সাথে সম্পৃক্ত। ইন্দ্রিয়নিচয় মানুষকে যে সব তথ্য সরবরাহ করে বিচারবুদ্ধি তা বিশ্লেষণ করে সত্য, মিথ্যা, ঠিক, ভুল, মিশ্রিত, বিভ্রান্তিকর, মায়া ইত্যাদি বিভিন্ন বিশেষণে বিশেষিত করে। শুধু বস্তুবিজ্ঞানই নয়, বরং ব্যক্তিগত কাশফ্ বা ইলহাম্ বা ওয়াহী বাদে পুরো ধর্মীয় জ্ঞানই ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে (শ্রবণ ও পঠনের মাধ্যমে) সংগৃহীত হয়ে থাকে। কিন্তু তার গ্রহণ-বর্জন ঘটে বিচারবুদ্ধির দ্বারা।
বিশেষ করে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় হচ্ছে এই যে, ইন্দ্রিয়নিচয়ের কাজ একমুখী অর্থাৎ শুধু তথ্য সরবরাহ করা। তার সত্যাসত্য যাচাই করা বা অন্য তথ্যের সাথে তার তুলনা করে তৃতীয় কোনো সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া ইন্দ্রিয়নিচয়ের কাজ নয়। বরং বিচারবুদ্ধিই এ সব তথ্য বিশ্লেষণ করে উপসংহারে উপনীত হয়।
বিচারবুদ্ধি যে ইন্দ্রিনিচয়ের দেয়া তথ্যাদি বিশ্লেষণ করে শুধু তা-ই নয়, বরং স্বয়ং জ্ঞানের উৎসও বটে। কারণ, ইন্দ্রিয়নিচয়ের সাহায্য ছাড়াই বিচারবুদ্ধি স্বীয় অস্তিত্ব অনুভব করে এবং ইন্দ্রিয়ের ওপরে স্বীয় শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে নিশ্চিত হয়। বিচারবুদ্ধি বস্তুসম্পর্কহীন-ভাবে বহু অকাট্য জ্ঞান অর্জন করে। যেমন, বিচারবুদ্ধি বলে: অভিন্ন স্থান-কালে কোনো জিনিস আছে এবং নেই - দুইই সত্য হতে পারে না, যে কোনো সমগ্রের অংশ ঐ সমগ্র হতে ক্ষুদ্রতর হতে বাধ্য, কারণ ছাড়া কোনো কার্য ঘটে না, দুই যোগ দুই (দুই বস্তু যোগ দুই বস্তু নয়) সমান চার, জ্যামিতিক বিন্দু ও রেখা কোনো জায়গা দখল করে না, কোনো ফলশ্রুতি যে কারণ থেকে উদ্ভূত সে কারণটি ঐ ফলশ্রুতি থেকে উদ্ভূত হতে পারে না, পরিবর্তনশীল বস্তুজগতের আদি উৎস অবশ্যই পরিবর্তনশীলতা থেকে মুক্ত হতে হবে; যার অস্তিত্ব নেই বস্তুর ওপরে তা প্রতিক্রিয়া করতে পারে না, যেহেতু মানুষ অবস্তুগত সত্তা নিয়ে বিতর্ক করে, অতএব, তা আছে, নইলে তা আছে বলে তার মনে হতো না অর্থাৎ আছে বলেই তা মানুষের মনে প্রতিক্রিয়া করেছে, ইত্যাদি।
মোদ্দা কথা, বিচারবুদ্ধি স্বয়ং জ্ঞানের উৎস এবং অন্যান্য জ্ঞানসূত্রের সত্যাসত্য বিচারকারী। অবশ্য বিভিন্ন কারণে বিচারবুদ্ধি ভুল করতে পারে, তবে বিচারবুদ্ধির বিশ্লেষণেই সে ভুল ধরা পড়ে ও সংশোধিত হয়। এমতাবস্থায় জীবন ও জগতের মহাসত্য সংক্রান্ত জিজ্ঞাসাসমূহের সঠিক জবাব পেতে হলে স্বয়ং বিচারবুদ্ধির কাছ থেকে জবাব শুনতে হবে এবং অন্যান্য সূত্রে প্রাপ্ত জবাবসমূহকেও বিচার-বিশ্লেষণের জন্য বিচারবুদ্ধির সামনে পেশ করতে হবে।
বিচারবুদ্ধির জবাব
মানুষ, অন্যান্য প্রাণীপ্রজাতি, উদ্ভিদরাজি ও মহাকাশের জ্যোতিষ্কনিচয় সহ এই যে সুবিশাল বিশ্বলোক স্বীয় অস্তিত্ব নিয়ে বিরাজ করছে এর পিছনে কোনো অস্তিত্বদাতা আছেন কি? এ হচ্ছে এমন একটি প্রশ্ন যা এড়িয়ে যাওয়া বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন কোন মানুষের পক্ষেই সম্ভব নয়। আর এর জবাব হবে হয় ‘হ্যা’ অথবা ‘না’; এর বাইরে তৃতীয় কোন জবাব হতে পারে না।
উপরোক্ত প্রশ্নের জবাবে কেউ হয়তো বলবে: “আমি জানি না।” কিন্তু এ প্রশ্নটি মানুষের জন্য এতোই গুরুত্বপূর্ণ যে, এর জবাবের ওপর তার গোটা জীবনের কর্মনীতি ও কর্মধারা নির্ভর করছে। অতএব, এর জবাবে “জানি না” বলে পাশ কাটিয়ে যাওয়ার কোনোই উপায় নেই। বরং অন্য যে কোনো কাজের আগে, এমনকি বেঁচে থাকার জন্যে অপরিহার্য দৈনন্দিন মামুলি কাযকর্মেরও আগে, এ প্রশ্নের সঠিক জবাব সন্ধান ও উদ্ঘাটন করা অপরিহার্য।
অবশ্য যারা মুখে “জানি না” বলে পাশ কাটিয়ে যাবার চেষ্টা করে কর্মনীতি ও কর্মধারার দিক থেকে তারা “না” জবাব-দানকারীদেরই দলভুক্ত। কারণ, এ প্রশ্নের “হ্যা” জবাব দিলে এরপর আরো অনেক প্রশ্নের উদয় হয় এবং সেগুলোরও সঠিক জবাব সন্ধান ও উদ্ঘাটন করা অপরিহার্য হয়ে পড়ে। তাছাড়া “হ্যা” জবাবদানের সাথে সাথেই বিশ্বলোকের অস্তিত্বদাতার সাথে তার (“হ্যা” জবাবদানকারীর) সম্পর্ক নির্ণয় করা এবং তার ভিত্তিতে বহু দায়িত্ব পালন অপরিহার্য হয়ে পড়ে। অন্যদিকে “না” জবাব দেয়া হলে এতদসংক্রান্ত প্রশ্নের এখানেই সমাপ্তি; অতঃপর আর কোনো দায়িত্ব থাকে না। কারণ, স্রষ্টা না থাকলে স্রষ্টার প্রতি এবং স্রষ্টার কাছে জবাবদিহি করার ভয়ে সৃষ্টির প্রতি দায়িত্ব পালনের প্রশ্নই ওঠে না। তেমনি যারা ‘জানি না’ বলে আর জানার চেষ্টাও করে না, তাদের জন্যও নতুন কোনো প্রশ্ন থাকে না। ফলতঃ এই দুই দল লোক চিন্তার দিক থেকে পরস্পর কিছুটা স্বতন্ত্র হলেও বাস্তব আচরণ ও কর্মনীতি-কর্মধারার দিক থেকে পরস্পর অভিন্ন।
ঠিক হোক বা ভুল হোক, উক্ত প্রশ্নের যদি একটিমাত্র জবাব পাওয়া যেতো; হয় শুধু ‘হ্যা’ অথবা শুধু ‘না’ জবাব পাওয়া যেতো, তাহলেও অন্ততঃ মানুষের পক্ষে নিশ্চিন্ত থাকার একটা উপায় হতো। কিন্তু যেহেতু এ প্রশ্নের দু’টি জবাব দেয়া হয়েছে এবং দু’টি জবাব পরস্পরের বিপরীত - ‘হ্যা’ এবং ‘না’, সেহেতু এ বিতর্কের ফয়সালা অপরিহার্য। কিন্তু কে করবে এর ফয়সালা? এজন্য এমন একজন ফয়সালাকারীর দ্বারস্থ হতে হবে যাকে মেনে নেয়া উভয় পক্ষের জন্যই সমানভাবে সম্ভব। এমন একমাত্র ফয়সালাকারী হচ্ছে বিচারবুদ্ধি (عقل)।
জীবনজিজ্ঞাসার জবাবদানের জন্য যতোগুলো জ্ঞানসূত্র এগিয়ে এসেছে তার মধ্যে একমাত্র বিচারবুদ্ধি ছাড়া আর কোনোটিরই সর্বজনীন গ্রহণযোগ্যতা নেই। এর মানে অবশ্য এ নয় যে, বিচারবুদ্ধির বাইরে সত্য উদ্ঘাটনের জন্য আর কোনো মাধ্যম নেই বা থাকতে পারে না; অবশ্যই থাকতে পারে বা আছে। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে, সে সব জ্ঞানসূত্র বা মাধ্যমের সর্বজনীন গ্রহণযোগ্যতা নেই; সে সবের সর্বজনীন গ্রহণযোগ্যতা থাকলে অন্ততঃ জীবন ও জগৎ সংক্রান্ত মৌলিক প্রশ্নসমূহের জবাবের ক্ষেত্রে মতপার্থক্যের সৃষ্টি হতো না। তাই জীবনজিজ্ঞাসাসমূহের ক্ষেত্রে বিভিন্ন জ্ঞানসূত্র বা মাধ্যম কর্তৃক প্রদত্ত সকল জবাবকে পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্যে বিচারবুদ্ধির আদালতে পেশ করা ছাড়া গত্যন্তর নেই।
অবশ্য এমন অনেক লোকও রয়েছেন যারা বিচারবুদ্ধির যোগ্যতা ও এর রায়ের গ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কে প্রশ্ন তোলেন। তাঁরা বিচারবুদ্ধির ভুল, দ্বন্দ্ব ও স্ব-বিরোধিতা প্রদর্শনের চেষ্টা করেন।
নিঃসন্দেহে বিচারবুদ্ধিও ভুলের উর্ধে নয়। কিন্তু মজার ব্যাপার হচ্ছে, যারা বিচারবুদ্ধিকে সালিস মানার বিরোধিতা করছেন তাঁরা কিন্তু বিচারবুদ্ধির অশ্রয় নিয়েই এ কাজ করছেন। কারণ, তাঁরা এ ক্ষেত্রে যুক্তিতর্ক ও বিচারবিশ্লেষণের আশ্রয় নিচ্ছেন। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, বিচারবুদ্ধি ভুল করলে তা-ও বিচারবুদ্ধির কাছেই ধরা পড়ে। ‘ক’-এর বিচারবুদ্ধি সঠিক মনে করে যে রায় দিয়েছে ‘খ’-এর বিচারবুদ্ধি বিচার-বিশ্লেষণ করে তার ভুল ধরিয়ে দিচ্ছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ভুলটি ধরা পড়ে যাচ্ছে এবং তা বিচারবুদ্ধির কাছেই ধরা পড়ে যাচ্ছে। এখানেই অন্যান্য জ্ঞানসূত্রের তুলনায় বিচারবুদ্ধির শ্রেষ্ঠত্ব। কারণ, ঐসব জ্ঞানসূত্র গ্রহণকারীরা বিচারবুদ্ধির আশ্রয় নিয়েই তাঁদের নিজেদের সমর্থিত জ্ঞানসূত্রসমূহের গ্রহণযোগ্যতা ও অন্যদের সমর্থিত জ্ঞানসূত্রসমূহের অগ্রহণযোগ্যতা প্রমাণ করার চেষ্টা করেন। আবার তাঁদের প্রতিপক্ষও তাঁদের সমর্থিত জ্ঞানসূত্রসমূহ প্রত্যাখ্যান ও নিজেদের সমর্থিত জ্ঞানসূত্রসমূহের গ্রহণযোগ্যতা বিচারবুদ্ধির মানদণ্ডের সাহায্যেই প্রমাণের চেষ্টা করেন। এভাবে তাঁরা সকলেই নিজেদের অজ্ঞাতসারেই স্বীয় সমর্থিত জ্ঞানসূত্রসমূহের গ্রহণযোগ্যতা বিচারের জন্য মানদণ্ড বা বিচারক হিসেবে বিচারবুদ্ধিকে ‘কার্যতঃ’ মেনে নেন। অন্যদিকে বিচারবুদ্ধি যদি কখনো ভুল করে তখন সে অন্য কারো দ্বারস্থ হয় না, বরং নিজেই নিজের ভুল চিহ্নিত করে। যদিও হতে পারে যে, একজনের বিচারবুদ্ধির ভুল আরেক জনের বিচারবুদ্ধির কাছে ধরা পড়ছে, কিন্তু যখন তা অকাট্যভাবে ভুল বলে প্রমাণিত হচ্ছে তখন প্রথমোক্ত ব্যক্তির বিচারবুদ্ধিও তা গ্রহণ করে নেয়।
যা-ই হোক, অন্যান্য জ্ঞানসূত্র জীবনজিজ্ঞাসার যে জবাব দিয়েছে তা যেহেতু অভিন্ন নয় এবং তার কোনোটাই সর্বজনীনভাবে গ্রহণযোগ্য প্রমাণিত হয় নি সেহেতু বাধ্য হয়ে আমাদেরকে বিচারবুদ্ধির নিকট থেকেই ফয়সালা নিতে হবে।
এখানে প্রথমেই একটি কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া প্রয়োজন, তা হচ্ছে, মানবসভ্যতার অগ্রগতির সাথে সাথে জ্ঞান-বিজ্ঞানের অসংখ্য শাখা-প্রশাখার বিকাশ ও বিস্তার ঘটেছে। জ্ঞান-বিজ্ঞানের এ সব শাখা-প্রশাখা প্রতিনিয়তই আমাদেরকে অসংখ্য বিষয়ে সঠিক ও ভুল উভয় ধরনের ধারণা দিচ্ছে। কিন্তু ভুল ধারণাগুলোকেও অনেকেই সঠিক বলে ধরে নিচ্ছে। তেমনি সামাজিক, পারিবারিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক ও প্রতিষ্ঠানিক শিক্ষা আমাদেরকে একইভাবে অসংখ্য সঠিক ও ভুলের মিশ্রণ গলাধঃকরণ করাচ্ছে। আর এ মিশ্রণের দ্বারা আমাদের বিচারবুদ্ধিও অনেকখানি প্রভাবিত হয়ে পড়ছে। অবশ্য বিচারবুদ্ধির বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে, তার ভুলকে ধরিয়ে দেয়া হলে সে বুঝতে পারে যে, এটা ভুল (যদিও কোনো বিশেষ স্বার্থের কারণে ব্যক্তি মুখে তা স্বীকার না-ও করতে পারে, কিন্তু অন্তরে ‘ঠিক’কে ‘ঠিক’ বলে ও ‘ভুল’কে ‘ভুল’ বলে জানবেই)। তবে যে নির্মল ও সুস্থ বিচারবুদ্ধি কোনোরূপ জটিল ভ্রান্ত জ্ঞানের পর্দা দ্বারা আবৃত হয় নি সে যেরূপ সহজেই ‘সঠিক’ ও ‘ভুল’ নির্ণয় করতে পারে ভ্রান্ত জ্ঞানের পর্দায় আবৃত বিচারবুদ্ধি ততো সহজে তা পারে না। বরং অসংখ্য নতুন নতুন সংশয় ও প্রশ্ন এসে তাকে সত্য থেকে দূরে সরিয়ে রাখে। এ কারণেই এ ধরনের বিচারবুদ্ধির সামনে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে সত্যকে উপস্থাপন করা অপরিহার্য। অর্থাৎ শুধু মূল প্রশ্নের সঠিক জবাব দেয়াই যথেষ্ট নয়, বরং সংশয়ের পর্দা ছিন্ন করাও অপরিহার্য। অন্য কথায় বলা চলে, বিচারবুদ্ধিকে প্রতিটি ব্যক্তির অবস্থা বিবেচনা করে তার সামনে জীবনজিজ্ঞাসার জবাব পেশ করতে হবে। অর্থাৎ প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার জন্যে সহজবোধগম্য করে জবাব দিতে হবে।
এবার আমরা বিচারবুদ্ধির আলোকে জীবনজিজ্ঞাসার জবাব সন্ধান করব।
জীবনজিজ্ঞাসার জবাব দিতে গিয়ে বিচারবুদ্ধি প্রথমেই আমাদেরকে একটি কর্মনীতি অনুসরণের জন্যে নির্দেশ প্রদান করে, তা হচ্ছে সতর্কতার কর্মনীতি। আস্তিক-নাস্তিক নির্বিশেষে প্রতিটি মানুষই সতর্কতার কর্মনীতিকে গ্রহণযোগ্য মনে করে। অর্থাৎ সকলেই সংশয়ের ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করে। যেমন: কেউ যদি বলে যে, ‘এ গ্লাসের পানিতে বিষ মেশানো আছে’, তখন এ কথার সত্যাসত্য সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়া সম্ভব না হলেও পিপাসার্ত ব্যক্তি সতর্কতার কারণে ঐ পানি পান করা থেকে বিরত থাকে। তেমনি পরিচয়পত্রবিহীন কোনো ব্যক্তি যদি প্রথম বারের মত অন্য কোনো দেশে যাবার জন্যে প্রস্তুতি নেয় এবং তখন যদি তাকে কেউ বলে যে, ‘পরিচয়পত্র ছাড়া কেউ ঐ দেশে প্রবেশ করলে তাকে গ্রেফতার ও কারারুদ্ধ করা হয়’, সে ক্ষেত্রে ঐ কথার সত্যাসত্য যাচাই করা সম্ভব না হলেও ঐ ব্যক্তি সতর্কতার কারণে পরিচয়পত্র ছাড়া ঐ দেশে গমন করা থেকে বিরত থাকে এবং সেখানে গমনের জন্যে পরিচয়পত্র সংগ্রহ করে। ইতিবাচক তথ্যের ক্ষেত্রেও তা-ই। মরুভূমিতে পানিবিহীন কোনো ব্যক্তিকে যদি কেউ বলে যে, অমুক দিকে এতোদূর গেলে পানি পাওয়া যাবে সে ক্ষেত্রে এ তথ্যের সত্যাসত্য যাচাই করা সম্ভব না হলেও সে ঐদিকে ছুটে যায়। তেমনি ক্ষুধার্ত ভিক্ষুককে যদি বলা হয় যে, আজ অমুক সময় অমুক ঠিকানায় কাঙ্গালী ভোজ হবে তাহলে এ তথ্যের সত্যাসত্য যাচাই করা সম্ভব না হলেও ক্ষুধার্ত ভিক্ষুক খাদ্যের আশায় সেখানে চলে যায়। আমাদের জীবন থেকে এ ধরনের অসংখ্য দৃষ্টান্ত মিলবে।
জীবনজিজ্ঞাসার ক্ষেত্রেও বিচারবুদ্ধি আমাদেরকে প্রথমতঃ সতর্কতার কর্মনীতি অনুসরণের নির্দেশ দেয়, তা হচ্ছে, বিচারবুদ্ধি বলে: এ জীবন ও জগতের পিছনে যদি কোনো অস্তিত্বদাতা শক্তি থাকেন তো অবশ্যই তাঁর নিকট নিজেকে দায়িত্বশীল গণ্য করে জীবনপথে পথ চলা ব্যক্তিদের জন্য অপরিহার্য, অন্যথায় ব্যক্তির জন্য বিপর্যয় অনিবার্য। এখন পরিস্থিতি যদি এরূপ হয় যে, আসলেই এরূপ কোনো সত্তার অস্তিত্ব নেই, সে ক্ষেত্রে যে ব্যক্তি অযথাই এরূপ সত্তার অস্তিত্ব আছে মনে করে দায়িত্বশীল জীবনযাপন ও আচরণ করলো এবং যে ব্যক্তি এরূপ সত্তার অস্তিত্ব নেই মনে করে দায়িত্বহীন জীবনযাপন ও আচরণ করলো এতদুভয়ের শেষ পরিণতিতে কোনোই পার্থক্য ঘটবে না; মৃত্যু উভয়ের অস্তিত্বের ওপর অনস্তিত্বের পর্দা টেনে দেবে এবং ঊভয়ের জন্যই লাভ-ক্ষতি অর্থহীন হয়ে যাবে। অর্থাৎ যে ব্যক্তি সৃষ্টিকর্তা না থাকা সত্ত্বেও আছে মনে করে দায়িত্বশীল জীবনযাপন ও আচরণ করেছে তা তাকে ক্ষতিগ্রস্ত করে নি; সে ভুলবশতঃ পার্থিব জীবনের অনেক ভোগ-আনন্দ থেকে নিজেকে বঞ্চিত করলেও তাতে তার আদৌ কোনো ক্ষতি হয় নি। কারণ, অনন্ত কালের তুলনায় এ পার্থিব জীবনকাল মহাসমুদ্রের তুলনায় বারিবিন্দুর সমতুল্যও নয়, বরং তার চেয়েও অকিঞ্চিৎকর। এহেন মূল্যহীন জীবনের ভোগ-আনন্দেরও আদৌ কোনো মূল্য নেই, বিশেষ করে যখন এ ভোগ-আনন্দের জন্যে অনেক ক্ষেত্রেই দুঃখ-কষ্ট ও ব্যথাবেদনার ঝুঁকি নিতে হয়। তাই মৃত্যুতেই যে জীবনের চিরপরিসমাপ্তি, প্রাকৃতিক মৃত্যুর জন্যে অপেক্ষা না করে সে জীবনকে বরং এখনি শেষ করে দেয়াই উত্তম।
কিন্তু প্রকৃতই যদি এ জীবন ও জগতের পিছনে কোনো স্রষ্টাসত্তা থেকে থাকেন তাহলে মৃত্যুতে এ জীবনের চিরপরিসমাপ্তি ঘটার কোনোই নিশ্চয়তা নেই। কারণ, এরূপ সত্তা - যিনি শূন্য থেকে সবকিছু সৃষ্টি করতে পেরেছেন, তাঁর পক্ষে ব্যক্তিদের জন্যে পার্থিব মৃত্যুর পরে নতুন ধরনের কোনো জীবনের ব্যবস্থা রাখা অসম্ভব কিছু নয়। সে ক্ষেত্রে যে ব্যক্তি দায়িত্বশীল জীবনযাপন ও আচরণ করেছে সে ব্যক্তি তার নতুন ধরনের জীবনে কোনোরূপ বিপদের সম্মুখীন হবে না। অন্যদিকে যে ব্যক্তি সৃষ্টিকর্তা নেই মনে করে দায়িত্বহীন জীবনযাপন ও আচরণ করেছে তার জন্যে ভয়াবহ বিপর্যয়কর অনন্ত জীবন অপেক্ষা করছে। এমতাবস্থায় বিচারবুদ্ধির পথনির্দেশ হচ্ছে, অনিশ্চয়তা ও সংশয়ের ক্ষেত্রে সতর্কতার কর্মনীতি অনুসরণ করতে হবে; সম্ভাব্য ভয়াবহ বিপর্যয় এড়ানোর লক্ষ্যে দায়িত্বশীল জীবনযাপন ও আচরণ করতে হবে।
তবে বিচারবুদ্ধি আমাদেরকে শুধু সতর্কতার কর্মনীতি অনুসরণেরই নির্দেশ দেয় না, বরং জীবনজিজ্ঞাসার অকাট্য জবাবও প্রদান করে। বিচারবুদ্ধি জীবনজিজ্ঞাসার জবাব কয়েকভাবে প্রদান করে থাকে।
বিচারবুদ্ধি জীবনজিজ্ঞাসার যে সব জবাব প্রদান করে তার মধ্যে এক ধরনের জবাব অত্যন্ত সহজ-সরল যা জ্ঞানী-মূর্খ যে কারো জন্যে সহজবোধগম্য। তা হচ্ছে: আমি ছিলাম না, কিন্তু আছি, অতএব, নিঃসন্দেহে আমার কোনো স্রষ্টা আছেন।
যে কোনো নির্মল-নিষ্কলুষ বিচারবুদ্ধিই এ জবাব গ্রহণ করতে বাধ্য। কিন্তু যে ব্যক্তির বিচারবুদ্ধির ওপর ভ্রান্ত জ্ঞানের আবরণ পড়েছে সে এতে তৃপ্ত হয় না। তাই সে এ ব্যাপারে নানা ধরনের পার্শ্ব-প্রশ্ন তুলতে পারে। যে সব তথ্যের অকাট্যতা নিশ্চিত নয় তাকে অকাট্য ধরে নিয়ে তার ভিত্তিতেও সে প্রশ্ন উত্থাপন করে থাকে। উদাহরণস্বরূপ, বস্তুবাদীদের দাবী হচ্ছে, গোটা বিশ্বলোকে শুধু বস্তুই আছে; আর কিছুই নেই। তাদের মতে, বস্তুজগতের সূচনার পূর্বে ‘স্রেফ বস্তু’ (absolute matter) বা ‘নির্গুণ বস্তু’ অর্থাৎ কোনো বিশেষ আকার-আকৃতি, গঠন-মিশ্রণ বা যৌগিকতা বিহীন ও গুণাবলী বা প্রাকৃতিক বস্তুধর্ম বিহীন বস্তু বিরাজমান ছিল, পরে এক সময় ‘র্ঘটনাক্রমে’ (accidentally) তাতে আলোড়ন বা বিস্ফোরণের ফলে গতিসঞ্চারের মাধ্যমে সৃষ্টির সূচনা হয় এবং বস্তুর ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়ায় ক্রমান্বয়ে বিভিন্ন ধরনের বস্তুনিচয়, বিশ্বজগৎ ও প্রজাতিসমূহ অস্তিত্বলাভ করে। অতএব, স্রষ্টা বলতে কিছু নেই।
কিন্তু এ তথাকথিত বৈজ্ঞানিক সৃষ্টিতত্ত্বের প্রবক্তারা অনেকগুলো মৌলিক প্রশ্নের জবাব দিতে সক্ষম হন নি। তা হচ্ছে:
এক: কথিত এ আদি নির্গুণ বস্তু কোত্থেকে এলো? কে তার অস্তিত্বদাতা? কারণ, বস্তু বা কথিত আদি বস্তু তো এমন কোনো অস্তিত্ব হতে পারে না যা নিজে নিজে সতত বিদ্যমান। বলা হয়: “ছিলো।” এ এক অবৈজ্ঞানিক জবাব। কারণ, বস্তুজগৎ ‘কারণ ও ফলশ্রুতি’ (cause and effect - علة و معلول) বিধির অধীন। অতএব, এটা হতে পারে না যে, ‘অনাদি কাল’ থেকে ‘আদি বস্তু’র অস্তিত্ব ছিলো, তারপর তা কারণ ও ফলশ্রুতি বিধির আওতাভুক্ত হলো।
দুই: বস্তুর ধর্ম অনুযায়ী তার ওপর কোনো শক্তি ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া না করলে তা অনন্ত কাল একই অবস্থায় থাকবে। অর্থাৎ যা স্থির তা স্থিরই থাকবে এবং যা গতিশীল তা গতিশীলই থাকবে। এমতাবস্থায় কথিত ‘আদি বস্তু’তে - যা প্রথমে স্থির বা গতিহীন ছিলো বলে এ মতের প্রবক্তাগণও স্বীকার করেন - গতিসঞ্চার (তা আলোড়ন বা বিস্ফোরণ যা-ই হোক না কেন) করলো কে? কোনো কারণ ছাড়া নিজে নিজে তো আর তাতে গতিসঞ্চার হওয়া সম্ভব ছিলো না।
তিন: কথিত আদি বস্তুতে গতি সঞ্চারিত হবার পর বিভিন্ন ধরনের মৌলিক পদার্থ ও যৌগিক বস্তুনিচয় এবং প্রাণশীল প্রজাতিসমূহ সৃষ্টি হলো যে প্রাকৃতিক নিয়মে বা যে কারণ ও ফলশ্রুতি বিধির অধীনে সে নিয়ম বা বিধি কোত্থেকে এলো? কারণ, নির্জ্ঞান বস্তু নিজের জন্য প্রাকৃতিক বিধি-বিধান তৈরী করতে, বিভিন্ন ধরনের অপরিবর্তনীয় বস্তুগুণ সৃষ্টি করতে, বিশ্বজগতে নিখুঁত শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করতে এবং প্রাণের উদ্ভব ঘটাতে সক্ষম নয়। স্বয়ং বস্তু যে প্রাকৃতিক নিয়ম বা কার্যকারণ বিধির অধীন সে নিজেই তো আর তা সৃষ্টি করতে পারে নি।
বিজ্ঞানের নামে কেউ কেউ দাবী করেছেন যে, দুর্ঘটনাক্রমে (accidentally) এক বিস্ফোরণের ফলে আদি বস্তুতে গতিসঞ্চার হয়। কিন্তু ‘দুর্ঘটনা’ একটি সাহিত্যিক, মানবিক ও লৌকিক পরিভাষা। খাঁটি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে ‘দুর্ঘটনা’ তথা কারণবিহীন বা নিয়মবহির্ভূতভাবে কোনো কিছু সংঘটিত হওয়া অসম্ভব। যদিও প্রচলিত কথায় যে ঘটনা সংঘটিত হতে পারে বলে পূর্বে ধারণা করা যায় নি বা ক্ষেত্রবিশেষে যে ঘটনার প্রকৃত কারণ পূর্বে জানা ছিলো না বা হয়তো পরেও জানা যায় নি সে ঘটনাকে ‘দুর্ঘটনা’ বলা হয়, কিন্তু প্রকৃত বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে, কোনো ঘটনা সম্পর্কে তা সংঘটিত হবার পূর্বে ধারণা করা যাক বা না-ই যাক, অথবা ঘটনার প্রকৃত কারণ পূর্বে বা পরে জানা যাক বা না-ই যাক, কারণ ছাড়া কোনো ঘটনাই সংঘটিত হতে পারে না। আর পরিবর্তনশীলতার বৈশিষ্ট্যের অধিকারী বস্তু অনাদি হতে পারে না; তার একটা শুরু বা সূচনা থাকতেই হবে এবং সে শুরু বা সূচনার উৎসকে অবশ্যই পরিবর্তনশীলতার বৈশিষ্ট্য থেকে মুক্ত থাকতে হবে। বলা বাহুল্য যে, বস্তু নিজেই সে সূচনা-উৎস হতে পারে না। কারণ, বস্তু পরিবর্তনশীলতার বৈশিষ্ট্য থেকে মুক্ত নয়। তার চেয়েও বড় কথা, বস্তুর তো অস্তিত্বই ছিল না, তাই সে স্বয়ং নিজের সূচনাকারী হবে কী করে? অতএব, এমন কোনো সত্তা থাকতেই হবে যিনি বস্তুর সূচনা বা সৃষ্টিকারী এবং তাতে প্রাণসঞ্চারকারী। আর সে সত্তা বস্তুগত হতে পারেন না, কারণ আমরা তো বস্তুরই উৎস সন্ধান করছি - যে বস্তু অনাদি ও পরিবর্তনশীলতামুক্ত হতে পারে না।
অবশ্য ‘স্রেফ আদি বস্তু’ তত্ত্ব অনেক আগেই স্বয়ং বিজ্ঞানের দ্বারাই অর্থহীন প্রমাণিত হয়েছে। সর্বশেষ বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার-উদ্ভাবন অনুযায়ী বস্তুলোকের মৌলিকতম পর্যায় কোনোরূপ সমগুণসম্পন্ন বস্তু নয়। কারণ, বস্তুর ক্ষুদ্রতম একক অণুসমূহের গুণবৈশিষ্ট্য বিভিন্ন বস্তুর ক্ষেত্রে বিভিন্ন। আবার অণুসমূহ পরমাণু সমবায়ে গঠিত। পরমাণুগুলোও মৌলিকতম একক নয়। কারণ, বিভিন্ন ধরনের পরমাণু রয়েছে। প্রতিটি পরমাণু একেকটি যৌগিক শক্তি এবং বিভিন্ন ধরনের পরমাণুর যৌগিক গঠন বিভিন্ন। প্রতিটি পরমাণুর কেন্দ্রে রয়েছে এক বা একাধিক প্রোটন যাকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হচ্ছে এক বা একাধিক ইলেকট্রন। এমনকি প্রোটন ও নিউট্রন পর্যন্ত মৌলিক নয়, বরং যৌগিক। প্রতিটি প্রোটন বা নিউট্রন তিনটি কোয়ার্ক দ্বারা গঠিত। কোয়ার্ক ছয় ধরনের এবং প্রত্যেক ধরনের কোয়ার্ক লাল, সবুজ বা নীল রঙের। (অবশ্য এ রং কোনোভাবেই দৃশ্যমান নয়, বরং বৈজ্ঞানিক কল্পনা।) অর্থাৎ আঠারো রকমের কোয়ার্ক থেকে প্রোটন বা নিউট্রন গঠিত যার প্রতিটিতে তিনটি করে কোয়ার্ক রয়েছে। ইলেকট্রন সহ ঊনিশটি মৌলিক একক দিয়ে পরমাণুসমূহ গঠিত। এছাড়া প্রতিটি বস্তুকণারই বিপরীত বা নেতিবাচক বস্তুকণা রয়েছে যাকে anti-matter বা পরাবস্তু বা প্রতিবস্তু বলা হয়। কোনো বস্তু ও সেই বস্তুর পরাবস্তু পরস্পর সংস্পর্শে এলে উভয়েরই বিলুপ্তি ঘটে।
মোদ্দা কথা, বস্তুর স্বরূপ সম্বন্ধে সর্বশেষ আবিষ্কার-উদ্ভাবন অনুযায়ী সমরূপ আদি ‘স্রেফ বস্তু’ বলে কখনো কিছু ছিলো না। বিশেষ করে ইলেকট্রন পরমাণুকেন্দ্রের চতুর্দিকে অস্বাভাবিক গতিতে ঘূর্ণনরত। এমতাবস্থায় অনাদি কাল থেকে ঊনিশটি এককে গঠিত পরমাণু বা তা থেকে গঠিত বস্তুনিচয় স্থির ছিলো এবং হঠাৎ ‘বিনা কারণে’ তা গতিশীল হলো - এরূপ দাবী হবে চরম অবৈজ্ঞানিক। বরং এ স্তরে এসে প্রশ্ন হচ্ছে, এই ঊনিশটি মৌলিক এককের আদি উৎস কী? এগুলোর বৈশিষ্ট্য এবং এগুলোর দ্বারা পরমাণুসমূহের গঠন একজন সূক্ষ্মদর্শী সুপরিকল্পনাবিদ মহাবিজ্ঞানীর অস্তিত্বের কথাই ঘোষণা করে। কারণ, তথাকথিত সমরূপবিশিষ্ট সীমাহীন বস্তুকণার নিষ্ক্রিয় অনাদি অস্তিত্ব যতোখানি অসম্ভব ঊনিশটি বিভিন্ন মৌলিক একক দ্বারা গঠিত পরমাণুসমূহের নিষ্ক্রিয় অনাদি অস্তিত্ব তার চেয়েও অনেক বেশী অসম্ভব।
মোদ্দা কথা, বস্তুজগতের সৃষ্টি, বিবর্তন ও তাতে প্রতিষ্ঠিত প্রাকৃতিক নিয়ম বা কার্যকারণ বিধির উৎস হিসেবে একটি অবস্তুগত পরম জ্ঞানী সুপরিকল্পনাবিদ উৎসের অস্তিত্ব মেনে নেয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই।
এখানে প্রসঙ্গতঃ ডারউইনের বিবর্তনবাদের ওপর সামান্য আলোকপাত করা প্রয়োজন বলে মনে করছি। কারণ, অনেকে ভ্রান্তিবশতঃ ডারউইনের বিবর্তনবাদকে সৃষ্টিকর্তা না থাকার প্রমাণ হিসেবে দাবী করে থাকেন। বস্তুতঃ এ এক উদ্ভট ও হাস্যকর দাবী। কারণ, প্রথমতঃ ডারউইনের বিবর্তনতত্ত্ব অকাট্যভাবে প্রমাণিত কোনো তত্ত্ব নয়, বরং সৃষ্টিবৈচিত্র্যের একটি কাল্পনিক ব্যাখ্যা মাত্র। দ্বিতীয়তঃ জেনেটিক বিজ্ঞানের সর্বশেষ আবিষ্কার-উদ্ভাবন প্রমাণ করেছে যে, প্রজাতিসমূহের মধ্যকার ক্রোমোজম-সংখ্যার পার্থক্যজনিত দেয়াল অতিক্রম করে এক প্রজাতির অন্য প্রজাতিতে উত্তরণ অসম্ভব। অর্থাৎ প্রজাতিসমূহের উদ্ভব বিবর্তন (evolution)-এর প্রক্রিয়ায় হয় নি, বরং হস্তক্ষেপ (revolution) প্রক্রিয়ায় হয়েছে। তাহলে নিঃসন্দেহে বস্তু-জগতের উর্ধে এমন একজন সুবিজ্ঞ পরিকল্পনাকারী রয়েছেন যিনি তাঁর পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য বস্তুজগতে হস্তক্ষেপ করে প্রাণীপ্রজাতি সমূহকে সৃষ্টি করেছেন।
এর চেয়েও মৌলিক কথা হচ্ছে, এমনকি তর্কের খাতিরে বিবর্তনবাদকে সত্য হিসেবে ধরে নিলেও তা সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্বহীনতা প্রমাণে সক্ষম নয়। কারণ, সৃষ্টিকর্তার জন্য অপরিহার্য নয় যে, তিনি প্রতিটি প্রজাতিকে আলাদাভাবে সৃষ্টি করবেন। বরং তিনি যদি সৃষ্টির শুরুতেই তাঁর পরিকল্পনা নির্ধারণ করে বিবর্তনপ্রক্রিয়া সহ প্রাকৃতিক বিধিবিধানসমূহ নির্ধারণ করে দিয়ে থাকেন এবং কালের প্রবাহে তা যথাসময়ে রূপ পরিগ্রহ করে থাকে তো তাতে বাধা কোথায়? (যদিও প্রমাণিত হয়েছে যে, তা বিবর্তনপ্রক্রিয়ায় হয় নি।) কিন্তু কোনো অবস্থাতেই বস্তুলোকের অবস্তুগত সজ্ঞান আদি উৎস ও নিয়ন্তার অস্তিত্ব অস্বীকার করার উপায় নেই।
বিচারবুদ্ধি উন্নততর প্রজ্ঞাসম্পন্ন লোকদের নিকট জীবনজিজ্ঞাসার অন্য একটি জবাব উপস্থাপন করে, তা হচ্ছে দার্শনিক জবাব।
‘অস্তিত্ব’ বলতে যা কিছু আছে বিচারবুদ্ধি প্রথমতঃ তাকে দুইভাবে চিন্তা করতে পারে: হয় তা থাকা অপরিহার্য অর্থাৎ থাকতেই হবে - যা না থাকা আদৌ সম্ভব নয়, অথবা তা থাকা অপরিহার্য নয়, বরং প্রয়োজনীয় শর্তাবলী পূর্ণ হলে তার অস্তিত্বলাভ অনিবার্য হয়ে ওঠে এবং প্রয়োজনীয় পূর্ণাঙ্গ কারণ উপস্থিত না থাকলে বা তাতে কোথাও ঘাটতি থাকলে তার অস্তিত্বপ্রাপ্তি অসম্ভব হয়ে পড়ে। দার্শনিকগণ প্রথম ধরনের অস্তিত্বকে বলেছেন ‘অপরিহার্য অস্তিত্ব’ (Essential Existence - واجب الوجود) এবং দ্বিতীয় ধরনের অস্তিত্বকে বলেছেন ‘সম্ভব অস্তিত্ব’ (Possible Existence - ممکن الوجود) অর্থাৎ যার অস্তিত্ব সর্বাবস্থায় অপরিহার্য বা অনিবার্য নয়, তবে তার অস্তিত্বলাভ সম্ভব অর্থাৎ শর্তাবলী পূর্ণ হলে সম্ভব, অন্যথায় অসম্ভব।
বলা বাহুল্য যে, কোনো অস্তিত্বকে অপরিহার্য অস্তিত্ব হতে হলে তাকে শুরু-শেষ, হ্রাস-বৃদ্ধি এবং যে কোনো ধরনের প্রয়োজন বা অভাববোধ থেকে মুক্ত থাকতে হবে। কিন্তু আমাদের অভিজ্ঞতার বস্তুজগতে আমরা যা কিছু ইন্দ্রিয়নিচয় দ্বারা প্রত্যক্ষ করছি তার সব কিছুই অস্তিত্বলাভের ক্ষেত্রে বিভিন্ন উপাদান ও বিভিন্ন কারণ বিদ্যমান থাকার শর্তসাপেক্ষ এবং অস্তিত্ব অব্যাহত থাকার জন্যও নিজের বাইরের অনেক কিছুর প্রতি মুখাপেক্ষী, তেমনি সদাপরিবর্তনশীল। অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের সব কিছুই ‘সম্ভব অস্তিত্বের’ অন্তর্ভুক্ত; এর কোনোটিই ‘অপরিহার্য অস্তিত্ব’ নয়।
এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এই পরিবর্তনশীল সম্ভব অস্তিত্বসমূহের আদি উৎস কী?
আমরা রূপান্তরপ্রক্রিয়ার ধারাবাহিকতায় পিছন দিকে যেতে যেতে অর্থাৎ উৎসের উৎস এবং তারও উৎস খুঁজতে খুঁজতে এমন এক স্তরে গিয়ে উপনীত হবো যার পিছনে আর কোনো বস্তুগত পর্যায় নেই। এক সময় এ পর্যায়কে আদি নির্গুণ বস্তু বলে দাবী করা হতো যার ভ্রান্তির বিষয়টি ইতিপূর্বেই তুলে ধরা হয়েছে।
সৃষ্টির সূচনা সম্বন্ধে বিজ্ঞানের নামে যে সব তত্ত্ব উপস্থাপন করা হয়েছে তার মধ্যে সর্বশেষ হচ্ছে স্টিফেন হকিং-এর বিগ্ ব্যাং বা মহাবিষ্ফোরণ তত্ত্ব। তাঁর মতে, অসীম ভর সম্পন্ন আদি বস্তুকণায় (primary particle) সংঘটিত মহাবিস্ফোরণের মধ্য দিয়ে বিশ্বজগতের সূচনা হয়েছে। তাঁর মহাবিষ্ফোরণ তত্ত্ব বিশ্বব্যাপী মহা আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। কিন্তু তিনি কথিত আদি বস্তুকণা ও তার অসীম ভরের উৎস, বিস্ফোরণের কারণ এবং বিস্ফোরণকালে অনুসৃত কারণ ও ফলশ্রুতি বিধির উৎস সম্বন্ধে নীরব।
কথিত আদি বস্তুকণা ‘অস্তিত্বলাভ করা’ বা ‘সৃষ্টি হবার’ পূর্বে তো কোনো ‘সম্ভব অস্তিত্ব’ (Possible Existence) ছিলো না; তাহলে তা কোন্ উৎস থেকে উৎসারিত? নিঃসন্দেহে কোনো অবস্তুগত অপরিহার্য অস্তিত্ব থেকেই তা উৎসারিত হয়েছিলো। আর বস্তুর ওপরে প্রাণী-প্রজাতিসমূহকে যা শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রাধান্য প্রদান করেছে তা হচ্ছে তার হস্তক্ষেপক্ষমতা তথা তার জীবন, জ্ঞান ও ইচ্ছাশক্তি। এমতাবস্থায় বস্তুজগতের আদি উৎস অপরিহার্য সত্তা যে প্রাণময়, ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন ও মহাজ্ঞানময় হবেন এটাও অপরিহার্য।
বিচারবুদ্ধি আরো এক ধরনের জবাব প্রদান করে। তা হচ্ছে, আমরা আমাদের অভিজ্ঞতার মধ্যেই বস্তুর ওপরে হস্তক্ষেপকারী এক ধরনের উচ্চতর অবস্তুগত সত্তার সন্ধান পাই। এ হচ্ছে এমন এক ধরনের সত্তা যা প্রাণী প্রজাতিতে রয়েছে। এটা স্রেফ বস্তুগত ও রাসায়নিক প্রতিক্রিয়ার ফল নয়। কারণ, আমাদের মধ্যে যে ইচ্ছাশক্তি ও বিচারবুদ্ধি রয়েছে তাকে আমরা সুস্পষ্ট অনুভব করি।
তর্কের খাতিরে আমরা আমাদের জীবনকে যদি যান্ত্রিক ক্রিয়া বা রাসায়নিক ক্রিয়ার ফল বলে ধরে নেই, তথাপি ইচ্ছাশক্তি ও বিচারবুদ্ধিকে সে পর্যায়ে ফেলা যায় না। কারণ, এ দু’য়ের সাথে বস্তুধর্মের সামঞ্জস্য নেই। বস্তুর একটি প্রধান গুণ হচ্ছে একমুখিতা; তাতে দ্বিধাদ্বন্দ্ব, দ্বৈততা, সংশয়, বিতর্ক, বিশ্বাস, প্রত্যয় ইত্যাদি থাকতে পারে না। কিন্তু প্রাণীর মধ্যে তা রয়েছে; বিশেষ করে মানুষের মধ্যে এ সব বৈশিষ্ট্য এতোই প্রবল যে, তা কেবল মানুষকে বস্তুগত সত্তার উর্ধস্থ সত্তারূপেই তুলে ধরে না, বরং ক্ষেত্রবিশেষে তা তাকে অন্যান্য প্রাণীপ্রজাতি থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে। উদাহরণস্বরূপ, প্রাণীকুলের সহজাত প্রবণতা (যা অবশ্য তার মধ্যে এক অবস্তুগত শক্তির অস্তিত্ব প্রমাণ করে) হচ্ছে এই যে, যে কোনো প্রাণীই ক্ষুধা পেলে তার দেহের চাহিদা মিটানোর উপযোগী খাবার খেতে চায়। তর্কের খাতিরে যদি ধরে নেই যে, তার এ ক্ষুধা লাগার বিষয়টি এক ধরনের বস্তুগত রাসায়নিক ক্রিয়া, তাহলে মানতে হবে যে, তার পক্ষে ক্ষুধা নিবৃত্তি করা সম্ভব হলে অবশ্যই সে ক্ষুধা নিবৃত্তি করবে। যেমন: ঝুঁকি না থাকলে একটি ক্ষুধার্ত মশা যে কোনো মানুষের রক্ত পান করে। ক্ষুধার্ত অবস্থায় একটি বিড়ালও তার খাওয়ার উপযোগী যে কোনো খাবারে কামড় দেয়। অবশ্য কাছাকাছি মানুষ দেখলে সে ‘ভয়’ পায়; তার এ ‘ভয় পাওয়া’ও প্রমাণ করে যে, তার মধ্যে অবস্তুগত কিছু আছে। কিন্তু একজন রোযাদার নারী বা পুরুষ চরম ক্ষুধার্ত অবস্থায় শেষ বিকেলে সুস্বাদু খাবার তৈরী করে এবং ইফতারীর সময় ভক্ষণ ও পরিবেশনের জন্যে সাজিয়ে রাখার কাজে ব্যস্ত থাকে, অথচ কোনোরূপ ঝুঁকি না থাকা সত্ত্বেও সে তখন খাবার খায় না। এটা নিঃসন্দেহে বস্তুগত রাসায়নিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ধর্মের সাথে সাংঘর্ষিক। তার এ আচরণ তার মধ্যে এক প্রবল ইচ্ছাশক্তি ও বিচারবুদ্ধির অস্তিত্বের প্রমাণ বহন করে যা বস্তুধর্মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ও লড়াই করতে পারে।
উপরোক্ত ক্ষেত্রে কেউ হয়তো মানুষের অভ্যাস ও সংস্কারের কথা তুলতে পারে। কিন্তু ব্যাপার হচ্ছে এই যে, বস্তুর বেলায় ‘সংস্কার’ ও কুসংস্কার’ কোনোটাই প্রযোজ্য নয়। অতএব, প্রাণীপ্রজাতিসমূহের সদস্যদের, বিশেষ করে মানুষের বস্তুগত শরীর জুড়ে এক বা একাধিক এমন ধরনের অবস্তুগত অস্তিত্ব রয়েছে যা বস্তুর ওপরে হস্তক্ষেপ করে থাকে এবং স্বয়ং বস্তুধর্মের বিরুদ্ধে লড়াই করতে পারে (তা সে লড়াইয়ে তার হার-জিত যা-ই হোক না কেন)। অতএব, গোটা সৃষ্টিলোকের সূচনা অর্থাৎ এর বস্তুগত ও অবস্তুগত উপাদানসমূহ সৃষ্টি এবং প্রাকৃতিক বিধান নির্ধারণ ও সৃষ্টিজগতের পরিচালনার পিছনে সীমাহীন ক্ষমতার অধিকারী এক অবস্তুগত শক্তির অস্তিত্ব থাকা খুবই সম্ভব, বরং অপরিহার্য।
বিচারবুদ্ধি এছাড়া আরো একভাবেও জীবনজিজ্ঞাসার জবাব দিতে পারে। তা হচ্ছে, বস্তুর ওপরে কেবল তা-ই প্রতিক্রিয়া করতে পারে যার অস্তিত্ব আছে। (অবশ্য অবস্তুর ওপরেও তা প্রতিক্রিয়া করতে পারে, তবে যারা অবস্তুগত অস্তিত্ব অস্বীকার ও অস্তিত্বহীন মনে করে তাদের জন্যে বস্তুগত অস্তিত্ব থেকেই অবস্তুগত অস্তিত্বে উপনীত হতে হবে।) উদাহরণস্বরূপ, একটা টেলিভিশনের পর্দায় কেবল সেই অনুষ্ঠানই দেখা যায় যা কোথাও না কোথাও থেকে প্রচার করা হয়। একটি সুপার কম্পিউটার কেবল সেই সব তথ্যই প্রদর্শন করে যা পূর্বেই তার মধ্যে দেয়া হয়েছে এবং যা সংগ্রহ করে পরিবেশন করার জন্যে তার মধ্যে যথাযথ ‘প্রোগ্রাম’ দেয়া হয়েছে; বস্তুতঃ যে প্রোগ্রাম তাকে নিয়ন্ত্রণ করে সে তদনুযায়ীই কাজ করে থাকে। এর বাইরে সে কিছুই করতে পারে না। বিশেষ করে তার মধ্যে যার অস্তিত্ব নেই বা যা তৈরী করার মত প্রোগ্রাম তাকে দেয়া হয় নি এমন কোনো কিছু সে প্রদর্শন বা সম্পাদন করতে পারে না। অর্থাৎ একটি কম্পিউটারের কার্যাবলী একজন প্রোগ্রামারের অস্তিত্ব প্রমাণ করে যিনি তার মধ্যে সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি বা প্রোগ্রাম সমূহ প্রদান করেছিলেন।
এখন প্রশ্ন হচ্ছে, মানুষ যে সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব ও অন্যান্য অবস্তুগত সত্তা, বিশেষ করে আত্মার অস্তিত্ব সম্বন্ধে বিতর্ক করছে, মানুষ যদি বস্তু ছাড়া আর কিছুই না হবে তাহলে তার মধ্যে এ বিতর্কের সূত্রপাত হলো কীভাবে? বলা যেতে পারে যে, এক কম্পিউটার থেকে অন্য কম্পিউটারে তথ্য ও প্রোগ্রাম স্থানান্তরের ন্যায় বংশানুক্রমে প্রাপ্ত ধারণা এ বিতর্কের সৃষ্টি করেছে। কিন্তু সে ক্ষেত্রে প্রশ্ন আসে, প্রথম বার যে ব্যক্তির মনে স্রষ্টা-প্রসঙ্গ উদিত হলো তার মনে তা কোত্থেকে এলো? যদি ইন্দ্রিয়াতীত অবস্তুগত স্রষ্টার অস্তিত্ব না-ই থাকবে তাহলে তার মন-মস্তিষ্কে এ ধারণা এলো কীভাবে? কীভাবে এ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হলো? যার অস্তিত্বই নেই তা তো প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে না। অতএব, স্রষ্টা সম্বন্ধে মানুষের মন-মস্তিষ্কে ধারণা সৃষ্টি এবং এতদসংক্রান্ত বিতর্ক সৃষ্টিই তাঁর অস্তিত্ব প্রমাণ করে।
এভাবে বিচারবুদ্ধি আরো অনেক পন্থায় জীবনজিজ্ঞাসার জবাব দিতে পারে। তার মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ জবাব হচ্ছে এই যে, যে ব্যক্তি সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব অস্বীকার করে সে-ও তার নিজের মধ্যে বস্তু-উর্ধ এক সত্তার অস্তিত্বকে অস্বীকার করতে পারে না। এ সত্তার সংজ্ঞা নিয়ে মতপার্থক্য থাকতে পারে, কিন্তু দু’টি বিষয়ে মতপার্থক্য থাকতে পারে না। তা হচ্ছে, তার নিজের অস্তিত্ব ও তার মধ্যকার বস্তু-উর্ধ বৈশিষ্ট্য। এমনকি সে মুখে যদি তা অস্বীকার করেও তথাপি কাজে ও আচরণে তা স্বীকার করে নেয়। সে বিতর্ক করে, আর বিতর্ক করা বস্তুর ধর্ম নয়। সত্য ও মিথ্যা, ভাল ও মন্দ, জ্ঞান ও অজ্ঞতা, সম্মান ও লাঞ্ছনা, লজ্জা ও গৌরব ইত্যাদি পরিভাষা ও এসবে পরিব্যক্ত তাৎপর্যের সাথে জড়িয়ে পড়ার ক্ষেত্রে সে স্রষ্টার অস্তিত্বে প্রত্যয় পোষণকারীদের সাথে অভিন্ন। শুধু তা-ই নয়, তার ব্যক্তিত্বের বিকাশ, রুচিবোধ, সাহিত্য-সংস্কৃতি, স্বাধীনতা, সাম্য, মৈত্রী, মুক্তি, জয়-পরাজয়, সুখ-দুঃখ, শোক-বেদনা, শ্রদ্ধা ও সম্মান ইত্যাদি সকল পরিভাষার সাথেই সে নিজেকে সম্পৃক্ত করে। অথচ বস্তুর ক্ষেত্রে এ সব পরিভাষা কোনো তাৎপর্য বহন করে না। এ সব পরিভাষা কেবল বস্তুদেহকে আশ্রয়কারী অবস্তুগত আত্মিক সত্তারই সৃষ্টি এবং এ আত্মিক সত্তার জন্যই তাৎপর্য বহন করে। অতএব, এ আত্মিক সত্তাকে অস্বীকার করা তার পক্ষে সম্ভব নয়। এমতাবস্থায় গোটা বিশ্বলোকের অস্তিত্ব ও পরিচালনার পিছনে এর চেয়ে অসংখ্য গুণ শক্তিশালী একজন পূর্ণতম অবস্তুগত সত্তার অস্তিত্ব অস্বীকার করার পক্ষে কোন্ যুক্তি থাকতে পারে?
অতঃপর সে কি সর্বজনীনভাবে গ্রহণযোগ্য জ্ঞান-উৎস বিচার-বুদ্ধির রায় মেনে নেবে? নাকি অন্ধভাবে সৃষ্টিকর্তাকে অস্বীকার করে চলবে? সে যদি তার বিচারবুদ্ধির রায়কে মুখে অস্বীকার করেও তথাপি তার বিচারবুদ্ধি যে এ রায়ই দিতেই থাকবে তাতে সন্দেহ নেই।
(নুর হোসেন মজিদী লিখিত জিবন জিজ্ঞাসা গ্রন্থ থেকে সংকলিত)