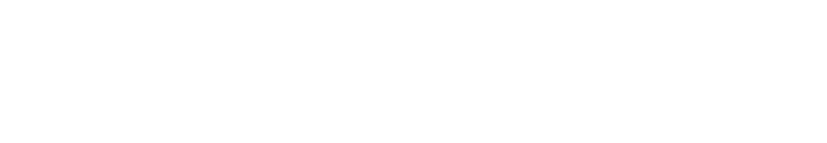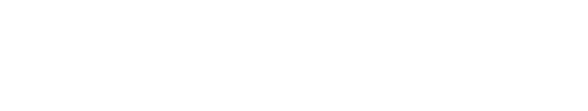শিয়া-সুন্নী বিতর্ক অনেক পুরনো, অবশ্য ইদানীং ফেসবুক-এর কল্যাণে এ বিতর্ক ব্যাপকতর পরিসরে বিস্তার লাভ করেছে। তবে একটি বিষয় লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, শিয়া-বিরোধীরা শিয়া সম্পর্কে যে ধারণা পোষণ করছেন তা শিয়াদের মৌলিক গ্রন্থাবলীর ওপর ভিত্তিশীল নয়, বরং অতীতের শিয়া-বিরোধী লোকদের লেখার ওপর ভিত্তিশীল যা বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই বিদ্বেষপ্রসূত। এখানে এ প্রসঙ্গে নিরপেক্ষভাবে কতগুলো মৌলিক তথ্য তুলে ধরার চেষ্টা করা হচ্ছে।
এ আলোচনায় আমরা কেবল বিতর্কাতীত অকাট্য তথ্যকে গ্রহণ করবো এবং বিচারবুদ্ধি (আক্বল্), কোরআন মজীদ, মুতাওয়াতির হাদীছ ও ছ্বাহাবীদের যুগ থেকে সকল মুসলমানের কাছে গ্রহণযোগ্য তথ্যাদি ও ত সমূহকে বিচারের মানদণ্ড হিসেবে গ্রহণ করবো; স্বল্পসূত্রে বর্ণিত হাদীছ ছোটখাট বিষয়ে গ্রহণযোগ্য হলেও মৌলিক বিষয়াদিতে ও বিতর্কিত বিষয়াদিতে আমরা তা গ্রহণ করবো না, বিশেষ করে এ কারণে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর ইন্তেকালের দুই শতাধিক বছর পরে সংকলিত হাদীছ গ্রন্থাদিতে (সতর্ক পরীক্ষা-নিরীক্ষা সত্ত্বেও) বহু জাল ও বিকৃত হাদীছ প্রবিষ্ট হয়ে থাকা অসম্ভব নয়।
শিয়া ও সুন্নীর মধ্যে কয়েকটি পার্থক্য হচ্ছে আক্বীদাহর ক্ষেত্রে এবং কয়েকটি পার্থক্য আহকাম বা বিধানের ক্ষেত্রে।
তবে শুরুতেই উল্লেখ করতে চাই যে, ইসলামের মৌলিকতম উপস্থাপনাসমূহ যা মুসলমান ও অমুসলমানদের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করে তা হচ্ছে তাওহীদ, আখেরাত ও হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর খাতমে নবুওয়াতে ঈমান; কোরআনে ঈমান খাতমে নবুওয়াতে ঈমান-এরই অন্তর্ভুক্ত। আর এ তিনটি বিষয় শিয়া ও সুন্নীর ক্ষেত্রে অভিন্ন।
এখানে আরো উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, কোরআন মজীদ থেকে জানা যায় যে, তাওহীদ ও আখেরাতের মূল বিষয়ের ঈমান সহজাত, তাই কোনো ব্যক্তিই এ দু’টি বিষয় গ্রহণের দায়িত্ব থেকে রেহাই পাবে না। কিন্তু নবুওয়াত্ সহ অন্যান্য বিষয় গ্রহণের দায়িত্ব ঐ সব বিষয়ে ইতমামে হুজ্জাত্ (কোনো বিষয়ে এমনভাবে ধারণা লাভ যে, তার সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ থাকে না) হওয়ার ওপর নির্ভরশীল। তাই আল্লাহ্ ও আখেরাতে ঈমান ও নেক আমলের অধিকারী ইয়াহুদী, খৃস্টান ও ছ্বাবেয়ীরা [হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর ওপর ঈমান না থাকা সত্ত্বেও] নাজাতের অধিকারী হবে (সূরাহ্ আল্-বাক্বারাহ্ – ৬২), অবশ্য হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর নবুওয়াত্ সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়া সত্ত্বেও কোনো ব্যক্তি তাঁর ওপর ঈমান না আনলে সে নাজাত পাবে না। এমতাবস্থায় শিয়া ও সুন্নীদের মধ্যে হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর নবুওয়াত্, খাতমে নবুওয়াত ও কোরআন মজীদের ওপর ঈমান অভিন্ন হওয়া অবস্থায় এ ক্ষেত্রে ইখলাছ্বের অধিকারী যে কারো নাজাত না পাওয়ার কোনোই কারণ নেই, তবে মতপার্থক্যেরে কোনো বিষয়ে ইখলাছ্বের সাথে ইয়াক্বীন হাছ্বিল্ হওয়া সত্ত্বেও তা গ্রহণ না করলে তাকে অবশ্যই আল্লাহ্ তাআলার কাছে পাকড়াও হতে হবে।
এবার আমরা শিয়া ও সুন্নীর পার্থেক্যের বিষয়গুলোর প্রতি সংক্ষেপে দৃষ্টি দেবো। প্রথমে দেখবো আক্বায়েদের সাথে সংশ্লিষ্ট মতপার্থক্যগুলো।
(১) তাওহীদ্ সম্বন্ধে শিয়া মাযহাবের আক্বীদাহর একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে, তারা আল্লাহ্ তাআলার সত্তা ও গুণাবলীকে অভিন্ন বলে জানে এবং এটাই হচ্ছে পূর্ণাঙ্গ একত্ব (তাওহীদ)। [এ প্রসঙ্গে উপমা হচ্ছে এই যে, যে বস্তু নিজে মিষ্ট নয় তাতে চিনি দেয়া হলে মিষ্ট হয় অর্থাৎ তার সত্তা ও মিষ্ট গুণ স্বতন্ত্র এবং বস্তুটিকে মিষ্টতা ছাড়াও চিন্তা করা যায়, কিন্তু চিনির মিষ্টতা তার সত্তা থেকে স্বতন্ত্র নয়।] এ বিষয়ে সুন্নী সমাজে অভিন্ন আক্বীদাহ্ নেই।
(২) আল্লাহ্ তাআলার শরীর ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আছে কিনা এবং ক্বিয়ামতের দিন তাঁকে দেখা যাবে কিনা – এ প্রশ্নে সুন্নীদের মধ্যে মতপার্থক্য আছে, কিন্তু শিয়াদের মতে আল্লাহ্ তাআলা অবস্তুগত অসীম সত্তা বিধায় তাঁর শরীর ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ থাকতে পারে না এবং তাঁকে দেখা যেতে পারে না; কোরআন মজীদে যে, তাঁর হাতের কথা বলা হয়েছে তাতে তাঁর শক্তি-ক্ষমতা বুঝানো হয়েছে যেমনটি মানুষ এ অর্থে এ শব্দ ব্যবহার করে থাকে। আর কোরআন মজীদে ক্বিয়ামতে আল্লাহ্ তাআলার লেক্বা’র (কাছাকাছি হওয়া, এখানে আত্মিকভাবে) কথা বলা হয়েছে, তাঁকে রুইয়াত্ (চাক্ষুষভাবে দেখা)-এর কথা বলা হয়য় নি।
(৩) শিয়া মায্হাবের আক্বীদাহ্ অনুযায়ী আল্লাহ্ তাআলা সুবিচারক বা ন্যায়বিচারক (আদেল্); তিনি যুলুম করতে পারেন না। কিন্তু সুন্নীদের মধ্যে অনেকে মনে করে যে, এ কথা বললে আল্লাহকে অক্ষম ও তাঁর শক্তি-ক্ষমতাকে সসীম মনে করা হয়। তাদের মধ্যে কতক লোক বলে, আল্লাহ্ চাইলে কোনো নেককারকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করতে পারেন এবং সে ক্ষেত্রে তাঁকে যালেম বলা যাবে না (অর্থাৎ মানবিক জ্ঞান এ কাজকে যুলুম বলে মনে করলেও বলা যাবে না যে, আল্লাহ্ যুলুম করেছেন)। কিন্তু এ ধারণা কোরআন মজীদের সাথে সাংঘর্ষিক। কারণ, মানুষ যুলুম বলতে যা বুঝে থাকে সে অর্থেই আল্লাহ্ তাআলা বহু বার বলেছেন যে, তিনি যুলুম করেন না। শুধু তা-ই নয়, তিনি এ-ও বলেছেন যে, তিনি ওয়াদা বরখেলাফী করেন না। এমতাবস্থায় তিনি যে, নেককারকে পুরষ্কার ও অপরাধী-পাপাচারীকে শাস্তিদানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তিনি তা ভঙ্গ করবেন না এবং ন্যায়বিচার করবেন। অবশ্য আল্লাহর আদেল্ হওয়ার মধ্যে এ তাৎপর্যও রয়েছে যে যার কাছে যে বিষয়ের এতমামে হুজ্জাত্ হয় নি তাকে তিনি সে বিষয়ে পাকড়াও করবেন না, কারণ, তিনি সাধ্যের অতীত দায়িত্ব দেন না; ওপরে সূরাহ্ আল্-বাক্বারাহর ৬২ নম্বর আয়াতের প্রতি যে ইঙ্গিত করা হয়েছে অর্থাৎ নবুওয়াতে মুহাম্মাদীর ওপর ঈমান না থাকা সত্ত্বেও (এতমামে হুজ্জাত না হওয়ার শর্তে) ইয়াহূদী, খৃস্টান ও ছ্বাবেয়ীদের নাজাত পাওয়ার বিষয়টিও আল্লাহর সুবিচারক হওয়ার বৈশিষ্ট্যের দাবী।
(৪) তাক্বদীর সম্পর্কে সুন্নীদের মধ্যে পরস্পর বিরোধী আক্বীদাহ্ রয়েছে; আশায়েরীরা অদৃষ্টবাদী এবং বলে যে, আল্লাহ্ ভাগ্যে সব লিখে দিয়েছেন এবং কেবল তা-ই ঘটে; এর অন্যথা নেই। অন্যদিকে মু‘তাযিলীরা মনে করে আল্লাহ্ সব কিছু প্রাকৃতিক বিধান ও মানুষের স্বাধীন এখতিয়ারের ওপর ছেড়ে দিয়েছেন; কোনো কিছুতেই হস্তক্ষেপ করেন না। প্রথম মতটি স্বীকার করলে বলতে হবে যে, ঈমান, আমল, ওয়াহী, নবুওয়াত ইত্যাদি সব কিছুই অর্থহীন, কারণ, আল্লাহ্ যা নির্ধারণ করে রেখেছেন বা ঘটাচ্ছেন তার অন্যথা হবে না, অথচ কোরআন মজীদের বিভিন্ন আয়াতে মানুষের ক্ষমতা, এখতিয়ার ও কর্মের কথা বলা হয়েছে। আর দ্বিতীয় মতটিও কোরআনের সাথে সাংঘর্ষিক, কারণ, কোরআন মজীদের বিভিন্ন আয়াতে মানুষের কাজে আল্লাহর হস্তক্ষেপের কথা আছে। এ বিষয়ে শিয়া মাযহাবের আক্বীদাহ্ হচ্ছে এই যে, আল্লাহ্ তাআলা প্রাকৃতিক বিধি-বিধান ও নবী-রাসূলগণকে প্রেরণ সহ সৃষ্টিলক্ষ্যের পূর্ণতা বিধানের জন্য অপরিহার্য বিষয়গুলোকে পূর্বেই নির্ধারণ করে রেখেছেন, এর আওতায় মানুষকে স্বাধীনতা, ইচ্ছাশক্তি ও এখতিয়ার দিয়েছেন, কতগুলো বিষয়কে দুই বা ততোধিক সম্ভাবনাযুক্ত করে নির্ধারণ করে রেখেছেন অর্থাৎ অমুক বিষয়ে মানুষ এরূপ করলে এ ফল হবে, ঐরূপ করলে ঐ ফল হবে। এছাড়া তিনি বান্দাহদের কাজ পর্যবেক্ষণ করেন এবং সৃষ্টিলক্ষ্যের জন্য বা বান্দাহর কল্যাণের জন্য তাদের কাজে হস্তক্ষেপও করেন। তক্বদীর বিষয়ক এ আক্বীদাহই হচ্ছে কোরআন-সম্মত আক্বীদাহ।
(৫) শিয়া মায্হাবের আক্বীদাহ্ অনুযায়ী নবী-রাসূলগণ (আ.) নবুওয়াত লাভের পূর্বে ও পরে যে কোনো ধরনের গুনাহ্ থেকে মুক্ত ছিলেন এবং তাঁদের এ পাপমুক্ততা (‘ইছ্বমাত্) অপরিহার্য বিষয়, অন্যথায় কোনো নবীর ব্যাপারে হুজ্জাত্ পূর্ণ হবে না, ফলে কোনো বান্দাহর মনে কোনো নবীকে নবী বলে প্রত্যয় সৃষ্টি না হলে সে যদি উক্ত নবীকে প্রত্যাখ্যান করে তাহলে আল্লাহ্ তাকে এ জন্য পাকড়াও করতে পারেন না, কারণ, এরূপ ক্ষেত্রে পাকাড়াও করলে তা ন্যায়বিচারের পরিপন্থী হবে। সুতরাং কোরআন মজীদের কোনো আয়াত থেকে যদি দৃশ্যতঃ কোনো নবী গুনাহ্ করেছেন বলে মনে হয় তখন মনে করতে হবে যে, আমরা ঐ আয়াতের সঠিক তাৎপর্য বুঝতে ব্যর্থ হয়েছি, সুতরাং উক্ত আয়াতের সঠিক তাৎপর্য বুঝার জন্য চেষ্টা করতে হবে। উদাহরণস্বরূপ, হযরত আদম (আ.) কর্তৃক নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল ভক্ষণ গুনাহ্ ছিলো না, কারণ, তখন (বেহেশতে) দ্বীন ও শারীআত্ ছিলো না, বরং তা ছিলো কোনো নাবালেগ্ব কর্তৃক কল্যাণকামী অভিভাবকের নছ্বীহত লঙ্ঘনের অনুরূপ।
কিন্তু সুন্নী ধারায় এ ব্যাপারে মতপার্থক্য আছে অর্থাৎ অনেকে নবী-রাসূলগণের (আ.) পাপমুক্ততাকে নবুওয়াতের পূর্বে ও পরে কোনো অবস্থায় যরূরী মনে করেন না, অনেকে নবুওয়াতের পরে পাপমুক্ততাকে যরূরী মনে করলেও নবুওয়াত লাভের পূর্ববর্তী জীবনের জন্য যরূরী মনে করেন না এবং কেউ কেউ শিয়াদের মতোই উভয় অবস্থায়ই পাপমুক্ততাকে যরূরী মনে করেন, যদিও সুন্নীদের মধ্যে এদের হার কম।
(৬) কোরআন মজীদের আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত সর্বশেষ, পূর্ণাঙ্গ ও ক্বিয়ামত পর্যন্ত সংরক্ষিত কিতাব হওয়ার ব্যাপারে শিয়া ও সুন্নীর সাধারণ ও মূল ধারায় কোনো রকমের মতপার্থক্য নেই। কিন্তু কতক লোক কোনরূপ প্রামাণ্য দলীল-প্রমাণ ছাড়াই দাবী করে যে, শিয়া মাযহাব কোরআনে বিকৃতিতে, বিশেষ করে সূরাহ্ বেলায়াত্ নামে একটি সূরাহ্ বিলুপ্ত করা হয়েছে বলে বিশ্বাস করে। কিন্তু এ দাবীর কোনো ভিত্তি নেই। শিয়া অধ্যুষিত দেশগুলোতে যে কোরআন মুদ্রিত হয় ও শিয়া মাযহাবের অনুসারীরা যা তেলাওয়াত করে তা সুন্নী অধ্যুষিত দেশগুলোতে মুদ্রিত কোরআনের সাথে অভিন্ন।
কতক লোক দাবী করে যে, শিয়ারা তাক্বীয়াহ্ নীতি অনুযায়ী তাদের ভিন্ন কোরআনের কথা গোপন রাখে এবং গোপনে তা শিক্ষা দেয়। এটা একটা উদ্ভট হাস্যকর দাবী। কারণ, তাক্বীয়াহ্ নীতি (যার উৎস কোরআন মজীদ) কেবল প্রাণ বাঁচানোর জন্য প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে অনুসরণ করা হয়। বিশ্বের গুটি কয়েক কাদীয়ানী যেখানে তাদের আক্বীদাহ্ প্রকাশ্যে প্রচার করে সেখানে শিয়া সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশে, বিশেষ করে ইরানের মতো শক্তিশালী দেশে (যে দেশ আমেরিকাকে চ্যালেঞ্জ করে চলছে) তাক্বীয়াহ্ নীতি অনুসরণ করা হয় বলে দাবী করার ন্যায় উদ্ভট হাস্যকর দাবী আর কী হতে পারে!
তবে সকল মাযহাবী ধারার মধ্যেই কতক বিকৃত চিন্তার বা অনুপ্রবেশকারী লোক থাকতে পারে এবং তারা উদ্ভট আক্বীদাহ্ প্রচার করতে পারে। যেমন, সুন্নী জগতে কতক ছোট ছোট উপধারা আছে যারা বলে যে, আল্লাহ্ সকলের মধ্যে আছেন সুতরাং সকলেই আল্লাহ্। কোনো কোনো উপধারা বিশ্বাস করে যে, তাদের পীর বিশ্বজগতের সব কিছুর পরিচালক, এমনকি জীবন-মৃত্যু ও রিযক্ব তার হাতে। কোনো কোনো উপধারায় পীরকে সিজদাহ্ করা হয়। আবার নব্বই হাজার কালামের কথা বলা হয় যার মধ্য থেকে মাত্র তিরিশ হাজার কালাম মুদ্রিত কোরআন মজীদে আছে। এ সব উদ্ভট বিষয়ের দায়-দায়িত্ব কি সাধারণভাবে সুন্নী ধারার ওপর চাপানো যাবে? তাহলে শিয়াদের মধ্যে যদি কতক বিকৃত বা অনুপ্রবেশকারী লোক কোরআন সম্বন্ধে বিকৃতির কথা বলে তার দায়িত্ব কেন শিয়া মাযহাবের সাধারণ ও মূল ধারার ওপর চাপানো হবে?
কতক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, হাদীছগ্রন্থসমূহে অনেক তথ্য সংগৃহীত হয়েছে যার সব হয়তো সঠিক নয়; এ সব তথ্যসংকলনকে কোনো মাযহাবের মত বা চর্া মনে করা ঠিক হবে না। যেমন, সুন্নীদের বিভিন্ন হাদীছ গ্রন্থে এমন কিছু হাদীছ আছে যেগুলোতে দাবী করা হয়েছে যে, কতক ছ্বাহাবী বিদ্যমান কোরআনে কম-বেশী করা হয়েছে বলে উল্লেখ করেছেন। একে কি সুন্নীদের আক্বীদাহ্ বলে দাবী করা যাবে? বলা বাহুল্য যে, এ সব হাদীছ মিথ্যা রচনা।
(৭) শিয়া ও সুন্নীর আক্বীদাহর মধ্যে সবচেয়ে বড় মতপার্থক্য হচ্ছে ইমামত ও খেলাফত প্রশ্নে। সুন্নী আক্বীদাহ্ অনুযায়ী হযরত রাসূলে আকরাম (সা.)-এর ইন্তেকালের পর উম্মাহর হেদায়াতের জন্য কোরআন ও সুন্নাহই যথেষ্ট এবং উম্মাহর নেতৃত্ব ও শাসনকর্তৃত্বের দায়িত্ব স্বয়ং উম্মাহ্ কর্তৃক নির্বাচিত ব্যক্তির ওপর অর্পিত হবে। কিন্তু শিয়া মাযহাবের আক্বীদাহ্ অনুযায়ী, যেহেতু যে কোনো রাসূলের দায়িত্ব কেবল আল্লাহর বাণী পৌঁছে দেয়া নয়, বরং তার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ, বাস্তবায়ন এবং স্বীয় উম্মাহকে নেতৃত্ব প্রদান ও সম্ভব হলে শাসন-কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা ও রাষ্ট্র পরিচালনা, সেহেতু শেষ নবীর (সা.) ইন্তেকালের পর নতুন ওয়াহী আগমন বন্ধ থাকলেও নবীর অবশিষ্ট দায়িত্বগুলো পালনের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে নবীর স্থলাভিষিক্ত নবীর গুণাবলীর অধিকারী (নিষ্পাপ, নির্ভুল ও পূর্ণ জ্ঞানী) ইমাম ও খলীফাহ্ মনোনীত হওয়া অপরিহার্য। আর আল্লাহ্ তাআলা হযরত আলী, ইমাম হাসান ও ইমাম হোসেন (আ.) এবং ইমাম হোসেনের পর্যায়ক্রমিক নয়জন বংশধরকে উম্মাতে মুহাম্মাদীর জন্য পর্যায়ক্রমিক ইমাম হিসেবে মনোনীত করেছেন। এ বিষয়টি রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বিভিন্ন উপলক্ষ্যে ঘোষণা করেছেন – যা শিয়া ও সুন্নী উভয় ধারার বিভিন্ন হাদীছ গ্রন্থে বর্ণিত বহু হাদীছে উল্লিখিত হয়েছে, বিশেষ করে হযরত আলী (আ.) কে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর অব্যবহিত পরবর্তী শাসক হিসেবে মনোনীত করার বিষয়টি হাদীছে গ্বাদীর্ নামক মুতাওয়াতির হাদীছে উল্লিখিত হয়েছে।
এ প্রসঙ্গে সুন্নী ধারার বক্তব্য হচ্ছে এই যে, হযরত আলীর মনোনয়নের কথা কোরআন মজীদে উল্লেখ করা হয় নি। এতে সন্দেহ নেই। আর হাদীছে গ্বাদীর-এ উল্লিখিত বক্তব্যকে তারা ভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করে। কিন্তু যদি ধরে নেয়া হয় যে, আল্লাহ্ তাআলা রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর পরবর্তী নেতা ও শাসক মনোনীত করে যান নি তাহলেও মুসলমানদের দায়িত্ব ছিলো স্বীয় ঈমান এবং দ্বীন ও দুনিয়ার কল্যাণের স্বার্থে কোরআন মজীদের পথনির্দেশের আলোকে এ মনোনয়নের কাজ আঞ্জাম দেয়া। কোরআন মজীদে আহলে বাইতের পবিত্রতার কথা বলা হয়েছে (সূরাহ্ আল্-আহযাব্ - ৩৩) যা উম্মাতে মুহাম্মাদীর অন্য কারো সম্বন্ধে বলা হয় নি। আর ছ্বাহাবীদের যুগ থেকে সর্বসম্মত মত অনুযায়ী আহলে বাইত বলতে হযরত ফাতেমাহ্, হযরত আলী, হযরত ইমাম হাসান ও হযরত ইমাম হুসাইন (আ.)কে বুঝানো হয়েছে। আরো যোগ করা যেতে পারে যে, আলে মুহাম্মাদ তথা রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর আহলে বাইতের প্রতি দরূদ প্রেরণ ছাড়া নামায ছ্বহীহ্ হয় না এবং হানাফী মাযহাবে নামাযে দরূদে ইবরাহীমী পড়া হয় যাতে আলে মুহাম্মাদকে আলে ইবরাহীমের সাথে অর্থাৎ হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর বংশে আগত নবী-রাসূলগণের (আ.) সাথে তুলনা করা হয়। এছাড়া সর্বসম্মত মত অনুযায়ী হযরত আলী (আ.) ছিলেন উম্মাহর মধ্যে সবচেয়ে বড় জ্ঞানী। [রাসূলুল্লাহ্ (সা.) নিজেকে জ্ঞানের নগরী ও আলীকে তার দরজা হিসেবে উল্লেখ করেছেন।] তাই উম্মাহর উচিত ছিলো পর্যায়ক্রমিকভাবে হযরত আলী, হযরত ইমাম হাসান ও হযরত ইমাম হুসাইন (আ.) কে খলীফাহ্ মেনে নেয়া এবং তাঁদের হেদায়াতের আলোকে পথচলা, আর বিতর্কিত বিষয়সমূহে তাঁদের মত মেনে নেয়া। এ তিনজনকে ইমাম ও খলীফাহ্ মেনে নিলে তাঁদের পরবর্তী নেতৃত্ব ও শাসনকর্তৃত্বের বিষয়টি তাঁদেরই পথনির্দেশের আলোকে নির্ধারিত হতো।
চার খলীফাহকে “খুলাফায়ে রাশেদীন” মনে করা ও তাঁদেরকে পর্যায়ক্রমিকভাবে মর্যাদা দেয়ার কোনো অকাট্য দালীলিক (আক্বল্, কোরআন, মুতাওয়াতির হাদীছ ও উম্মাহর ধারাবাহিক মতৈক্য) আক্বাএদী ভিত্তি নেই। এ আক্বীদাহ্ একটি ভিত্তিহীন ও ভক্তিপ্রসূত অন্ধ ধারণা মাত্র।
অন্যদিকে রাসূলুল্লাহর (সা.) ইন্তেকালের পর কোরআন-সুন্নাহ্ যথেষ্ট হলেও এ কোরআন-সুন্নাহর জ্ঞান পূর্ণ মাত্রায় একমাত্র হযরত আলীর (আ.) ছিলো। বিশেষ করে রাসূলুল্লাহর (সা.) পরিপূর্ণ সাহচর্য একমাত্র তিনিই পেয়েছিলেন, সুতরাং পূর্ণাঙ্গ সুন্নাহ্ কেবল তাঁর কাছ থেকেই পাওয়া সম্ভব ছিলো।
এছাড়া প্রথম তিন খলীফাহর যুগে সুন্নাহর লিখন, সংকলন ও চর্চা নিষিদ্ধ করা হয়। সুতরাং তাঁরা উম্মাহর নেতৃত্ব ও শাসনকর্তৃত্বের জন্যে কোরআন ও সুন্নাহকে যথেষ্ট মনে করতেন বলা চলে না, বরং পরবর্তীকালে এ ব্যাখ্যা দাঁড় করানো হয়েছিলো। [হাদীছ লিপিবদ্ধকরণ নিষিদ্ধ করার যথার্থতা প্রমাণের জন্য বলা হয় যে, কোরআনের সাথে মিশ্রণের আশঙ্কা এড়ানোর জন্য এটা করা হয়। যদি তা-ই হয়ে থাকে তাহলে বলতে হবে যে, স্বয়ং আল্লাহ্ যে কোরআনের হেফাযতের দায়িত্ব নিয়েছেন সে সংক্রান্ত আয়াতের দিকে তাঁদের দৃষ্টি যায় নি এবং তাঁরা এ আক্বীদাহ্ পোষণ করতেন না যে, কোরআনকে বিকৃতকরণ বা তাতে কোনো কিছুর মিশ্রণ ঘটানো কারো পক্ষে সম্ভব নয়।]
(৮) সাধারণভাবে সুন্নীরা ছ্বাহাবীদেরকে সমালোচনার উর্ধে মনে করে, কিন্তু শিয়ারা তাঁদের গ্রহণযোগ্যতাকে তাঁদের আমলের ওপরে ভিত্তিশীল বলে মনে করে। কোরআন মজীদে ছ্বাহাবীদের নিষ্পাপত্ব ঘোষণা করা হয় নি এবং তাঁদের আমলও প্রমাণ করে যে, তাঁদের সকলে নিষ্পাপ ছিলেন না। বিশেষ করে তাঁরা যখন পরস্পর যুদ্ধ করেছেন ও পরস্পরকে হত্যা করেছেন তখন এটা নিশ্চিত যে, তাঁদের সকলে সত্যের ওপর ছিলেন না। কোরআন মজীদে রাসূলুল্লাহর (সা.) যুগের মুনাফিক্বদের কথা বলা হয়েছে যাদের সংখ্যা ছিলো অনেক। ইতিহাসে আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই সহ দু’চার জন বাদে অন্য শত শত মুনাফিক্বকে চিহ্নিত করা হয় নি। এমনকি স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্ (সা.)ও তাদের সকলকে চিনতেন না (সূরাহ্ আত্-তাওবাহ্ - ১০১)। এরা সকলেই ছ্বাহাবী হিসেবে পরিচিত হয়। অতএব, ছ্বাহাবীরা সমালোচনার উর্ধে নন। অথবা ছ্বাহাবীর সংজ্ঞায় পরিবর্তন করতে হবে এবং রাসূলুল্লাহকে (সা.) ঈমানের ঘোষণা সহ দর্শনকারীদের মধ্য থেকে কেবল যাদের আমল সঠিক ছিলো তাঁদেরকে ছ্বাহাবী হিসেবে গণ্য করতে হবে। যে সব আয়াতে তাঁদের প্রতি আল্লাহর সন্তুষ্টির কথা বলা হয়েছে সেগুলোর বক্তব্য সাধারণ (আম্) যার ব্যতিক্রম থাকতে পারে। তাছাড়া কোনো ঘটনার সময় সন্তোষজনক কাজ করার কারণে (যেমন – বায়আতে রেযওয়ানে অংশগ্রহণ) আল্লাহ্ ঐ সময় কারো ওপর সন্তুষ্ট হলে পরে সে ব্যক্তি নাফরমানী করলে আল্লাহর সন্তুষ্টি তার প্রতি অব্যাহত থাকবে এমনটি মনে করা চলে না।
অন্যদিকে যারা মক্কাহ্ বিজয়ের দিনে নিরুপায় হয়ে ঈমানের ঘোষণা দেয় তাদের ঈমান আল্লাহর কাছে কবূল হয় নি (সূরাহ্ আস্-সাজদাহ্ - ২৯), কিন্তু তারাও ছ্বাহাবী হিসেবে পরিচিত। তাই প্রচলিত সংজ্ঞার ছ্বাহাবীদেরকে সমালোচনার উর্ধে গণ্য করার কোনো ভিত্তি নেই।
এবার আহকাম্ সংক্রান্ত কয়েকটি মতপার্থক্য
(১) শিয়া-সুন্নী উভয়ই পাঁচ ওয়াক্ত ও ১৭ রাক্আত্ ফরয নামায আদায় করে। তবে শিয়া মাযহাব্ মনে করে যে, এক আযান ও দুই ইক্বামত দিয়ে যোহর ও আছ্বর্ একত্রে এবং মাগ্বরিব্ ও এশা একত্রে আদায় করা জায়েয। সুন্নী মতে কেবল যরূরী প্রয়োজনের ক্ষেত্রে এটা জায়েয। কিন্তু নবী করীম (সা.) কোথাও বলেন নি যে, কেবল যরূরী প্রয়োজনের ক্ষেত্রে এটা জায়েয। অতএব, মনগড়া কারণের ভিত্তিতে এ জায়েযকে সীমিত করা যেতে পারে না। তাছাড়া হজ্বের সময় (সুন্নী ইমামের পিছনে) আরাফায় যোহর ও আছ্বর্ এবং মাশ্আরুল্ হারাম্-এ (মুজদালিফায়) মাগ্বরিব ও এশা একত্রে আদায় করা হয় যদিও যথাক্রমে আছ্বর্ ও এশা আদায় করার পর ঐ দুই স্থানে অবস্থান ছাড়া কোনো যারূরী ফরয কাজের ব্যস্ততা থাকে না।
এছাড়া পৃথিবীর কোনো কোনো অংশে গ্রীষ্মকালে কোনো কোনো সময় ষোলো ঘণ্টা দিন ও আট ঘণ্টা রাত হয় এবং শীতকালে এর বিপরীত হয়। ঐ সব জায়গার লোকদের জন্য পাঁচ ওয়াক্ত নামায পাঁচ বারে আদায় করা কঠিন ব্যাপার; আছ্বর্ ও এশা ক্বাযা হওয়ার আশঙ্কা থাকে।
অবশ্য কেউ পাঁচ ওয়াক্ত নামায পাঁচ বারে আদায় করলে শিয়া মাযহাব সে কাজকে ভুল বলে গণ্য করে না।
(২) সুন্নীরা কোনো কোনো হাদীছের ভিত্তিতে সূর্যাস্তের সাথে সাথে ইফতার করে, কিন্তু শিয়া মাযহাবের অনুসারীরা প্রায় আধ ঘণ্টা পর অন্ধকার হওয়ার পরে ইফতার করে। কারণ, কোরআন মজীদে রাত (লাইল) হওয়া পর্যন্ত রোযা পূর্ণ করার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়েছে, সূর্যাস্ত (গ্বুরূব্) পর্যন্ত নয়। অতএব, নিঃসন্দেহে কোরআনের আদেশের সাথে সাংঘর্ষিক উক্ত হাদীছ জাল।
(৩) শিয়া মাযহাবে অস্থায়ী বিবাহ (মুতআহ্) বৈধ বলে পরিগণিত হয়, কিন্তু সুন্নী মাযহাবে এটি হারাম বলে গণ্য করা হয়। এটা সর্বস্বীকৃত যে, রাসূলুল্লাহর সময় মুতআহ্ বৈধ ছিলো এবং তিনি কখনোই এটির অবৈধতা ঘোষণা করেন নি। এরপর প্রথম ও দ্বিতীয় খলীফাহর যুগে এটি চালু থাকে এবং দ্বিতীয় খলীফাহ্ তাঁর শাসনামলের মোটামুটি মাঝামাঝি সময়ে এটি নিষিদ্ধ করেন। বলা বাহুল্য যে, আল্লাহ্ ও রাসূলের বিধানে পরবর্তী কারো পরিবর্তনের এখতিয়ার নেই।
মুতআহ্ যে আল্লাহ্ ও রাসূলের বিধানে বৈধ এ সত্যের দিকে দৃষ্টি না দিয়ে অনেকে এটির বিরুদ্ধে বিভিন্ন মনগড়া যুক্তি উপস্থাপন করে। কিন্তু আল্লাহ্ বলেন, “হয়তো তোমরা এমন কিছু অপছন্দ কর যা আসলে তোমাদের জন্য কল্যাণকর এবং হয়তো তোমরা এমন কিছু পছন্দ কর যা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর; আল্লাহ্ জানেন এবং তোমরা জানো না।” (সূরাহ্ আল্-বাক্বারাহ্ - ২১৬)
এখানে আরো স্মর্তব্য যে, ইসলামে নর-নারীর যৌন সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার জন্য তিনটি বৈধ পন্থা রাখা হয়েছে, তা হচ্ছে – স্থায়ী বিবাহ (যদিও তাতে তালাক্বের সুযোগ আছে বিধায় আক্ষরিক অর্থে স্থায়ী নয়), অস্থায়ী বিবাহ ও ক্রীতদাসীকে (এক ব্যক্তি সর্বোচ্চ পাঁচ জন) ভোগ। ইসলাম স্থায়ী বিবাহকে অগ্রাধিকার প্রদান করে, কিন্তু যারা নিজেদের জন্য এর প্রয়োজন রয়েছে বলে অনুভব করে তাদের জন্য অস্থায়ী বিবাহে কোনো বাধা নেই।
(৪) সুন্নী মাযহাবে এক বারে ‘তিন তালাক্ব’ উচ্চারণ করে বা ‘তালাক্ব্ দিলাম’ কথাটি তিন বার উচ্চারণ করে তালাক্ব দিলে ফেরৎ-অযোগ্য চূড়ান্ত তালাক্ব বলে পরিগণিত হয়, কিন্তু শিয়া মাযহাবে এটি ফেরৎযোগ্য এক তালাক্ব বলে পরিগণিত হয়। সুন্নী মাযহাবের এ বিধানটি দ্বিতীয় খলীফাহর সিদ্ধান্ত থেকে গৃহীত। কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর যুগে, প্রথম খলীফাহর যুগে ও দ্বিতীয় খলীফাহর যুগের প্রথম অংশে এ ধরনের তালাক্ব ফেরৎযোগ্য এক তালাক্ব বলে পরিগণিত হতো। সুতরাং তাঁর সিদ্ধান্তের কোনো শর‘ঈ ভিত্তি নেই।
স্মর্তব্য, কোরআন মজীদে (ফেরৎযোগ্য) তালাক্ব্ ‘দুই বার’ (মার্রাতান্) বলে উল্লেখ করা হয়েছে, [‘দুইটি’ (ইছ্নান্) বলা হয় নি] এবং এরপর ভালোভাবে রাখতে বা ভালোভাবে বিদায় দিতে বলা হয়েছে। যে কোনো কথা বলেই তালাক্ব দেয়া হোক না কেন, একবার তালাক্ব দেয়ার পর স্ত্রীকে ফিরিয়ে এনে তার সাথে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার পরেই কেবল তাকে দ্বিতীয় বার তালাক্ব দেয়া যেতে পারে। ‘তালাক্ব্’ উচ্চারণ করার পর তো আর ব্যক্তির স্ত্রী তার স্ত্রী থাকে না, তাহলে সে এর পর পরই কীভাবে দ্বিতীয় বার তালাক্ব দেবে?